
আমরা যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, তাদের গর্বের অন্ত্য নেই। আমরা মনে করি যে আমরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করি। আমরা রাজনীতিতে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা মানুষ। দেশের সমস্যা আমাদের চেয়ে কেউ ভালো বোঝে না। সেসব নিয়ে আমরা আন্দোলন করি, গলা ফাটাই। নানা রঙের রাজনীতির মাথা ও সেবক হয়ে আলো ছড়াই। সেই আলোতে আলোকিত হয় জনজাতির প্রান্তিক মানুষ, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা।
ভুল, ভুল। বাঙালি জাতির প্রতিনিধি ভেবে আত্মপ্রসাদ আমরা লাভ করতে পারি, কিন্তু আদপে আমরাই সংখ্যালঘু। গোটা দেশ ও জাতির কতটুকু আমরা? দেশের আপামর মানুষের সঙ্গে কতটুকু যোগ আছে আমাদের? কতটুকু চিনি তাদের? কতটুকু জীবনে জীবন যোগ করতে পেরেছি তাদের সঙ্গে?
এ সব কথা কেন মনে এল, বলি। এডুকেশন ফোরামের কর্তা আজিজুল হক আর তার বউ-এর ডাকে গিয়েছিলাম পয়লা বৈশাখ। তার ছোট ঘরে জনা সাতেক মানুষ। তার মধ্যে একটি মধ্যবয়েসী মেয়েকে দেখিয়ে আজিজুল বলল, ‘দাদা, এর নাম বন্দনা মালিক। বাগদি বাড়ির মেয়ে ও বউ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তবু পড়া আর লেখা তার নেশা। আমরা তার একটা বই বের করেছি এবার।’

শুনেছি। মনোযোগ দিই নি। সেই মধ্যবিত্তসুলভ উন্নাসিকতা। লেখাপড়াহীন এক বাগদি মেয়ে কি আর লিখবে! বন্দনা আমার হাতে তুলে দিল তার সদ্য প্রকাশিত ‘জীবনের গীতিকাব্য’। পাতা উল্টে এলাম ‘কথামুখে’। চমকে উঠলাম প্রথম লাইনটি পড়ে। — ‘সন্ধ্যায় ডাক্তার রাউণ্ডে এসে জানালেন, ডায়ালিসিস করতে হবে।’ কোন ভূমিকা নেই, ছোটগল্পের মতো একেবারে নাটকীয়ভাবে আরম্ভ। বন্দনা বলতে চাইছে তার স্বামীর অসুস্থতার কথা। জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে উপস্থিত তার স্বামী গণেশচন্দ্র। বন্দনা ততক্ষণে ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে গেছে মৃত্যুর পদধ্বনির কথা। সে আসছে। নেভার আগে জ্বলে উঠল প্রদীপ। বন্দনা বলছে, ‘উত্তপ্ত শরীর একসময়ে শীতল হয়ে আসে। রাত্রি গভীর। সারাটা রাত বুকের উষ্মতায় জড়িয়ে তোমায় নিয়ে স্মৃতিময় জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সবে চোখটা লেগেছে, হঠাৎ শীতল হাতখানি আমাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে আরও খুব কাছে এসে ক’ফোঁটা চোখের জল আমার বুকের মধ্যে গড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলে অনাগত আগামীতে আমার একলা চলার ছাড়পত্র।’ এ যেন জীবনের গীতিকাব্যে মৃত্যুর কথা।
এই গদ্য লিখছে এক প্রথাগত শিক্ষাহীনা নারী! বিস্ময়, বিস্ময়। নিরাভরণ গদ্য অথচ কাব্যসুরভিত। এই গদ্য ধারণ করে আছে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা নিটোল ও আন্তরিক ভাব ও ভাবনা। বইটির পাতা উল্টে দেখলাম অবশিষ্ট লেখাগুলি কবিতায় লেখা। সেখানেও আছে জীবনের গীতিকাব্য। আছে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর স্মৃতিচারণ। বন্দনা নিঃসন্দেহে কবি। লেখাগুলোর মধ্যে তার ঝলক আছে। ‘চোখের কোণে রক্ত ফোঁটা/মনের কোণে ক্ষত’, ‘খেয়ালখুশির ময়ুরপঙ্খী ভাসছে ও অন্তরে’, ‘মেঘ জমেছে বুকের ভেতর বজ্র হাহাকার’, ‘মন হারাবে মনের মানুষ শ্রাবণ বরষায়’, ‘অভিমানের বাঁধ ভেঙেছে তাই খেয়েছো বিষ’, ‘বাতাসে উড়িয়ে ছাই/যাচ্ছো চলে অন্তরালে একা’, ‘কালো হরফ গুনগুনিয়ে গাইছে অনেক ব্যথা’, ‘রৌদ্রদুপুরে সূর্য ডুবিছে/এসেছে সন্ধ্যাবেলা’, ‘তোমায় সব দিয়ে আমি নদী হতে চাই’ — এসব মনকে স্পর্শ করে যায়। বোঝা যায় কবিতা তার আসে। কবিতা সে লিখতে জানে। তবু আমার কেন যেন মনে হল জীবনের এই গীতিকাব্য বন্দনা তার নির্ভার গদ্যে লিখলে ভালো হত।
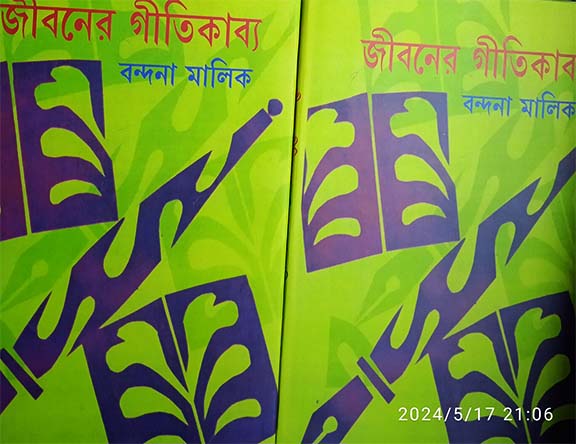
আমি বন্দনার লেখার গুণাগুণ বিচার করতে বসিনি। আমি তার জীবনযুদ্ধের কথাই বলব। গরীবঘরের এই নারী এক যোদ্ধা। কঠিন তার লড়াই। আশ্চর্যের কথা, লড়াইটা সাহিত্যের জন্য। ও, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাবুমশাইরা, চমকে উঠলেন তো আমার কথা শুনে! সাহিত্যের জন্য লড়াই করছে এক বাগদি ঘরের চালচুলোহীন কৃষ্ণকলি মেয়ে! এ কেমন কথা!
সে লড়াইএর কথা বলব বইকি। তবে তার আগে বন্দনার বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক।
বন্দনার বাপের বাড়ি বর্ধমানের সাহাপুর পর্বতপুরে। তার বাবা ধীরেনচন্দ্র মালিক, মা ললিতা মালিক। অর্চনা ও ঝরনা তার দুই বোন। নুন আনতে পান্তা ফুরায় যে সংসারে সেখানে লেখাপড়া বিলাসিতা বইকি। তাই কোনরকমে প্রাথমিক শিক্ষার পরে বন্দনাকে নিযুক্ত হতে হয় ঘর-সংসারের কাজে। কাঠকুটো জোগাড় করে, মাঠে যায় গরু-ছাগল নিয়ে। তবে তার মায়ের একটা নীরব প্রেরণা কাজ করে যায় নীরবে নিভৃতে। পড়ো, জানো। সেই থেকে তৈরি হবে যায় পড়ার অভ্যেস। যেখানে যা পাওয়া যায় –টুকরো কাগজ, ছেঁড়া বইএর পাতা, গোগ্রাসে পড়ে বন্দনা। পড়তে পড়তে মনে হয় নিজের মনের ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করার কথা। শুরু হল কবিতা লেখা। বৃন্দাবন ঘোষ নামক এক মাস্টারমশাই (ইনি আর এক অদ্ভুত মানুষ, বারান্তরে এাঁর কথা বলতেই হবে আমাকে) উসকে দেন বন্দনার মনের ইচ্ছাকে।

ষোলো বছর বয়েসে বন্দনার বিয়ে হয়ে গেল হুগলি জেলার খাজুরদহ গ্রামের গণেশচন্দ্র মালিকের সঙ্গে। তার বিবাহিত জীবন ছিল সুখের। সহমর্মী ছিল গণেশ। কিন্তু লেখালিখির ব্যাপারটা কেমনভাবে নেবে স্বামী, সে সংশয় ছিল বন্দনার। সে তাই রাতের বেলা সকলে ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেত ছাদের কোণে। লম্ফের আলোয় লিখে যেত নিজের আনন্দে। নিজের লেখা পড়ে শোনাত নিজেকে। মাস্টারমশাই বলে দিয়েছিলেন, ‘নিজের লেখা নিজে পড়বে, নিজে শুনবে, লেখা থামাবে না।’ এই করতে করতে বন্দনা তার একটা কবিতা একদিন পাঠিয়ে দিল এক পত্রিকায়। কবিতার নাম ‘ভাতের অধিকার’। ‘শ্যামদুর্বা’ পত্রিকায় প্রকাশিত সেই কবিতা দেখে ফেলল তার স্বামী। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিরূপ হওয়া তো দূরের কথা, গণেশচন্দ্র আনন্দে আত্মহারা। সেও বলল, ‘থামবে না তুমি যত সংকট আসুক না কেন’। স্বামীর সঙ্গে চাষের কাজে মাঠে যেত বন্দনা। রোদঝলসানো সেই মাঠ তাকে দিত লেখার প্রেরণা। রাতের অন্ধকার যখন নিবিড় হয়ে উঠত, তখন লম্ফের আলোয় বন্দনা লিখত তার মনের কথা। কল্পনার মায়াজাল নয়, লিখত সে নিজের জীবনের কথা, তার সুখ-দুঃখ, তার আলো-অন্ধকারের কথা।
অকালে চলে গেল স্বামী। ছেলে-মেয়েকে (সুমন আর মৌমিতা) মানুষ করতে হবে। সংসারের জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিল বন্দনা। চাষের কাজে সময় কাটল মাঠে। রান্না-বান্না, হাট-বাজার। ছেলে-মেয়ের দেখা-শোনা। সব করে বন্দনা। হাসিমুখে। আর নিশুতি রাতের অন্ধকারে লম্ফের আলোয় সাদা খাতার উপরে কালো কালির আঁচড় টেনে যায়। যা সে দেখেছে, যা সে অনুভব করেছে, প্রকাশ করার চেষ্টা করে যায়। প্রকাশ করে তার মাতৃভাষায়। বাংলায়। ঘরে-বাইরের আক্রমণে যে বাংলাভাষার নাভিশ্বাস, সে বাংলা বেঁচে থাকে বন্দনাদের সাধনায়।
সাধনা? সাহিত্যের সাধনা?
তাছাড়া আর কি!
সাহিত্যের সাধনা। সাহিত্যের জন্য লড়াই।
ও, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাবুমশাইরা, এই বন্দনাদের আপনারা চেনেন? এদের মতো লড়াই করে সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কি আপনাদের করতে হয়েছে? নাকি, ভাবের ঘরে চুরি করতে করতে আপনাদের দিন কাবার?
ভাবুন না একটু, ভাবুন, ভাবুন।
যদি পারেন, বন্দনাদের একটু তুলে ধরুন।
কিছু ব্যতিক্রম বাদে পৃথিবীর সব প্রতিভাই অতি
সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছে।তারই এক অনন্য উদাহরণ এই কাব্য যোদ্ধা নারী। তার কয়েকটি কবিতা আমি পড়লাম যা প্রথা বিরোধী।
সমকালীন বাস্তবতার যে লেখচিত্র তিনি এঁকেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।জীবীকার কাছে যে জীবন কখনো হারে না তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তথাকথিত কবি সমাজকে।
আমি তার শব্দচয়নে অভিভূত– বাক্য বিন্যাসে আনন্দিত।
অনেক অনেক শুভকামনা রইল এই কলম যোদ্ধার প্রতি।
আর আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
বন্দনা এখন আর শুধু বাগদীর নয় বাঙালির মেয়ে, মিষ্টি লেখিকা। বন্দনা কে চেনার যেটুকু সুযোগ হয়েছে তাতে বলতে লড়াইয়ের আর এক প্রতীক বন্দনা। উপরোক্ত লেখকের জ্ঞাতার্থে এটুকু জানাই আমি সব সময় বন্দনার সাহিত্যের বন্দনা চাই। বন্দনা আরও বন্দিত হোক বাগচীর ঘেরাটোপে নয় আদর্শ লেখিকা হিসেবে।
সেখ আব্দুল মান্নান, কলকাতা।
ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ ।
বন্দনা মালিকের জন্য অনেক শুভকামনা রইল 🎉🎉🎉🎉
ধন্যবাদ শেখ আবদুল মান্নান ।
ধন্যবাদ সৈয়দ হামিদুর রহমান ।