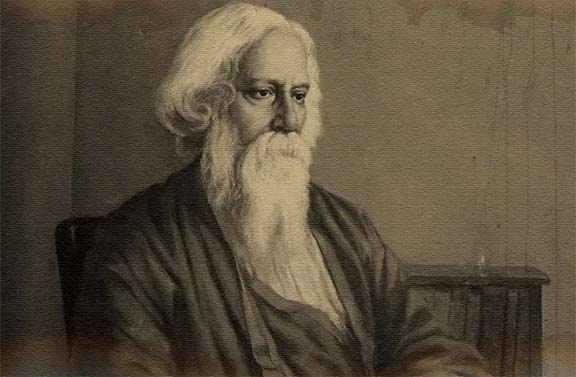
গত শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পাকিস্তানে জোড়া আক্রমণে বিদ্ধ হয়েছিলেন। একদিকে ছিলেন পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্বের সমর্থকরা এবং অন্যদিকে মার্কসবাদীরা। এঁদের মধ্যে নীতিগত কোন মিল ছিল না, কিন্তু আক্রমণটা হয়েছিল একই সময়ে।
রবীন্দ্রনাথকে তখনকার মার্কসবাদীরা যে আক্রমণ করেছিলেন, তার ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই রকম : —
১৯৪৮ সালে নতুন করে ‘মার্কসবাদী’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তার সম্পাদক ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ভবানী সেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল রবীন্দ্র গুপ্ত। ভবানী সেনের নেতৃত্বে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে মতবাদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হত ‘মার্কসবাদী’ পত্রিকাটিকে।
এই পত্রিকায় ‘প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা’ নামক প্রবন্ধে (পঞ্চম সংকলন, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১২৫-১৭২) তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেন তার মূল কথাগুলি হল : —
ক] উপনিষদের যে মায়াবাদ রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা, তা শ্রেণি সংগ্রামের ঠিক বিপরীত। এত বড় শক্তিশালী অস্ত্র বুর্জোয়ারাও আবিষ্কার করতে পারে নি। সমাজতন্ত্র রবীন্দ্র দর্শনের বিরোধী।
খ] ১৮৭৫ সালের পর থেকে ভারতবর্ষে যে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণির আবির্ভাব ঘটল, রবীন্দ্রনাথ তাদেরই প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধালাভ, সমাজের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনে অনীহা, গণসংগ্রামের প্রতি বিমুখতা, জমিদারি প্রথা বাঁচিয়ে রেখে সামন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে আপোষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়।
গ] রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল কথা হল এই সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা-শোষণ-অবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই, শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদ করার চেষ্টা অন্যায়। তাঁর এইসব চিন্তা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা; তার সঙ্গে টলস্টয়ের চিন্তার সাদৃশ্য নেই।
ঘ] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় তিনি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত দেখতে পান নি। তিনি হিন্দুর পক্ষ যতটা নিয়েছেন, ততটা মুসলমানের পক্ষ নেন নি।
ঙ] হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত অনেকটা মিলে যায় এবং এর ফলে তিনি গান্ধীর চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, যেন সাভারকরের দীক্ষাগুরু।
চ] রবীন্দ্রদর্শন হল ভারতের শাসকশ্রেণির দর্শন। শাসকশ্রেণিকে আক্রমণ করতে হলে রবীন্দ্রদর্শনকে আক্রমণ করতে হবে। মার্কসবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের প্রচণ্ড বিরোধ, তাই প্রগতি শিবিরে রবীন্দ্রনাথের কোন স্থান হতে পারে না।
ভবানী সেনের এই বক্তব্য তখনকার প্রগতি শিবিরে সবাইকে প্রভাবিত না করলেও অনেককেই করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু লেখক ও বুদ্ধিজীবীও প্রভাবিত হয়েছিলেন।
১৯৪০ সালের মাঝামাঝি ঢাকায় গড়ে ওঠে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। সভাপতি ছিলেন কাজি আবদুল ওদুদ। সম্মেলনে রণেশ দাশগুপ্তকে সম্পাদক ও সোমেন চন্দকে সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী জড়িত ছিলেন ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে।
১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে সদরঘাটের ব্যাপ্টিস্ট মিশন হলে ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সোমেন চন্দ সম্পাদক হিসেবে এবং অচ্যুত গোস্বামী সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। সোমেন চন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় স্বল্পদিনের মধ্যে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি যৌথভাবে ফ্যাসিবাদবিরোধী জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রগতি লেখক সংঘের কর্মকাণ্ড বিকশিত হয়। প্রতি রবিবার সকাল ১১টায় মধুর রেস্তোরাঁয় বসত সংঘের আসর। উপস্থিত থাকতেন মুনীর চৌধুরী, শামসুর রহমান খান, সুলতানুজ্জামান খান, অরবিন্দ সেন, মদনমোহন বসাক, আমিনুল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গির, ওসমান জামাল, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এ এইচ শাহাদাৎ উল্লাহ। মূল সংগঠক ছিলেন মুনীর চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত ও অরবিন্দ সেন।
ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের কয়েকজন সদস্যের উপর পড়েছিল ভবানী সেনের রবীন্দ্র-বিরোধী তত্ত্বের প্রভাব। আনিসুজ্জামান লিখেছেন : —
“রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকের অভাব কখনও ছিল না, পূর্ববঙ্গেও তার অভাব হয় নি, বিশেষত উপনিবেশ-উত্তরকালে। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে নীতি ও কর্মপন্থা গৃহীত হয় তার অনুসরণে ভবানী সেন দেন সাংস্কৃতিক তত্ত্ব। তাতে আরও অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা হয় প্রতিক্রিয়াশীল বলে। তারই প্রভাবে পূর্ব বাংলায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ রবীন্দ্রনাথকে গণ্য করলেন প্রগতিবিরোধী বুর্জোয়া হিসেবে। মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মুতি, আলাউদ্দিন আল আজাদ — এঁদের সবারই এই মত। দ্বিমত প্রকাশ করেন সংগঠনের সভাপতি অজিতকুমার গুহ — তিনি এখন সংঘ থেকে দূরে সরে গেলেন। কারাগারে নিরাপত্তা বন্দি বামপন্থী কর্মিদের মধ্যেও এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। সবাই ভবানী সেনের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত, কেবল দ্বিমত পোষণ করলেন রণেশ দাশগুপ্ত।” (চলবে)
লেখক সিনিয়র ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক