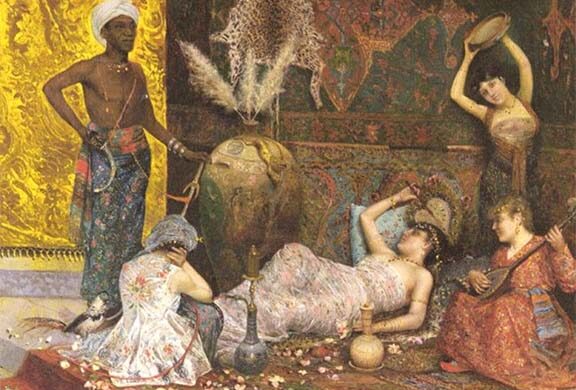
বাংলার মত দারুলইসলামের প্রান্ত এলাকাগুলোয় বালকদের খোজাকরণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় শল্য চিকিৎসার কাজ করতেন স্থানীয় অমুসলমান বৈদ্য আর গ্রামীন চিকিৎসকেরা। বাংলার মূলত সিলেট এবং ঘোড়াঘাট অঞ্চলেই খোজাকারীরা অপহৃত, কিনে আনা, বেপথে চলে যাওয়া বালকদের মুসলমান দাস ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে দিত। তবে বাংলার বাইরে মুসলমান ব্যবসায়ীরা শিশুদের খোজাকরণের কাজ নিজেরাই করিয়ে নিত স্থানীয় এলাকার সংখ্যালঘু চিকিৎসকেদের কাজ লাগিয়ে যেমন মিশরে এই কাজটা করত কোপ্টিক সন্ন্যাসীরা।
জাহাঙ্গির ‘খোজা নজর’ [বকেয়া রাজস্বের দায় খোজাদের দান করে মেটানোর প্রথা] দেওয়ার প্রথাকে ঘেন্না প্রকাশ করে বাংলার সুবাদার কোকাভাই ইসলাম খানকে ১৬০৮এ লিখলেন সিলেট থেকে রাজস্ব না দিয়ে কেন্দ্রিয় খাজাঞ্চিতে খোজা/হিজড়া পাঠানোর প্রথাটি সুবার বিভিন্ন সরকারের কাছারিগুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই কাজকে মুঘল আমলাদের স্বাভাবিক কাজ বলে বলে মনে হচ্ছে, একে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জাহাঙ্গির নির্দেশ দিলেন খোজাকরণ করা মৃত্যুদণ্ডসম অপরাধ। স্বয়ং সুবাদারকে উদ্যোগী হয়ে খোজাদারদের কবলে থাকা বালক খোজাদের এর আগে, বিশেষ করে আকবরের সময় প্রথাটি নিষদ্ধ করার উদ্যম ব্যর্থ হলেও জেদী সম্রাট জাহাঙ্গিরের কঠোর নির্দেশে বাংলায় খোজাকরণ করার উদ্যমে কিছুটা ধাক্কা লাগল। ঐতিহাসিকেরা বলছেন পূর্ণ বয়স্ক হিজড়ে বা খোজাদের সম্বন্ধে জাহাঙ্গির কোনও নির্দেশ দেন নি।
তুজুকই জাহাঙ্গিরিতে বহুবারই খোজাদের বিষয় নিয়ে লিখেছেন সম্রাট। ১৬১০-এ বিহারের সুবাদার আফজল খান প্রথাটি সম্রাট নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও, আইনভঙ্গ করে জোর করে খোজাকরণ করার অভিযোগে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রিয় দরবারে পাঠালেন তিনি। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। ১৬১৩-য় বাংলা থেকে ৫০ জন হিজড়াকে আগরার দরবারে নজর হিসেবে পাঠালেন ইসলাম খান। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছ’বছর আগে পাদশার নির্দেশে বিভিন্ন আমীরের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা খোজা/হিজড়ে। ইসলাম খানের পরে বাংলার সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গ ১৬২১-এ দুজন খোজা আর একজন উভয়লিঙ্গকে পাঠান।
জাহাঙ্গিরের খোজা নিষিদ্ধকরণের উদ্যম সত্ত্বেও খোজাদের চাহিদা কমল না। আকবর এবং স্বয়ং জাহাঙ্গিরের দরবারের এক উচ্চপদস্থ আমলা সৈয়দ খান চুঘতাই, বাংলা, বিহার এবং পাঞ্জাবের সুবাদারি দপ্তরে কাজ করেছেন। তিনি নাকী ১২,০০০ খোজা নিয়ে এক বিশৃঙ্খল পরিবার চালাতেন। মুঘল আমলের শীর্ষ সময়ে, সমগ্র সপ্তদশ শতক জুড়ে খোজা ব্যবসার বিন্দুমাত্র পতন ঘটে নি। খোজা নিষিদ্ধকরণের শাহী ফরমান আসার আগের সময়ে বাংলায় কিছু সময় কাটানো ফরাসি মুসাফির ফ্রাঙ্কো পাইরার্ড বাংলায় বিপুল খোজা ব্যবসার প্রচলন দেখেছিলেন – ‘বাংলার অন্যতম বড় ব্যবসা-পণ্য ছিল দাসেরা। এখানে কিছু জায়গায় [সিলেট?] রাজার নির্দেশে বাবা তার পুত্রকে বিক্রি করে রাজাকে উপহার দিত; ভারতের অধিকাংশ দাস তাই এই অঞ্চল থেকে আসত। অধিকাংশ ব্যবসায়ী লুঠ করা বালকদের খোজা করত। শুধু তাদের অন্ডোকোষই কাটা হত না, সামগ্রিকভাবে যৌনাঙ্গই দেহাঙ্গ থেকে উপড়ে ফেলা হত। আমি এরকম কয়েকজনকে দেখেছি, যাদের দেহ থেকে জল বের করবার জন্যে একটি মাত্র ফুটো আছে — কোনও জননাঙ্গই নেই। এদের মহিলাদের সুরক্ষার কাজে নিয়োগ করা হত। তাছাড়া গৃহস্থর বাড়ির নিরাপত্তাও তাদের হাতে ছিল। গৃহস্থরা এদের যতটা বিশ্বাস করত, তার স্ত্রীকে ততটা বিশ্বাস করত না’।
সমস্যা হল, খোজা ব্যবসা বা খোজাদের নিয়ে এর থেকে বেশি তথ্য আমরা পাই না। শুধু আবুলফজলের লেখজা আইনইআকবরিতে বলা আছে বাংলা থেকে ৩ ধরণের খোজা বাজারে আসত — এদের কারোর নাম সান্ডালি, কারোর বাদামি আর কারোর বা কাফুরি। প্রথম ধরণের খোজাদের গোটা জননাঙ্গ কাটা থাকত। তাদের আরেক নাম আলতাসি। পরের ধরণের খোজাদের লিঙ্গ থাকলেও একটা অংশ কিছুটা কাজ করত, একটা অংশ করত না। তৃতীয় ধরণের খোজাদের হয় অন্ডকোষ কাটা থাকত বা সেটিকে অকেজো করে বিচূর্ণ করে দেওয়া হত। পাঠককে নিশ্চিই সান্ডালি, বাদামি আর কাফুরির নামে বোঝাতে হবে না — সান্ডালি অর্থে চন্দনগন্ধী, বাদামী অর্থে কজুবাদামের বর্ণের, আর কাফুরি অর্থে কর্পূরগন্ধী। আগেই আমরা বলেছি হিজড়া বা খোজাদের এই সব নামে ডাকা হত এবং এগুলো হয়ত তাদের শ্রেণীবিভাগও বোঝাত। কাফুর অর্থে সাদা, কালো দাসেদের ডাক নাম। সান্ডালি হল হাল্কা রঙের চামড়ার খোজা।
খোজা ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ মুসলমান। তারা খোজা করার জন্যে বালক কিনত হয় পিতামাতা বা ছেলেধরাদের থেকে। আর ব্যবসায়ী যদি খোজা বালক না পেত, তাহলে তাকে বালকটিকে খোজা করার ব্যবস্থা করতে হত। খোজা করার কাজ করত অমুসলমান হিন্দু বৈদ্যরা। খোজা করে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে পরিবারের কর্তারা বাচ্চাদের বিক্রি করে দিত সে যুক্তি আজ ৪০০ বছর পর বোঝা মুশকিল — হয়ত গরীবি থেকে মুক্তি, হয়ত খোজাদের প্রশাসনের উচ্চপদে ওঠার পরের সামাজিক সম্মান অর্জনের হাতছানি, হয়ত বা রাজস্ব দিতে না পারার অক্ষমতা (পরে আমরা আলোচনা করব এই বিষয়টা; বাদাউনি, মনরিকে, বার্নিয়ে, মানুচি প্রত্যেক মুঘল সমালোচক বলছেন মুঘল আমলে রাজস্ব বা দিতে পারলে মানুষ নিলাম করে রাজস্ব আদায় করা হত)। সে সময় খোজারা যেহেতু বিপুল সামাজিক সম্মান এবং অর্থ উপার্জন করত, ফলে পরিবারের এক সদস্যকে খোজা করার অর্থ হল সম্ভাব্য লটারির প্রথম পুরষ্কার জেতার সুযোগ নেওয়া। এরকম একটা উদাহরণ মুসাফির মানুচি সূত্রে পাচ্ছি।
আওরঙ্গজেব খোজা মুতামিদ বা ইতিবরকে শাহজাহানএর কারাবাসের সময় কারাগার পাহারা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইতিবর খানের জন্ম বাংলায়। বাল্য বয়সের খোজা হয়ে মুঘল শাহী প্রশাসনে তিনি ঢুকেপড়ে উচ্চপদে আরোহন করেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের উত্তর সময়ে তিনি দরবারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত হিসেবে গণ্য হতেন। খোজা পুত্রের নাম সাম্রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে, পিতামাতার কানেও পুত্রের খ্যাতি কানে গেল। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর এই প্রথম খোজা মুতামিদের বাবা-মা বাংলা থেকে আগরায় এলেন পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পিতামাতা যেহেতু তাকে শৈশবের সব থেকে দামি অনুভূতি, পরিবারের সদস্যদের ভালবাসা থেকে বিচ্যুত করেছেন, তাই তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রাসাদের দরজায় বহু দিন অপেক্ষা করিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেন। হয়ত অতিরঞ্জিত, কিন্তু বাচ্চাদের খোজা করার তাগিদের একটা যুক্তি পাওয়া গেল।
কিন্তু পৌরাণিক আমল থেকে চলা বাংলার এই ব্যবসা কীভাবে বন্ধ হয়ে গেল তার কোনও সূত্র ইতিহাসের পাতায় অনুপস্থিত। তবুও উনবিংশ শতাব্দের উপনিবেশ আমল পর্যন্ত বাংলায় সীমিতভাবে হলেও দাস ব্যবসা চলেছে। মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও বাংলা অবধ বা হায়দারাবাদের মত সাকসেসর স্টেটগুলিতে দাসের চাহিদা আদৌ কমেছিল, এমন কোনও উদাহরণ পাচ্ছি না। তবে মুর্শিদাবাদ দরবারে তুলনামূলকভাবে দাসের উপস্থিত কম ছিল। অবধের দরবারে দাসেদের বহু উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে বহু ইওরোপিয় লেখায়। ১৮৫৬এর পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ওয়াজেদ আলি শাহ গার্ডেনরিচে বন্দী হওয়ার পর বাংলায় এই ব্যবসার ইতি ঘটে। (চলবে)