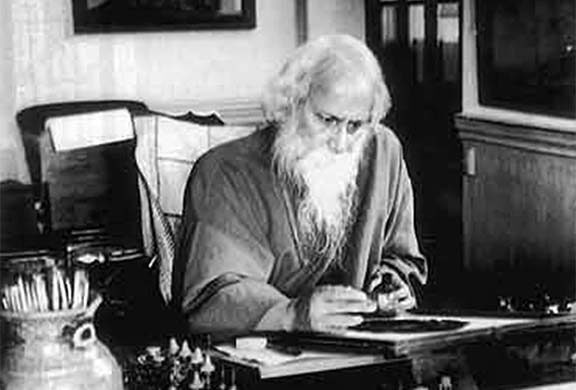
তেত্রিশ-বৎসর ছয়-মাস বয়সে প্রকাশিত সাধনা (নভেম্বর-১৮৯৪) পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও প্রেসিডেন্সির স্নাতক ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথকে তার তিন-বৎসর পূর্বে সাধনা (নভেম্বর-১৮৯১) সম্পাদকের পদে বসিয়ে ব-কলমে সাধনা-সম্পাদনা করতেন তিরিশ-বৎসর ছয়-মাস বয়সের সুধীন্দ্র-পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ প্রকাশ্যত না হলেও অপ্রকাশ্যে ১৮৯১-খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। সাধনার প্রকাশ-অবসান ঘটে কার্তিক-১৩০২ (নভেম্বর-১৮৯৫)-এ। তারপর দুই-বৎসর পাঁচ-মাস পর, দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারতী (বৈশাখ-১৩০৫ / এপ্রিল-১৮৯৮)র। এক-বছর ভারতী-সম্পাদনার পর তার দায়িত্ব ত্যাগ করেন চৈত্র-১৩০৫ (এপ্রিল-১৮৯৯)-এ। তারপরের দুই বৎসর তিনি আর কোনও সাময়িকপত্রের সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন নি। বৈশাখ-১৩০৮ (এপ্রিল-১৯০১)-এ পুনরায় বঙ্গদর্শন নবপর্যায়-এর সম্পাদকতা শুরু করেন। টানা পাঁচবছর বঙ্গদর্শন নবপর্যায় সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ। বৈশাখ-১৩০৮ (এপ্রিল-১৯০১) থেকে চৈত্র-১৩১২ (এপ্রিল-১৯০৬) পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন নবপর্যায়-এর শেষ বছর অর্থাৎ বৈশাখ-১৩১২ (এপ্রিল-১৯০৫) থেকে চৈত্র-১৩১৩ (মার্চ-১৯০৬)-এই কালপর্বে পুরোপুরি একবছর তিনি একই সঙ্গে বঙ্গদর্শন নবপর্যায় এবং ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদন-কর্ম চালনা করেন। একবছর একইসঙ্গে দুটি পত্রিকা সম্পাদনার পর, চৈত্র ১৩১২ (এপ্রিল-১৯০৬)-তে বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের সম্পাদন-দায়িত্বভার ত্যাগ করেন, কিন্তু ভাণ্ডার-সম্পাদনা চালিয়ে যান। দুই-বৎসর এক-মাস ভাণ্ডার-সম্পাদনার পর বৈশাখ-১৩১৪ (এপ্রিল-১৯০৭)-তে ভাণ্ডার সম্পাদন-ভার ত্যাগ করেন। অর্থাৎ বৈশাখ-১৩০৮ (এপ্রিল-১৯০১) থেকে বৈশাখ-১৩১৪, (এপ্রিল-১৯০৭) পর্যন্ত, একটানা ছয়-বৎসর এক-মাস বঙ্গদর্শন নবপর্যায় এবং ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদনাকর্ম পরিচালনা করেন সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ। ভাণ্ডার-এর দায়িত্বভার ত্যাগ করার পরের চার-বছর (মে-১৯০৭ থেকে মার্চ-১৯১১) তিনি আর কোনও সাময়িকপত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন নি। বৈশাখ-১৩১৮ (এপ্রিল-১৯১১) থেকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেন চার-বছর। অর্থাৎ চৈত্র-১৩২১ (এপ্রিল-১৯১৫) পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা-সম্পাদনার পর বাংলা সময়িকপত্র-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সম্পাদক-জীবনের সমাপ্তি ঘটে। যদিও আরও আটবছর পর, ১৯২৩-এর এপ্রিল-এ রবীন্দ্রনাথকে আমরা ‘এডিটরি’ করতে দেখি Visva-Bharati Quarterly নামক একটি ইংরেজি সাময়িকপত্রের প্রথম সংখ্যাটির।
ত্রিশ-বৎসর ছয়-মাস বয়সে অপ্রকাশ্যে সাধনা-সম্পাদনার যে দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, ভারতী, বঙ্গদর্শন–নবপর্যায়, ভাণ্ডার পার করে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার দায়িত্ব যখন ত্যাগ করেন, তখন তাঁর তিপ্পান্ন-বৎসর এগারো-মাস বয়েস। অর্থাৎ নভেম্বর-১৮৯১ থেকে এপ্রিল-১৯১৫–এই তেইশ-বৎসর পাঁচ-মাস কালপর্বে, বিচ্ছিন্ন ব্যবধানে সর্বমোট বারো-বৎসর এক-মাস প্রত্যক্ষত যুক্ত ছিলেন পাঁচ-পাঁচটি সাময়িকপত্র-সম্পাদনায়। এই সময়কালে সম্পাদিত সাময়িকপত্রের যাবতীয় লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটে সেই সেই পত্রিকার প্রয়োজন অনিবার্যতায়।
রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পাঁচটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল সর্বমোট বারো-বছর এক-মাস কালসীমায়। কিন্তু বৈশাখ-চৈত্র-১৩১২, (এপ্রিল-১৯০৫ – মার্চ-১৯০৬) তে বঙ্গদর্শন নবপর্যায় এবং ভাণ্ডার একই সঙ্গে প্রকাশিত হওয়ায় মোট ১৩-বছর ১-মাস অর্থাৎ সর্বমোট ১৫৭-মাস সম্পাদন-দায়িত্বভার পালন করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৫৭-মাসে পাঁচটি সাময়িকপত্রের মোট ১৪৭-টি সংখ্যা সম্পাদনা করেন তিনি। সাধনা বারো-মাসে প্রকাশিত হয় দশটি সংখ্যা। সাধনার শেষ তিন মাসে তিনটি সংখ্যার বদলে ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক-১৩০২ একত্র একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাধনার একবৎসরে প্রকাশিত-সংখ্যা- দশ। ভারতীর বর্ষব্যাপী রবীন্দ্র-সম্পাদনায় প্রকাশিত-সংখ্যা- দশ। পৌষ ও মাঘ-১৩০৫ এবং ফাল্গুন ও চৈত্র-১৩০৫ -এই চার-মাসে দুটি যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতীর বারো-মাসে দশটি সংখ্যা পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ে কোনও যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি, ফলত পাঁচ-বছরে ষাটটি-সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। ভাণ্ডার সম্পাদনা করেন দুই-বৎসর এক-মাস, অর্থাৎ পঁচিশ-মাস। পঁচিশ-মাসে ভাণ্ডার-এর তিনটি যুগ্ম-সংখ্যা-(ভাদ্র-আশ্বিন-১৩১২, শ্রাবণ-ভাদ্র-১৩১৩, অগ্রহায়ণ-পৌষ-১৩১৩) প্রকাশিত হওয়ায় মোট ২২-টি সংখ্যা সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা সম্পাদনা করেন চার-বৎসর অর্থাৎ আটচল্লিশ-মাস। এই আটচল্লিশ-মাসে তিনটি যুগ্ম-সংখ্যা (আশ্বিন-কার্তিক-১৩১৮, অগ্রহায়ণ-পৌষ-১৩২০, আশ্বিন-কার্তিক-১৩২১) প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি-সংখ্যা সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত পাঁচটি সাময়িকপত্রের ১৪৭-টি সংখ্যায় ‘বিজ্ঞাপন’, ‘ভ্রম সংশোধন’, ‘আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব’ এবং ‘প্রশ্ন’ প্রভৃতি প্রকাশিত হয় ৫৬-টি। সর্বমোট ১০০-টি রচনায় রচনাকারের নাম প্রকাশিত হয়নি। রচনাকারের নাম পাওয়া যায় ১৭০১-টি রচনায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পাঁচটি সাময়িকপত্রে মোট ১৮০১-টি রচনা প্রকাশিত হয়। স্বয়ং সম্পাদক লিখেছিলেন ৫৭৩-টি রচনা। সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য লেখকেরা (যাঁদের রচনায় লেখক-নাম প্রকাশিত হয়েছিল) লেখেন ১১২৮-টি রচনা। সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের লেখা– ২৫৩-টি। সম্পাদক এবং ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের মোটরচনা ৫৭৩ + ২৫৩ = ৮২৬-টি। সম্পাদক ও ঠাকুর-পরিবারভুক্ত অন্যান্য সদস্য ভিন্ন, আর যে অন্যান্য লেখকেরা লিখেছিলেন, তাঁদের রচনা-সংখ্যা – ৮৭৫ । সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় আমরা মোট ২৩৬-জন প্রকাশিত-নামা লেখকের রচনা প্রকাশিত হতে দেখি পাঁচটি-সাময়িকপত্রে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, একশোটি রচনায় রচনাকারের নাম প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত। যদিও নামহীন-অস্বাক্ষরিত রচনাগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে।
আমাদের অনুসন্ধান সম্পাদক-ব্যতীত অন্যান্য ২৩৬-জন লেখক-লেখিকাদের নিয়ে। তাঁরা কারা? কী তাঁদের পরিচয়? সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন্ কোন্ সূত্রে তাঁদের যোগাযোগ? সম্পাদন-কালে এতজন লেখকের রচনা কীভাবে তিনি সংগ্রহ করলেন? লেখককুলের উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে আমরা তাঁদের কয়েকটি বর্গে ভাগ করে নিয়ে সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছি—
ক. ঠাকুরবাড়ি এবং এই পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়–সম্বন্ধ–যুক্ত লেখকেরা:
সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথের পরিবার তৎকালীন বাংলাদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্রে ও নানান সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়েরা সম্পাদকের আহবানে সাড়া দিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যে পাঁচটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেই পত্রিকাগুলিতে ঠাকুরবাড়ির সদস্য-আত্মীয় কুড়ি-জন লেখকের সন্ধান পাই আমরা। এই কুড়িজন সদস্যের ২৫৩-টি রচনা সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের মধ্যে যেমন ছিলেন অগ্রজ-সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ। সহোদরা স্বর্ণকুমারীদেবী। ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ। ভাগিনেয়ী সরলাদেবী, হিরন্ময়ীদেবী। সম্পাদকের দুই-কন্যা অতসীলতা, মাধুরীলতা, জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতাদেবী (বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়-স্ত্রী)। ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়-সম্বন্ধযুক্ত আরও তিন জামাতার সন্ধান পাই আমরা, যাঁরা আদতে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জামাতা হলেও হৃদ্যতায় তাঁরা বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। এঁরা হলেন আশুতোষ চৌধুরী (সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের জামাতা, প্রতিভাদেবীর স্বামী)। প্রমথ চৌধুরী (মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথের জামাতা, ইন্দিরাদেবীর স্বামী) এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা, সরোজার স্বামী)।
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িকপত্রে ঠাকুরবাড়ির সদস্য ও আত্মীয়, যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা হলেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, হেমলতা দেবী, অতসীলতা দেবী, মাধুরীলতা দেবী, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
খ. অনাত্মীয়, অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং সাহিত্য–আগ্রহী বন্ধু–মহল:
সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ শুধু ঠাকুরপরিবারের সদস্যদের লেখা নিয়েই বকলমে সাধনার প্রথম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ-১২৯৮) সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। সময়ের অমোঘ নিয়মে ঠাকুরপরিবার ব্যতিরেকে অনাত্মীয়, অন্তরঙ্গ সাহিত্যানুরাগী-সুহৃদদের লেখা সংগ্রহ শুরু করেন। আর, সেখান থেকেই সূচিত হয় রবীন্দ্র-লেখকগোষ্ঠীর নির্মাণ। তেইশ-বছর পাঁচ-মাস সময়ের বিস্তৃত সম্পাদন-কালপর্বে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়ে ওঠেন ‘কাছের মানুষ’। যাঁদের সঙ্গে হয়তো তাঁর রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু ‘সাহিত্য’কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আত্মীয়তা। সেরকম বেশ কিছু মানুষের সন্ধান পাই আমরা, যাঁদের কাছ থেকে সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন ৮২-টি রচনা। সম্পাদকের অনাত্মীয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুরা হলেন— কৃষ্ণবিহারী সেন, কেদারনাথ দাশগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, জগদানন্দ রায়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র দেববর্মা, মোহিতচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, শরৎকুমারী দেবী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।
গ. সমকালীন বিখ্যাত লেখক-কবি-সমালোচক:
সাময়িকপত্র সম্পাদনা করতে গেলে সমকালীন খ্যাতনামা লেখক-কবি-সমালোচকদের রচনা সংগ্রহ এবং প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য। অনেক ক্ষেত্রে রচনার বিষয়বস্তু নয়, প্রখ্যাত লেখকদের ‘নাম’ এবং ‘সুনাম’ পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি করে, পত্রিকার সুখ্যাতি প্রচারে সহায়ক হয়। দুই-যুগ কাল-পর্বের একযুগ-একমাস সময় পত্রিকা-সম্পাদনে অতিবাহিত করেন সম্পাদক-স্রষ্টা। স্বভাবতই সমকালীন বিখ্যাত লেখকদের রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন নিজ-সম্পাদনায়। সমকালীন প্রখ্যাত লেখকেরা, কেউ সম্পাদকের সমকালীন, কেউ অগ্রজ, কেউ অনুজ, এঁরা সকলেই সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় লেখা প্রকাশ করে বহুসংখ্যক পাঠকের কাছে তাঁদের বার্তা পৌঁছে দিত সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা যে শুধু রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় লিখেছিলেন, এমন নয়। পূর্বেই তাঁদের রচনার সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অনেককেই রবীন্দ্রগোষ্ঠীভুক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালীন খ্যাতনামা লেখকেরা হলেন—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অতুলচন্দ্র ঘোষ [ওরফে বীরেশ্বর গোস্বামী], উপেন্দ্রকিশোর রায় [চৌধুরী], ক্ষিতিমোহন সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র সেন, নিখিলনাথ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [কথা সাহিত্যিক], বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিধুশেখর শাস্ত্রী [শর্ম্মা/ভট্টাচার্য], বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যোগেশচন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শরৎকুমার রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুকুমার রায় [চৌধুরী], হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (চলবে)
লেখক, শুভাশিস মণ্ডল, সহ শিক্ষক (বাংলা), কসবা চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল, কসবা, কলকাতা।