
বাংলায় বৈষ্ণবীয় ধারায় পটচিত্র অঙ্কন করার রীতিও যথেষ্ট। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে শুরু করে নগর কীর্তনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে পট আঁকা হয়েছে । এই সকল পটচিত্র আবার কাহিনী আকারে মানুষের মধ্যে পরিবেশিত হওয়ার কথাও জানা যায়। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের পরবর্তীতে বৈষ্ণবীয় ধারার পটের প্রসার ঘটে বেশি। নগর কীর্তনের মতো পটের গানও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে যথেষ্ট প্রভাব রাখে।
বাংলার পৌরাণিক আখ্যানগুলো কোনো অতিলৌকিক জীবনের প্রশ্রয় পায়নি। সাধারণ গৃহী জীবনের কথাই সেখানে বিবৃত হয়েছে। যেমন শিব দেবতার অনেক কাহিনী পটের গানে আশ্রয় পেয়েছে। শিব এখানে কোনো অতিলৌকিক জগতের দেবতা নন। তিনি একজন সাধারণ গৃহস্থ। যখন তিনি.ক্ষেতে চাষ করতে গেছেন তখন তার স্ত্রী দুর্গা তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছেন। তিনি তাঁকে দেখার জন্য অসি’র চিত্ত নিয়ে নারদের নিকট তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন। এই চিত্রে নিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের প্রতিচ্ছবিই পটের চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই সেখানে মাহেশ্বরও একজন সাধারণ কৃষকের চরিত্রে অঙ্কিত। শিবের কাহিনী নির্ভর একটি পটের গান এমন-
ব্যাঘ্রের আসনে বসিলেন যুগপতি
নারদে ডাকিয়া দুর্গা বলিছে বচন ॥
অন্য লোকে চাষ করে ঘুরে আসে ঘর
চাষ করতে গেছে আমার ভোলা মহেশ্বর ॥
উপায় বল মোরে বাছা বুদ্ধি বলো মোরে
তোমার মামা ঘরকে আসে কেমন প্রকারে ॥
নারদ বলে যদি মামী ঘরতে পারো বাগ্দিনী বরণ
রূপেগুণে মামার সঙ্গে হবে দরশন ॥
নারদের কথাটি দুর্গার মনেতে লাগিল
স্বর্গে ছিলেন কামিলা সেদিন মর্ত্তে আসিল ॥
হেদে বলি কামিলা বাটার তাম্বুল খাবি
শীঘ্র করে জাল দড়ি নির্মাণ করিবি ॥
এক ছিলেন কামিলা ঠাকুর দ্বিজ আজ্ঞ পেল
আড়াই দিবসের মধ্যে জাল নির্মাণ হইল ॥
ঘন ঘন পাশ ফেলাই পাশ ফেলাই গিয়ে লেখা নাই
জালিখানটি নির্মান করিলেন কামিলা গোঁসাই ॥
জাল-দড়ি নির্মাণ করে দুর্গার আগে দিল
জাল-দড়ি দেখে দুর্গা হাস্য-বদন হল।
যাও বাছা কামিলা তোমারে দিলাম বর
মৃত্তিকাতে দেউল দালান দেবতা লোকের ঘর ॥

বাংলার পটচিত্র রীতির দুইটি আকৃতি লক্ষ করা যায়। একটি হলো জড়ানো এবং অন্যটি চৌকো। জড়ানো পট ১২ থেকে ২৫ ফুট লম্বা এবং ১ থেকে ৩ ফুট চওড়া হতে পারে। সকল জড়ানো পটই কাহিনী নির্ভর। এক একটি ছবি দেখানো হতো এবং সমবেতভাবে গীত-বদ্য-নৃত্যের মধ্য দিয়ে তা পরিবেশিত হতো। আর চৌকো পটের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করা যায় কলকাতার কলীঘাটে। এই তীর্থকে কেন্দ্র করে পটুয়ারা নান আঙ্গিকে পট অঙ্কন করেছেন। বিভিন্ন উৎসবের সময় বাঙালিরা তীর্থ ভ্রমণ করতে এসে এই পটচিত্র নিয়ে ঘরে ফিরতেন। তবে এই পটচিত্রকে অবলম্বন করে কোনো গীত-বাদ্যের প্রচলন লক্ষ করা যায় না। বিশেষ করে পটের গান জড়ানো পটকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছে।
পট অঙ্কনের কয়েকটি রীতি দেখা যায়। বিশেষ করে পটের গানের জন্য যে পট ব্যবহৃত হতো সেগুলো প্রধানত কাপড়ে আঁকা হতো। কখনো কখনো কাপড়ের উপর কাগজও লাগানো থাকতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাপড়ের পটই ব্যবহৃত হতো। কাপড়ের উপর লাল মাটির প্রলেপ বা গোবর মিশ্রিত মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো। মাটির প্রলেপের পর তেঁতুল বিচি জ্বাল দিয়ে এক প্রকার আঠা তৈরী করে তার উপর লাগানো হতো। তেঁতুল বিচির আঠা লাগিয়ে পট তৈরীর উপযুক্ত জমিন তৈরী করে নেওয়া হতো। পটুয়ারা নিজস্ব পদ্ধতিতে গাছের পাতা, বাঁকল, ইত্যাদির রস-আঠা ব্যবহার করে রঙ তৈরী করতেন। এর সঙ্গে মেশানো হতো তেঁতুল বিচির তৈরী আঠা। বিভিন্ন আখ্যান অনুযায়ী এক একটি পট অঙ্কন করতে এক একজন পটুয়ার এক থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হতো।
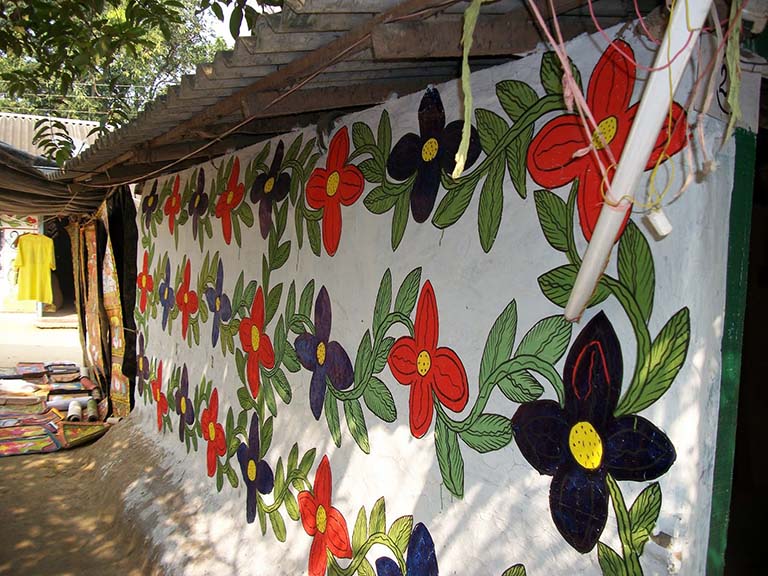
ছবির নাম গাজীর পট
গাজী পীরের উপাখ্যানের বিভিন্ন দৃশ্য সম্বলিত চিত্রকলা গাজীর পট৷ বাংলার এক সময়ের অত্যনত্ম জনপ্রিয় এ লোকচিত্রকলা পটুয়ারা সঙ্গীতযোগে পরিবেশন করত৷ গাজীর পট সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে বাড়ির উঠোনে প্রদর্শিত হত৷ কুশলীলবরা জুড়ি, ঢোল, চটি প্রভৃতি বাজিয়ে গান গায় আর পট প্রদর্শন করে৷ এ সময় পটে অঙ্কিত চিত্রসমূহ একটি লাঠির সাহায্যে নির্দেশ করে তা সুর, তাল ও কথার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়৷ নির্দিষ্ট কোন কাহিনীর পরিবর্তে গাজীর পটের বর্ণনাংশে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে গাজী পীরের মাহাত্ম্য ও অলৌকিক ৰমতা, কৌতুক মিশ্রিত হিতোপদেশ এবং মৃতু্য তথা যমরাজের ভয়৷
পটের চিত্রসমূহ সাধারণত মোটা কাপড়ে অঙ্কিত হয়৷ সমগ্র পটটি মোট পঁচিশটি প্যানেলে বিভক্ত৷ তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় প্যানেলটি বৃহত্৷ এর ওপরে চার ও নিচে তিন সারি প্যানেল থাকে৷ সর্বনিম্ন সারিটি বাদে অন্যসব সারিতেই তিনটি করে প্যানেল থাকে৷ কেন্দ্রীয় প্যানেলে অঙ্কিত হয় বাঘের পিঠে উপবিষ্ট গাজী এবং তার দু’পাশে থাকে মানিক পীর ও কালু পীর৷ ওপর থেকে দ্বিতীয় সারির মাঝে থাকে নাকাড়া বাদনরত ছাওয়াল ফকির এবং তৃতীয় সারির মাঝের প্যানেলে থাকে কেরামতি শিমুল গাছ ও তার ডানে আসাহাতে গাজীর গুণকীর্তনরত দুই মহিলা৷ কেন্দ্রীয় প্যানেলের নিচের সারির মাঝে অঙ্কিত হয় গাজী পীরের ভগ্নী লক্ষ্মী ও তার বাহন পেঁচা৷ দ্বিতীয় সারির ডানদিকের প্যানেলে থাকে মকর মাছের পিঠে উপবিষ্ট গঙ্গা দেবী এবং সর্বনিম্ন সারির বামে থাকে যমদূত, ডানে কালদূত ও মাঝে মানুষের মাথা রন্ধনরত যমরাজের মা৷ প্রতিটি ফ্রেমের চারপাশে সাদার ওপর খয়েরি রঙের শিকল নকশাকৃত বর্ডার থাকে৷

গাজীর পট জড়ানো প্রকৃতির এবং তা সাধারণত মোটা কাপড়ে অঙ্কন করা হয়৷ অঙ্কনের আগে তেঁতুল বিচি বা বেলের আঠা দিয়ে পটের জমিন তৈরি করা হয়; তার ওপর চক পাউডার, তেঁতুল বিচির আঠা ও ইটের গুঁড়ার মিশ্রণের প্রলেপ দেয়া হয়৷ এটি ভালভাবে রোদে শুকানোর পর সমগ্র পটটি নির্দিষ্ট প্যানেলে ভাগ করে শিল্পী বিভিন্ন প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন৷
চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় রঙ নানা ধরনের উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ থেকে সংগৃহীত হয়, যেমন- মশালের ওপর উপুড় করা মাটির সরার কালি থেকে কালো, শঙ্খগুঁড়া থেকে সাদা, সিঁদুর থেকে লাল, হলুদ গুঁড়া থেকে হলুদ, গোপীমাটি থেকে মেটে হলুদ এবং নীল গাছ থেকে নীল রঙ সংগ্রহ করা হয়৷ ছাগল বা ভেড়ার লোম দিয়ে শিল্পী নিজেই তুলি তৈরি করেন৷ বর্তমানে অবশ্য বাজারে প্রাপ্ত রাসায়নিক রঙ এবং বিভিন্ন ধরনের তুলিও শিল্পীরা ব্যবহার করেন৷
কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ, গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহ, সোনারগাঁয়ের লোকশিল্প যাদুঘর, ঢাকার বাংলা একাডেমী সংগ্রহ প্রভৃতি স্থানে বেশ কিছু জড়ানো পট সুরক্ষিত আছে৷ পট শিল্পীদের সকলেই বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল৷
বাংলাদেশের এই পটশিল্পের শুরম্ন খৃস্টীয় সপ্তম শতকে বলে মনে করা হয়৷ গাজীর পটে যমদূত ও তার মায়ের চিত্র থেকে অনুমিত হয় যে, এর উত্স প্রাচীন যমপট, যেখানে ধর্মরাজ যমের মূর্তি এবং যমালয়ের ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য অঙ্কিত হত৷ বাংলাদেশের পট চিত্রকলা ভারতীয় উপমহাদেশের বৌদ্ধ পূর্ব ও অজনত্মাপূর্ব যুগের চিত্রকলা এবং পরবর্তীকালে তিব্বত, নেপাল, চীন ও জাপানের ঐতিহ্যবাহী পট চিত্রের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়৷ প্রাচীন বাংলায় যখন কোন দরবারি শিল্পের ধারা গড়ে ওঠেনি তখন পট চিত্রই ছিল বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক৷ পট চিত্রের শিল্পীদের পটুয়া বলা হয়৷ গাজীর এ পট চিত্রে গাজীকে কখনও দেখা যায় সুন্দরবনের রাজার সঙ্গে লড়াই করতে; কখনও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে সমাসীন, কখনও মাথায় টুপি অথবা রাজমুকুট, পরনে রঙিন পাজামা কিংবা ধুতি, এক হাতে চামর বা ত্রিকোণ পতাকা এবং অপর হাতে তলোয়ার কিংবা মুষ্টিঘেরা জ্যোতি৷ এখানে মানিক পীর, মাদার পীর, সত্য পীর, কালু ফকির, বনবিবি প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ছবিও প্রদর্শিত হয়৷ এরূপ ধর্র্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি নানা কৌতুক, রঙ্গারস সম্বলিত কাহিনী, ব্যঙ্গচিত্র এবং সামাজিক দুরবস্থার চিত্রও অঙ্কিত হয়৷ কখনও কখনও পেঁচা, বানর, গরম্ন, বাঘ, সাপ, কুমির ও গাছপালাও স্থান পায়৷ লোক ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ অনেক সময় পটুয়া বা পটচিত্রকে ঝাড়ফুঁকের ৰেত্রে ব্যবহার করে৷ অনেক গৃহে পটচিত্র সংরৰণ করাকে কল্যাণ ও দৈব-দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলেও মনে করে৷
চক্ষুদান পট
যখনই কোনও সাঁওতাল পুরুষ, নারী অথবা শিশু মারা যায়, তখনই মৃতের কল্পিত ছবি এঁকে জাদু-পটুয়া চলে যান শোকের সেই বাড়িতে। সে ছবিতে ব্যক্তির ছাপ নেই। শুধু লিঙ্গ আর বয়স ভেদের ছাপ। রং-রেখায় ছবিটি পুরোপুরি তৈরি হলেও চক্ষুদানটুকু কেবল বাকি থাকে। চোখ-না-ফোটা সেই ছবিটি দেখিয়ে পটুয়া মৃতের স্বজনদের বলেন, চোখ-না-থাকা অবস্থায় পরলোকে মানুষটি ঘুরে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছেন, স্বজনদের কাছ থেকে ‘ভুজ্জি’ পেয়ে পটুয়া চিত্রে চক্ষুদান করলেই ম্যাজিকের মতো তাঁর পরিত্রাণ। সে জন্যই এ পটুয়ার নাম জাদু-পটুয়া আর পটের এই বিশেষ ধারার নাম চক্ষুদান পট। গুরুসদয় দত্তের বর্ণনায় এমনই ধারণা মেলে সাঁওতালি পটের এই বিশেষ ধারা সম্পর্কে। মৃত্যুর পাশাপাশি সাঁওতালি পটে থাকে জন্মও। অনেক সাঁওতালি পটেই ছবির বিষয় সাঁওতাল উপজাতিটির জন্মকথা। ‘যমপট’ আবার সমতল বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। সেখানে ধর্মরাজের বিচারে দণ্ডিত মানুষের নরকভোগ আর পুরস্কৃত মানুষের স্বর্গসুখের ছবি।
পটুয়া ও রবীন্দ্রনাথ
যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।
সে মনে ভাবে, ‘ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।’
এমনমসয় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।
কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।
নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।
যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, ‘এইজন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম। এত দিনে বর দিলে কি এই অপমান।’

২
এমনসময় রথের মেলা বসল।
সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।
সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, ‘আমি কিনব।’
অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘ছেলেটি কে।’
সে বললে, ‘আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।’
অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, ‘বেচব না।’
শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।
অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।
মন্ত্রী মনে মনে বললে, ‘এত বড় স্পর্ধা!’
অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, ‘এই আমার জিত।’

৩
প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।
একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।
দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ণ বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, ‘বুঝতে পেরেছি।’
আজ সে স্পষ্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠছে।
তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, ‘মন্ত্রীরই জিত হল।’
সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, ‘এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।’
মন্ত্রী বললে, ‘কত দাম।’
অভিরাম বললে, ‘আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।’
মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।