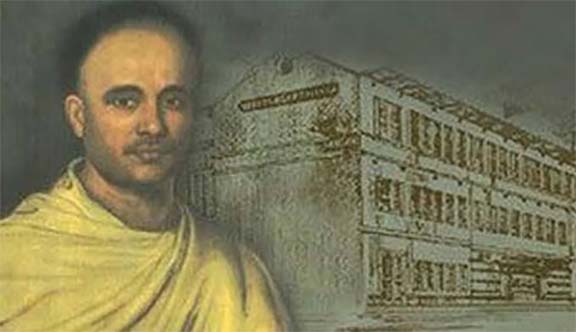
আজ এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষকে ঠিকঠাক ভাবে অনুধাবন করতে গেলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে—যা বাঙালির কাছে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের কাল; নানামুখী চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব সংঘাত—সেই সময়টিকে ভালো করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে দুটি কারণে। প্রথমত, এই সময় বাঙালী জীবনে এসে লেগেছে নবজাগরণের ঢেউ, যদিও তা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত, পড়াশোনা সূত্রেই বিদ্যাসাগর কলকাতায় এবং তাঁর মানসিক গঠনটি তৈরি হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটেই।
১৮২৯ সালে নয় বৎসর বয়সে বিদ্যাসাগর যখন কলকাতায় এলেন পড়াশোনা করতে, তার আগেই ‘মর্নিং স্টার অফ রেঁনেসাঁস’ রামমোহনের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। উল্লেখ্য এ বছরই সতীদাহ প্রথা রদ আইন সিদ্ধ হয়। আর বিদ্যাসাগর এই বছরই ১লা জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ব্যাকরণ বিভাগের তৃতীয় শ্রেণিতে। তারপর ১৮৪১ সালের ডিসেম্বরে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজে যোগ দেন। ১৮৪৯ -এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ‘হেড রাইটার এন্ড ট্রেজারার’ পদে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পরে ১৮৫০ এ সংস্কৃত কলেজের লেকচারার পদে যোগদান করেন। আর এ বছর থেকেই শুরু হয় তাঁর সমাজ সংস্কারকেন্দ্রিক কাজকর্ম। কেন না এ বছরেই ‘সর্ব্বশুভকরী’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তা বিষয়ক প্রথম রচনা—‘বাল্য বিবাহের দোষ’।
অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্ম শুরুর আগের পর্বটি হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ—নবজাগরণের কাল। এখন এই নবজাগরণ ব্যাপারটি অত সহজে হয়নি। ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর যোগসূত্র এবং উভয় সংস্কৃতির তুলনা; এর ফলে ইওরোপীয় নবজাগরণের নূতন চকচকে পাথর আর প্রাচীন ভারতীয় জগদ্দল পাথরের ঠোকাঠুকিতে যে আলো ঠিকরে বেরিয়েছিল তাই হল নবজাগরণের আলো। কথাটা বললাম এই জন্যই এই সময় সংস্কারপন্থীদের কোনো কাজই অতো সহজে হওয়ার ছিল না। বহু শিক্ষিত বাঙালীও যথেষ্ট প্রাচীনপন্থীই ছিলেন। এ বড় অদ্ভূত এক দ্বান্দ্বিক সময়। বহু শিক্ষিত বাঙালীকে দেখা গেছে কখনো সংস্কারপন্থী কখনো বা প্রাচীনপন্থী। অর্থাৎ নবজাগরণের যে মূল কথা যুক্তি, সেই যুক্তির হাত ধরেই শিক্ষিত বাঙালী নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন—যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আর এই যুক্তিনির্ভর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আলোচনা, লেখালেখি এর মধ্যে দিয়েই অতি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মানবতাবাদ। এর সূত্রপাত বলা যেতে পারে রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রদ বিষয়টিকে। আর চার বছরের মধ্যেই ১৮৩৩ এ রামমোহন পরলোক গমন করেন। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স তেরো। আর তাঁর ব্যাকরণ বিদ্যায় সমাপ্ত। অর্থাৎ তাঁর এই মানসিক গঠন পর্বেই তিনি যেমন দেখেছেন রামমোহনকে, তেমনি দেখেছেন রাধাকান্তদেবকে, আবার দেখেছেন ডিরোজিও এবং তাঁর ইয়ংবেঙ্গল দলকেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তির পথ ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পথে তিনি এগিয়ে চলেন মানবতার প্রতিষ্ঠায়। যার শুরু ১৯৫০ এ ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ প্রবন্ধ দিয়ে।
বাঙালীর নবজাগরণের শুরু হয়েছিল রামমোহনের নারীকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা দিয়ে। ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা রদ আইন সিদ্ধ হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই বালবৈধব্য বাড়তে থাকে। বিদ্যাসাগর এই বাল্যবৈধব্যের কারণ হিসেবে বাল্যবিবাহকে দায়ী মনে করেন। তাই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার ও নারীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা দিয়েই শুরু। বিদ্যাসাগরের মূল যে দুটি কাজ, মূলত তার দু’টি হল বন্ধ করা আর দু’টি হল চালু করা— বাল্যবিবাহ রদ, বহুবিবাহ রদ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন ও স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন। প্রতিটি নারীকেন্দ্রিক এবং প্রতিটিই একটি আর একটির সঙ্গে যুক্ত মানবতাবাদের সূত্রে।
‘বাল্যবিবাহের দোষ’ রচনায় তিনি দেখিয়েছেন কেন বাল্যবিবাহ বন্ধ করা উচিৎ। প্রথমত প্রবন্ধটি পড়লে মনে হবে, তা যেন এক শরীরবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির রচনা। সেই মেডিকেল সাইন্সের প্রেক্ষিত ছাড়াও এতে রয়েছে মনস্তাত্বিক দিক। তিনি বলেছেন— বিবাহের উদ্দেশ্য ‘পরস্পর সুমধুর প্রণয়’। সুতরাং অতি অল্প বয়সে—প্রেম ভালোবাসার বোধই যখন জন্মায় না তখন বিবাহ উচিৎ নয়। এরকম নানা দিক থেকে বিশ্লেষণের পর তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছেন—
“…অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়পূর্ণ দুর্ণয় আস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া মতত এমন যত্নবান্ হউন।” (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা তীর্থপদ দত্ত, তুলিকলম —পৃ ৬৮২)
আর এই দেশবাসীর কাছেই সবচেয়ে বেশি বাধাপ্রাপ্ত হন এবং আহত হন বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে। ১৮৫৬ তে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় কিন্তু তার পূর্ব ইতিহাস বড়ই কষ্টদায়ক। এই ভাবনার বীজ হিসেবে বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের ছোটবেলাকার চমৎকার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—কলকাতায় পড়াকালীন একদিন গ্রামের বাড়িতে এসে জানতে পারেন একটি ছোট্ট মেয়ে, তার বাল্য সহচরী বৈধব্যের কারণে সারাদিন না খেয়ে আছে। বিহারীলাল লিখছেন —
“ এবার গিয়ে জানিতে পারিলেন, তাহার বাল্যসহচরী কিছুই খায় নাই; সেদিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা নিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন সেদিন হইতে তাহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩/১৪ বৎসর হইবে।” ( বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, নবপত্র প্রকাশন, পৃ ১২৭)
প্রকৃতিগত ভাবে বিদ্যাসাগর খুব নরম মনের মানুষ ছিলেন—‘কুসুমাদপিকোমলানী’। কাজেই এ ঘটনার গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার সামাজিক প্রেক্ষিত লক্ষ্য করলে বিদ্যাসাগরের শুধু হৃদয়বত্তাই নয়, সামাজিক সত্তারও এক বৃহৎ পরিচয় উঠে আসে। কেননা সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গেলে বাল্যবৈধব্য বাড়তে থাকে আর এই সব ছোট ছোট মেয়েরা, যারা জানে না বৈধব্য কী, স্বামী-সংসারই বা কী; অথচ সেই অবস্থাতেই বৈধব্য-যাপন; প্রাণধর্মের স্বাভাবিক বিকাশ তাদেরও তো একদিন হতই! মানবিক গুণের স্বাভাবিক বিকাশকে তো আর রুদ্ধ করা যায় না! স্বাভাবিক ভাবেই এই সব বিধবারা অনেক সময় পদস্খলিতা হত। আর তারপর, যে পুরুষশাসিত সমাজ দ্বারাই এই অধঃপতন ঘটত তাদেরই জন্য এদের পরিণতি ছিল হয় মৃত্যু নয় পতিতালয়। উনিশ শতকের বহু গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।
যাই হোক, বিদ্যাসাগর তাঁর মানবতাবাদী হৃদয় দিয়ে বিধবাদের পুনর্বিবাহের একটি সূত্র খুঁজতে থাকেন, যা শাস্ত্রসম্মত। ১৮৫৩ সালের শেষ দিকে সে সূত্র পেয়ে যান বলে জানান তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—
“… ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও একত্র আমি বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতে ছিলাম তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশর সংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দ বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন —‘পাইয়াছি, পাইয়াছি’। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘কি পাইয়াছ?’
তিনি তখনই পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন —
‘নষ্টে মৃতে প্রবজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চমাপৎসু নারীনাং পতিরন্যা বিধিয়তে।’
বিধবা বিবাহের ইহাই অকাট্য প্রমাণ ভাবিয়া, তিনি তখন লিখিতে বসিয়াছিলেন। সারা রাত্রি লিখিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, পরে তাহা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন।” (বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ১২৮)
লক্ষ্য করার বিষয় তিনি এখানে মনুকে ধরলেন না। পরাশর সংহিতার একটি শ্লোক থেকে প্রমাণ করলেন যে কলিযুগে পরাশরই শেষ কথা হওয়া উচিৎ। তারপর পরাশর সংহিতা থেকে যে শ্লোকটি তুলে ধরলেন— নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে… যার বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ —
“স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গবাস করে।” (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০)
বিধবা বিবাহের জন্য সরকারের কাছে যে আবেদন প্রেরিত হয় তাতে হাজার খানেক গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু কেন আমরা শুরুতেই উনিশ শতকের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করেছিলাম তা স্পষ্ট হবে এই তথ্য জানলে যে, রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদপক্ষে স্বাক্ষর ছিল পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি— বিহারীলাল সরকার সে রকমই জানিয়েছিলেন। আর বিদ্যাসাগরের সরকারকে প্রেরিত পত্রে স্বাক্ষর ছিল যে ঈশ্বর গুপ্তের, তিনিই আবার এর বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর মহাশ্যকে খোঁচা দিয়ে কবিতাও লেখেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করেও বিদ্যাসাগরই জয়ী হন। ১৮৫৬ তে বিধবা বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। বিহারীলাল সরকার জানিয়েছেন, শেষ বয়স পর্যন্ত সর্বস্ব পণ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে বিদ্যাসাগর নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, প্রচুর লোকের কাছে প্রচুর ঋণ করে প্রতারিতও হয়েছেন।
একইরমক বিরোধিতার সম্মূখীন হয়েছিলেন বহুবিবাহ রদ করার ক্ষেত্রেও। ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ রচনার ভূমিকা স্বরূপ অংশে বিদ্যাসাগর যা লিখেছিলেন তা থেকেই স্পষ্ট হয়, কেন তিনি এই প্রথা বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হন—
“এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমিশ্রকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশত: স্ত্রী জাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে তা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগ্য স্ত্রী জাতিকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।” (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৪৪)
শুধু লেখা নয় বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন সরকারি সহায়তা ছাড়া এই প্রথা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারত সরকারের সদস্য জে.পি. গ্রান্ড- এর কাছে আবেদনপত্র পাঠান, যাতে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজদের সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ১৮৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বহুবিবাহ বিরোধের জন্য একটি বিলের খসড়াও প্রস্তুত হয় বলে জানা যায় বিহারীলাল সরকারের গ্রন্থ থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি; কারণ সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সরকারও চাপে ছিল। দ্বিতীয়ত বিধবা বিবাহের মতই এর বিরুদ্ধেও প্রচুর স্বাক্ষরসহ আবেদন যায় সরকারের কাছে। শুধু তাই নয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন বরিশালের অধিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন লেখেন— ‘প্রেরিত তেতুল’। ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন প্রচারিত ‘বহুবিবাহ বিষয়ক বিচার’, সত্যব্রত সামশ্রয়ী প্রচারিত ‘বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা’ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যাই হোক ভারত সরকারের নির্দেশে বাংলার সরকার এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করেন—
“সাতজন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হল—১. হবহাউস ২. প্রিন্সেপ, ৩. সত্যচরণ ঘোষাল, ৪. বিদ্যাসাগর ৫. রমানাথ ঠাকুর, ৬. জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৭. দিগম্বর মিত্র। এদের রিপোর্ট থেকে মনে হয়, একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া আর সকলেই আইন করে বহুবিবাহ প্রথা বিরোধের বিপক্ষেই মত দিয়েছিলেন।” ( বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩০)
একমাত্র বিদ্যাসাগরই প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে বহুবিবাহ রদের স্বপক্ষে বলেছিলেন। শুধু তাই নয় বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে যারা নানান গ্রন্থ বা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন তাদেরও সমস্ত মতকে খন্ডন করে ‘বিধবা বিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক’ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন যে শাস্ত্রের অর্থ না বুঝে অথবা স্বার্থসিদ্ধির কারণে শাস্ত্রভিন্ন অর্থ করলে শাস্ত্রকারদের নরকে নিক্ষেপ করা হয়।
বিদ্যাসাগরের সমস্ত কর্মই বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক একটি মাইলস্টোন। তবুও আজ এই একুশ শতকের প্রেক্ষিতে মনে হয় সবার উপরে বোধহয় স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন। মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ‘দ্য সেরামপোর নেটিব ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি’ ছিল মূলত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেন্দ্রিক। আর নানা পত্রপত্রিকায় বা জ্ঞানপাঠ জিজ্ঞাসা সভায় স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে একটু একটু আলোচনাও তখন চলছে। যার ফল স্বরূপ নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে ১৮৪৭ এ বারাসাতে প্রতিষ্ঠিতি বালিকা বিদ্যালয়টি কোনরকমে চলছে। আর ১৮৪৯ এর মে মাসে বেথুন সাহেবের প্রচেষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার কর্মের পূর্বে মোটামুটি এই ছিল স্ত্রী শিক্ষার হাল। বরং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই যে এর বিরুদ্ধে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। সুতরাং একটা বিরোধিতা তো চলেছেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয় এক নতুন অভিজ্ঞতা—বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হওয়ার পর। কারণ কয়েকশ’ বৎসরের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দীর্ঘলালিত বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তৎকালীন সময়ের বহু বিধবাও মেনে নিতে পারেন নি বিধবা বিবাহকে। এও এক অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের কাছে। এ জন্যই বোধ হয় স্ত্রী শিক্ষাকে এত গুরুত্ব দেন তিনি। তাই ১৮৫৭ সালের মে মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদিয়া জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বিদ্যাসাগর। তৎকালীন সরকারের সাহায্য না পেয়েও নিরাশ হননি তিনি। এই বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভান্ডার খুলেছেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। অনেক কটূক্তি এবং ব্যঙ্গ সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত তিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তার প্রমাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.এ চন্দ্রমুখী বসুকে তিনি নিজে স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী। আরও একটি ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালের ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায়, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর—
“স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজে আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, ‘মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পারিল না— এই দুঃখে হৃদয় কাঁটিয়া যাইতেছে।” (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র, পৃ—২৩১)
এ আবেগপ্রবণ মানুষটি সমাজসংস্কারমূলক এইসব কাজ করতে গিয়ে এত বিরোধিতা এবং ব্যঙ্গ কটূক্তির সম্মুখীন হয়েছেন যা লিখতে গেলে পৃথক একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। হয়তো বা এই জন্যই তথাকথিত সভ্য সমাজ ছেড়ে জীবনের শেষ দশ-বারটি বছর চলে যান কার্মাটারে। সেখানে সাঁওতালদের সঙ্গেই কাটাতেন অধিকাংশ সময়। কলকাতা থেকে তাদের জন্য নিয়ে যেতেন জামা কাপড়, হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিতেন, তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাদের মধ্যে লেখাপড়ারও প্রচলন শুরু করেন। তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য সমাজ ছেড়ে কেন তিনি এই সব সরল মানুষদের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন— তা আজ আমরা ভাবতে বাধ্য হই।
এই আলোচনার উপসংহারে এসে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ‘কেন বিদ্যাসাগর’ এই প্রশ্ন আমাদের ভাবায়। আজকের বিচার বিশ্লেষণের নানা তাত্ত্বিক পটভূমিতে কয়েকটি দিক অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, উনিশ শতকের নবজাগরণের দূত যারা ছিলেন, বিশেষত সংস্কারপন্থীরা তাঁরা অধিকাংশই ‘ইংলিসাইস্ড’। মূলত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিষয়গুলিকে দেখতেন। একমাত্র বিদ্যাসাগরের যাবতীয় প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা, এমনকি তৎকালীন পন্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক সবই ভারতীয় শাস্ত্রকে সামনে রেখেই। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পক্ষে পুরুষ প্রথম কলম ধরেন ১৮২৫-এ উইলিয়াম টমসন—‘নারীদের আবেদন মানবজাতির অপর অর্ধেক’। এটি তেমন গুরুত্ব পায়নি; বরং তিনি উপহাসের পাত্র হন। তারপর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লেখা জন স্টুয়াট মিলের ‘নারী অধীনতা’ ১৮৬৯-এ। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫০ থেকে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, তার অধিকাংশ কর্ম এবং রচনার কেন্দ্রে নারী। তৃতীয়ত, মেদিনীপুরের এক গ্রামের দরিদ্র পরিবারের একটি ছেলে কলকাতায় এসে এভাবে ইতিহাস তৈরি করলেন। আর চতুর্থত, এত বাধাবিপত্তি, এত কর্মকান্ডের পর এই ব্রাহ্মণ সন্তান জীবনের শেষ বছরগুলি কাটালেন কার্মাটারে সাঁওতালদের সঙ্গে। সময়টা উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত। আজকে জাতপাতের এই বাড়বাড়ন্তের যুগে, যেখানে ভোটের ময়দানেও জাতপাতই প্রধান অস্ত্র; সেই সমইয়ে দাঁড়িয়ে একে কি সমাজ সংস্কার বলবেন? আর সব মিলিয়েই বা কি বলবেন, পোস্টকলোনিয়াল বা ফেমিনিস্ট বা পোস্টমর্ডান বা সাবঅল্টার্ন স্টাডির তাত্ত্বিকেরা?
লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর