
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে মথুরবাবু গেলেন পতিতাপল্লীতে।
রামকৃষ্ণদেব তাদের ডেকে বললেন, ‘মা’। দেখা গেল পতিতারা সংসারে একেবারেই পতিত নয়। সমাজ যাদের ক্রমাগত পায়ে ঠেলে দিয়েছে, সাহিত্য তাদের জন্য বহন করেছে সমবেদনার অজস্র বাণী। কখনও কোনো গণিকা নিজের আত্মজীবনীতে সেই সমবেদনার কথা প্রকাশ করেছে, কখনও কোনো পতিতা সমাজসংস্কারকদের কাছে চিঠি লিখে প্রকাশ করেছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা। সমজের এই পঙ্কিলতার প্রতি সমবেদনার এক অনুদ্ঘাটিত ইতিহাস।
একটি মেয়ে কেন সমাজের সুস্থ বন্ধন ছেড়ে অসুস্থ বারবনিতার জীবন যাপন করতে যায়, এ প্রশ্নের উত্তর সমাজতত্ত্ববিদরা দিতে পারেন। তার অপরাধী জীবনের অপরাধের পরিমাণ ও কারণ নিয়ে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা নানা চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং করছেন। পৃথিবীর এই প্রাচীন বৃত্তি সম্পর্কে দেশে-বিদেশে ঢাউস ঢাউস আকারের বই-পত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রবল ঘৃণা, একটা বিমুখীনতা সত্ত্বেও এই উপজীবিকা আজকের সভ্য (?) সমাজে এখনও রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বরং বলা ভাল, আগে যা ছিল প্রকাশ্য-গোপন, এখন তা উল্টে গিয়ে গোপন-প্রকাশ্য হয়ে গেছে। দাগীদের তবু চেনা যায়, এখন ভদ্র বনিতার আড়ালে এই পাপ-ব্যবসা সমাজের নানা স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতিতে এদের উপস্থিতি এখন অনিবার্য। কিন্তু যতই এদের ক্রিয়াকর্মে এবং পোশাক-আশাকে সামাজিক অবস্থানের বদল হোক, গোটা সুস্থ সমাজ এদের জন্য জমা করে রেখেছে অপরিমিত ঘৃণা, চূড়ান্ত অমর্যাদা এবং প্রবল অবহেলা। আর্থ-সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে এই ঘৃণা তাদের কতখানি প্রাপ্য-অপ্রাপ্য জানি না, কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যুগে যুগে এদের জন্যে সমাজ কিছু সহানুভূতি, কিছু বেদনা, কিছু সান্ত্বনার জমা রেখেছে। এই নিবন্ধে সেই সহানুভূতি ও সান্ত্বনা কিছু সাহিত্যিক বা লিখিত দলিল আমরা উদ্ধার করে পতিতা-সমাজের প্রতি এখনও বর্তমান সমাজের যদি কিছু করণীয় থাকে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধু অন্ধকারই জীবন নয়, আলোকও প্রার্থিত। পঙ্কে জন্ম হলেও পঙ্কজের তপস্যা সূর্যের জন্য।
দুই
তার আগে আমাদের এই পুরুষ শাসিত মানব সমাজ কীভাবে ধীরে ধীরে পতিতাশ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বোধ করি এঁকে নেওয়া ভাল। কারণ রোগের ইতিহাস জানা থাকলে তার চিকিৎসা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়।
দেখা গেছে একগোষ্ঠী কর্তৃক অন্যগোষ্ঠী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাস হিসেবে বন্দী হয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। যদি বন্দীদের মধ্যে বন্দিনী থেকে থাকেই, সহজেই তিনি বিজেতাদলের উপভোগের পাত্রী হয়েছেন এবং পরিণামে তাঁকে বহুভোগ্যা হতে হয়েছে। কুমারী বলি তো এক হিসাবে কৌমার্য বলি। পণ আদায়ের জন্য কন্যাকে নিয়মিত গণিকাবৃত্তির পথে ঠেলে দিতেন সেকালের পেলেউ (Pelew) পিতারা। লিডিয়ার মেয়েরা তো সেজন্যেই নিয়মিত গণিকার খাতায় নাম লিখিয়ে বসতে বাধ্য হত। এই শতকের সূচনাতেও আলজিরিয়াতে গ্রামের মেয়েরা নাচ দেখাবার ছলে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে টাকা রোজগার করত। গ্রামের কেন, বিস্কারা শহরের মেয়েদেরও এভাবে-উপার্জনের সংবাদ আমরা সংবাদপত্র দেখেছি। যে পাত্রী যত টাকা জমিয়েছেন, বধূ হিসেবে তার মর্যাদা নাকি তত বেশি হয়েছে।
ধর্মের নামে চিরকালই নানা অনাচার প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। দেবদাসী প্রথা তো ধর্মের আড়ালে পাপবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা ছলনা মাত্র। ব্যাবিলনে মন্দিরের দেবদাসীরা অতিথিদের আপ্যায়নে (?) নিযুক্ত হতেন। আর তারা রূপোর মোহর দিয়ে এসব মেয়েদের খুশি রাখতেন। সাইপ্রাসে ও ইস্তার মন্দিরের মধ্য আমরা এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। বাইবেলে আছে, সেই ধর্মভীরু যুগেও প্যালেস্টাইনে প্রচুর পণ্যা নারীর বাস ছিল।
কথায় বলে মহাকালই হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। কালে কালে গণিকারা সমাজে একটা স্থান করে নিলেন। এঁদের উদ্ধারের জন্য গণিকাবিবাহ সমর্থন করেছিলেন। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট পর্যন্ত। কিন্তু সে বিবাহ ভোগে মাত্র পর্যবসিত হয়েছিল।
তারপরে মধ্যযুগে সংস্কারের ইচ্ছা প্রবল হল। ১৭৫১ সালেই বোধহয় প্রথম গণিকালয়গুলি ‘Disorderly Houses Act’-এর অধীনে প্রথম এল। উনিশ শতকে এঁদের মোকাবিলা করার জন্যে পুলিশবাহিনীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এঁদের উদ্ধার করার জন্যে খ্রিস্টানদের মধ্যে Salvation Army― পতিতোদ্ধারী সেনাদলের সৃষ্টি হল এ যুগেই। তাতে কি উপকার হয়েছে জানি না। তবে কঠোর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় এঁদের নিরাকরণ যে সম্ভব, তা দেখা গেছে বর্তমান রাশিয়ায়। সেখানে নাকি কোনো পতিতালয় নেই। তবে পতিতা নেই, এমন কথা জোর করে বলা মুশকিল। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মানুষের দেহের ক্ষুধাকে সব সময় শাসন করতে কি সমর্থ?
এসব দেখে মনে হয়, এই যে গণিকাবৃত্তির ক্রমঅগ্রসরমান প্রবণতা― এটা কি শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য অথবা এটা একটা মানসিক বা দৈহিক আবেগের অসংযত বিস্ফোরণ? না কি জাতিগত প্রয়োজনের সঙ্গে আত্মরক্ষার দ্বন্দ্ব? না কি সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রতিশোধের ইচ্ছা? না কি শুধু যৌনবিকৃতি? প্রবৃত্তি?
এডোয়ার্ড গ্রোভার যে বলেছেন, একে নির্মূল করা একটা absurd― একটা অবাস্তব চিন্তা তা সত্য। কিন্তু এর জন্য মেয়েদের সঙ্গে পুরুষেরা কি অনেকখানি দায়ী নয়? মনে মনে বহুচারিতা পুরুষের যে একটা বড় বৈশিষ্ট্য—তা কি অস্বীকার করা যাবে? এটাও তো সত্য যে পদস্খলিতাদের অনেকেই বিয়ে করে সুস্থ জীবন যাপন করতে চান― কী হবে তাঁদের?
এখানে উপভোগী পুরুষদের একটা শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। যুবক-ছাত্র, স্ত্রীসঙ্গ-বিচ্যুত ভ্রমণকারী বা দুরান্তগামী পুরুষ, উপভোগে অসমর্থ স্ত্রীদের স্বামীরা অথবা বিকৃত পুরুষেরা এর জন্য কম দায়ী নয়। বিয়ে করাটা একটা সুস্থ উপায়, কিন্তু চিরস্থায়ী সমাধান নয়। কারণ বার্নাড শ বলেছেন,—Marriage is a legal Prostitution― ভেবে দেখার ব্যাপার।

তিন
এসব ভাবতে শুরু করাটা মাত্র এ যুগের প্রবণতা― এমন মনে করার কারণ নেই। কারণ সহানুভূতি বা প্রীতি দিয়ে এঁদেরকে শোধন করার প্রবণতা শাস্ত্রেই আছে। শাস্ত্রেই এঁদের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের কথা রয়েছে। বলা বাহুল্য তাতে কাজ হয়নি। কিন্তু যিশু যে বলেছিলেন― পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়—তার জ্বলন্ত প্রমাণ আছে বাইবেলেই। বাইবেলে মেরি ম্যাগ ডালেন পতিতার কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু যিশুর এই উপদেশ কি সেই অধঃপতিত শ্রেণীর প্রতিই সহানুভূতিমূলক আত্মশোধনের উপায় নয়?
একদা একদল লোক এক ব্যভিচারিণীকে যিশুর কাছে ধরে নিয়ে এসে বললেন― প্রভু একে আমরা পাথর ছুঁড়ে হত্যা করব, কারণ মুশা এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।
যিশু মাথা নিচু করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপরে বললেন—‘বেশ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো পাপ-কাজ জীবনে করোনি― সেই প্রথম পাথরটি তার দিকে ছুঁড়ে মারো।’
কেউ ছুঁড়ে মারতে সাহসী হল না। যিশু পাপীয়সীকে বললেন― যাও, তোমাকে অভিযুক্ত করছি না, কিন্তু এই পাপ পথ তুমি পরিত্যাগ কর― Hate the sin, not the sinner.
অথবা রূপসী পতিতা অম্বপালীর কথা মনে করুন। একদা বুদ্ধ তাঁর মহাপরিনির্বাণের কিছুদিন আগে এলেন বৈশালীর কোটিগ্রামের সেই বারবনিতার বিশাল আমবাগানটিতে। অম্বপালীকে দেখে মনে হল বুদ্ধের― ‘পরমাসুন্দরী এই নারীর প্রতি রাজপুরুষেরাও আসক্ত। এখন তো একে দেখছি সুধীরা এক রমণী, যিনি যৌবনমদমত্তা নন।’ অম্বপালী বুদ্ধের পাশে বসে তাঁর বাণীনিচয় পান করে পরিবর্তিত হলেন। বুদ্ধকে তিনি পরের দিন সশিষ্য নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, ওইদিনই স্বয়ং রাজা তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি রাজকীয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। রাজা অম্বপালীর কাছে লোক পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিলেন। কিন্তু রাজকোষের সমস্ত অর্থ, বৈশালী নগর সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহারে সম্মত হলেন না তিনি। বুদ্ধ তাঁর গৃহে সশিষ্য আহার করলেন। অম্বপালী দান করলেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বুদ্ধসঙ্ঘে। পতিতার সে দান গ্রহণেও তিনি সম্মত হলেন। অম্বপালী একসময়ে বৃদ্ধা হলেন। শিক্ষিতা এই রমণী রূপগৌরবের তুচ্ছতার কথা ভেবে কত কবিতা রচনা করলেন। বৌদ্ধ থেরীগাথায় তার উল্লেখ আছে। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘থেরীগাথা’ অনুবাদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ‘বিসতীনিপাত’-এর কুড়ি শ্লোকে শিক্ষিতা পতিতা অম্বপালীর জীবনায়নকে অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যে এমন আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মনিবেদন কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা এক শ্লোকের অনুবাদ তুলে দিচ্ছিঃ
করিকর সম মম গুরু ঊরু শোভিত;
হয়েছে সে দিন আজ অতীত।
রসহীন, দুর্বল, যেন রে বাঁশের নল!
আজি সারা দেহ জরামথিত
এমনি তো জর্জর― দেহ দুখ-গেহটি
তার পানে ফিরে চাহে কেহ কি?
দেয়াল হইতে ঝরে, রূপের প্রলেপ পড়ে !
গরবের ধন এই দেহ কি?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা?
এই অনুশোচনা তো প্রতি বিগতযৌবনা পতিতার ক্ষেত্রেই সত্য। অম্বপালীর বুদ্ধশরণ ঘটেছিল। কিন্তু পৃথিবীর অগণিত গণিকার ? মনে পড়ে যায় হয়তো এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত ‘অভিসার’ কবিতার কথা। যৌবনমদমত্তা নগরের নটী অভিসারে যাবার সময় ক্ষমাসুন্দর উপগুপ্ত নিজগৃহে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ
ক্ষমা কর মোরে কুমার কিশোর
দয়া করে যদি গৃহে চল মোর
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।…
সন্ন্যাসী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেননি। বলেছিলেন, ‘সময় আবার হইবে যখনি যাইব তোমার কুঞ্জে।’ সময় এসেছিল যখন বসন্তমহামারী-আক্রান্ত নটীকে প্রজারা ‘পুর পরিখার’ বাইরে ‘পরিহার’ করে এসেছিল। সন্ন্যাসী তখন সেই ‘রোগমসীঢালা’ তনুদেহে ‘সিতচন্দনপঙ্কে’ লিপ্ত করেন। রোগিণী নটী আর্তস্বরে প্রশ্ন করেছিল, ‘কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়?’ করুণাঘন উপগুপ্ত তখনই বলেছিলেন, ‘আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।’
রামায়ণপ্রসঙ্গ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ একদা রচনা করেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত ‘পতিতা’ কবিতা। তাঁর কোনো বইয়েই এটি গৃহীত হয়নি। বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলীতে ছাড়া অন্য সংস্করণে পরিশিষ্টে কবিতা মুদ্রিত আছে। কবিতা রামায়ণের বালকাণ্ডের ৮-১০ সর্গে উল্লিখিত সুখ্যাত ‘ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান’ অবলম্বনে রচিত। রামায়ণে আছে পুত্র কামনায় দশরথ যজ্ঞ করতে শুরু করলে তাঁর মন্ত্রী সুমন্ত্র তাঁকে এই উপাখ্যান শোনান। তাতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কিভাবে লোমপাদ রাজার রাজ্যে এসে অনাবৃষ্টি দূর করে সে দেশকে বৃষ্টিযুক্ত করেছিলেন তার ব্যাখ্যান আছে। ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার জন্যে লোমপাদ কয়েকজন বারাঙ্গনাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জ্ঞান ছিল না। তাই বারাঙ্গনারা তাঁদের যুগলবক্ষ উন্মোচিত করে চুম্বন করলেও তাঁর বিকার ঘটেনি। পিতা বিভাণ্ডক ফিরে এলে তাই ঋষ্যশৃঙ্গ সরলভাবে বলেছিলেন― ‘কয়েকজন ঋষিকুমার’ এসে আমাকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁদের স্পর্শে আমার সুখ উপস্থিত হল। মুখে মুখে স্পর্শ করে তাঁরা একপ্রকার ধ্বনি করলেন― তাতে আমার হর্ষ হল’।
রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটিকে উপজীব্য করে ‘পতিতা’ কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে সেই বারাঙ্গনাদের একজনকে মুখপাত্র করে বলিয়াছিলেন―
ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই।
নাহিক করম, লজ্জা শরম,
জানি নে জনমে সতীর প্রথা―
তা বলে নারীর নরীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা?
এই ‘নারীর নারীত্ব’ টুকুই দীর্ঘকাল কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বারাঙ্গনাদের জন্য একটু সহানুভূতির অনুভবে প্রেরণা জুগিয়েছিল।
এই নারীত্বটুকু এমনই, যাকে ভোগে বা পূজায় তুল্যভাবে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে ঋষ্যশৃঙ্গ এই বারাঙ্গনার মধ্যেই নারীত্বের পূজা করে তাঁকে উদ্বোধিত করেছিলেন। সমাজে দুর্বল পুরুষ অগণিত নারীত্বের অবমাননা করে চলেছে। শক্তিমানের পূজো না পেলে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। ভাগবতে তাই দেখি, ঋষভ মুনির সশ্রদ্ধ আচরণের জন্যই অবন্তী দেশের গণিকা পিঙ্গলা পরের জন্মে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মেয়ে কীর্তিমালিনী রূপে জন্মলাভ করতে পেরেছিলেন।
চার
কথা উঠতে পারে, কি হবে এসব প্রাচীন গালগল্পের কথা বলে? নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে। সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই সমাজের এই অনিবার্য সমস্যা কবি-সাহিত্যকদের দৃষ্টিতে কেমনভাবে ধরা পড়েছিল, তার সামাজিকতাটা অবশ্যই জানা যাবে। উনিশ শতকের সমাজে তাই ফরাসি দেশে এমিল জোলার ‘নানা’ অথবা দৌদেটের ‘স্যাফো’র জন্যে এত ভাবনাচিন্তার উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল। তবে একথা সত্য, একালের সাহিত্যের পতিতারা― চন্দ্রমুখী, বিজলী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মীদের চরিত্র সেকালের তুলনায় রীতিমতো বদল হয়ে গিয়েছিল বইকি! তাছাড়া আমাদের এই বিশ শতকের কালের সবচেয়ে সংলগ্ন শতাব্দীটা তো উনিশ শতকই― যে শতকের সমাজে শিক্ষা, অর্থ এবং সমাজবোধে একটা দারুণ পরিবর্তন এসেছিল― বিশেষ করে আমাদের দেশে ইংরাজ আগমনের প্রায় সমকালেই।
মাঝের সময়টা যে ফাঁকা গিয়েছিল মনে করার কারণ নেই। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে একটু তাকান। হায় রে, এমন যে মহাদেব শিব, তাঁর চরিত্রের প্রতি কি কটাক্ষ! মৈমনসিংহের পুয়া গানে শুনুনঃ
গিয়ে কুচ্নী পাড়া ভাঙধুতুরা শিবশম্ভু খায়।
তানপুরা বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায়।
শিবকেই যেখানে কুচনীবাড়ি রাত কাটাতে হয় সেখানে সেই শিথিল সমাজে মদন সাধু ও ভেলুয়াকে নিয়ে গান পালা লেখা হবে, তাতে আশ্চর্য কি !
পাঁচ
আঠারো শতকের শেষের দিকে বাঙালি সমাজের তলায় যে ঘুণ ধরতে শুরু করেছিল তার একটা কারণ অবশ্য বণিক ইংরাজের আনুকূল্যে কিছু মানুষের হঠাৎ করে নবাব হয়ে যাওয়া। হাতে হঠাৎ অনেক টাকা এসে গেলে সৎভাবে ব্যয় করার চেয়ে অসৎভাবে খরচ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। সৃষ্টি হয় ‘বাবু’ শ্রেণীর। হয়েছিলও তাই। মদ খেয়ে, মেয়েমানুষ রেখে, বেশ্যাবাড়ি গিয়ে, লক্ষ টাকা দিয়ে বেড়ালের বিয়ে দিয়ে, মাইফেলি আর বাঈদের মুজরা বসিয়ে এঁরা সমাজটাকে একেবারে পাঁকের তলায় ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। নৌকা নিয়ে বেড়াতে গিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে ঘুরে এঁরা গান ধরেন ইয়ার বক্সী মিলে―
যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী
কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী।
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারইপুরে ঘুনসি খাসা,
উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামণি।
এ যুগের বারবনিতারা মাত্র উপভোগের পাত্র, ‘হুতোম প্যাঁচা’ তাই এই উপভোগের ছবি মাত্রই এঁকেছেন, সহানুভূতির কথা নয়―
আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোম্টার ভিতর খ্যাম্টা নেচে ঝমঝমাবে মল।
এই সমাজেরই একটা বিশ্বস্ত ছবি আছে প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (D. L. Roy) পিতা কৃষ্ণনগরের রাজদরবারের প্রখ্যাত দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীতে। যে দেশে বেশ্যাগমন অধর্ম বলে গণ্য হত, গণিকালয়ে প্রবেশের মানে সঞ্চিত পুণ্য যেখানে বাইরের দরজায় রেখে যেতে হত (এ জন্যই বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা এত পবিত্র!) সে দেশে তখন বাজারে বাজারে গণিকালয়। কারণ যেখানেই পতি পত্নীদের গ্রামের বাড়িতে রেখে ধন-উপার্জনের জন্য অন্যত্র কর্মরত, তখন তাঁদের আস্তানার আশে-পাশে গণিকালয় গড়ে উঠবে এতে আশ্চর্য কী ? কৃষ্ণনগরের আমিনবাজার, বর্ধমানের মহাজনুলির আবির্ভাব তো এমনি করেই। গ্রিস দেশেও তো একদা পণ্ডিতেরা বেশ্যালয়েই একত্রিত হয়ে সদালাপ করতেন। উনিশ শতকের সূচনাতে এদেশেও ‘সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষত পর্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।’ রাজবাড়ি অথবা জমিদারের বাড়িতে যখন খ্যাম্টা নাচ হত তখন সেই আসরে ‘অবিজ্ঞ যুবা’ এবং ‘বিজ্ঞবর প্রাচীন’ একই সঙ্গে নাচ জুড়ে দিতেন। দেখেশুনে কর্তিকেয়চন্দ্রের (১৮২০-৮৫) মনে প্রশ্ন জাগত ‘ইহারা কি যথার্থই সুখী?’ পরে জানতে পারেন ‘প্রায় বারাঙ্গনাই গিলটির বস্তা।’ কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগত― ‘কে তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে ? কে তাহাদের স্ত্রী সর্বস্বধন সতীত্বরত্ন হরণ করিয়া ভিখারিণী করিয়াছে ?’ উত্তর পেতেন মনে মনে― ‘স্বার্থপর রাক্ষসাধম পুরুষেরাই ক্ষণিক বা কিয়ৎকালের সুখসাধনের নিমিত্ত এই দুর্দশা করিয়াছে।….এত বারাঙ্গনা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, রমণীর বৈধব্যদশা ও কোমল স্বভাব এবং পুরুষের কৌশল।’
এই হঠাৎ-বাবুর দল যেমন সমাজের তলদেশে ঘুণ ধরিয়াছিলেন তেমনি সমাজে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত যে করেছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। এবং সেখানেও তাঁরা বারাঙ্গনাদের সহায়তা নিয়েছিলেন। আমরা বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং বারবনিতাদের জীবন নিয়ে এই সুযোগে আলোচনা করে নিতে চাইছি। কারণ বারাঙ্গনাদের নিয়ে সমাজের সম্মুখে এক নতুনতর আন্দোলন সৃষ্টি করতে এগিয়ে এসেছিল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আদিযুগের পুরুষেরা।
ছয়
১৮৭২ সালে স্থাপিত হল বঙ্গ রঙ্গালয়ের জন্য সাধারণ মঞ্চ। ঠিক তার পরের বছরটিতেই ঘটে গেল সেই বিপ্লব। বাস্তবতার খাতিরে সেই বছরে শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন একসঙ্গে চার নারী। ভদ্র সমাজের মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করবেন (একা একা করবেন, তাই ভাবা যায় না) ―একথা সেকালে ভাবাই যেত না। কাজেই এই চারজন অভিনেত্রী এলেন নিষিদ্ধপল্লী থেকে। এঁরা হলেন গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যামা। বলা বাহুল্য, সমাজ রসাতলে গেল বলে হায় হায় পড়ে গেল।
মজার কথা, এই গোলাপসুন্দরী কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। সেকালের অনেক বারবনিতাই কিছু কিছু পড়াশুনো জানতেন। সুশ্রী, সুকণ্ঠী, নবযৌবন গোলাপসুন্দরী মধুসূদনের ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরে উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ-সরোজিনী’ নাটকে সুকুমারীর ভূমিকায় এমন প্রাণবন্ত অভিনয় করলেন যে, তিনি সুকুমারী নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন। বারবনিতার কন্যা এবং নিজে বারবনিতা হলেও সুকুমারী স্ত্রীর মর্যাদা পেয়ে গেলেন উপেন্দ্রনাথ দাসের মধ্যস্থতায় তাঁর দলের অভিনেতা সুদর্শন গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে। পদবিহীন গণিকা হয়ে গেলেন মিসেস সুকুমারী দত্ত। কবিতায় ছড়া কাটা হল―
আমি সখের নারী সুকুমারী
স্ত্রী-পুরুষে এ্যাক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা-রে।
গোষ্ঠবিহারী তখন সমাজে পতিত হয়ে গেলেন সত্য, কিন্তু ভদ্রপল্লীতে সংসার পাতলেন। সুকুমারীর গর্ভে কন্যাসন্তানের জন্ম হল। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, সুকুমারী ওরফে গোলাপসুন্দরী রচনা করলেন এক চমৎকার ছোট নাটিকা (৯০ পৃ.) ‘অপূর্ব সতী’ নাম দিয়ে। ‘বঙ্গবিদ্যা হিতৈষিণী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়ার করকমলে এই হীনজন প্রণীত নাটকখানি উপহৃত’ হয়েছিল। ১২৮২ সালে নাটক মুদ্রিত হয়। আখ্যানবস্তু করুণ রসাত্মক। নায়িকা নলিনী পতিতার কন্যা। শিক্ষার সামান্য আলো পেয়ে সে সৎ-জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা নেয়। কিন্তু নিজের মায়ের হীন চক্রান্তে তার এই প্রতিজ্ঞা ভেসে যেতে চায়। ফলে আত্মহত্যা করে নলিনী তার আদর্শ রক্ষা করে। পাঠক, বই না পড়লেও এ থেকে আপনার বুঝতে অসুবিধে নেই যে, নলিনী আর কেউ নয় স্বয়ং সুকুমারী।
গোলাপসুন্দরীর যে ভিতরের টানাপোড়েন নাটকের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, বিনোদিনী দাসীর সেই টানাপোড়েন তাঁর ‘আমার কথা’য় নিদারুণভাবে প্রকাশিত হয়। বিনোদিনীও রূপোপজীবিনীর ঘরের মেয়ে। খুব বালিকাবস্থায় তাঁরও বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সে শুধু নামের বিয়ে। একটু বড় হয়ে এক ধনী জমিদারপুত্রের নজরে পড়লেন। তিনিও বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়রে― পতিতার সামাজিক স্বীকৃতি ! রঙ্গমঞ্চে থাকতে থাকতে তাঁর জীবনে আরও পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে শুধু তাঁর স্বপ্নকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে। জীবনে তাঁর অনেক ব্যর্থতা। কিন্তু সার্থকতাও কি কম ! আমি অভিনয়ের কথা বলছি, আর বলছি সেই সূত্রে অর্জিত তাঁর পরমধন শ্রীরামকৃষ্ণের আর্শীবাদের কথাও। ‘বখাটে নট আর অখাঁটি নটীবৃন্দ’ দিয়ে ‘চৈতন্যলীলা’ নাটকের সাহায্যে ধর্মপ্রচারকে অনেকে বাঁকা চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু একথা ভুললেও কি চলবে যে নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ‘চৈতন্যলীলা’র নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে পুত্র মথুরানাথকে বলেছিলেন, ‘তবে কি আবার গৌর এল?’ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, ‘দেখ যাঁরা বেশ্যা ও মূর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলেন, তাদের আমি একটা কথা বলতে চাই।….এই বেশ্যা তো সমাজে আছে তাদের ত্যাগ করা, ঘৃণা করাই কি সমাজসংস্কার?…বেশ্যাদের একটি নতুন পথে চালিত করছি, যে পথে তারা ইচ্ছা করলে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্য লোককে প্রলোভিত করতে ক্ষান্ত থাকবে।’ গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের চিন্তামণি― বেশ্যার পরিণতির কথা পাঠকের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে।
যাই হোক, বিনোদিনীর কথা বলছিলাম। রামকৃষ্ণদেব এসেছেন রঙ্গমঞ্চে। কারণ―
কি লম্পট, কি কপট হীন হেয় জন
বেশ্যা বারাঙ্গনা জাতি অভিনেত্রীগণ
আবাহন সকলেই বার বারে করে।
পদরেণু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে।
এই বারাঙ্গনাদের মধ্যে বিনোদিনী একজন। চৈতন্যলীলায় তিনি নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে আর্শীবাদ করে বলেছিলেন, ‘মা তোমার চৈতন্য হোক।’ বিনোদিনী লিখেছেন, ‘সেই পরম পূজনীয় দেবতা চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন।….আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, ‘মা তোমার চৈতন্য হউক।’ অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গেলে তিনি বিনোদিনীকে স্নেহস্বরে ডেকে বলেছিলেন, ‘আয় মা বোস।’
এই যে ‘মা’ বলে ডাকা―এটা একটা কথার কথা ছিল না। কারণ রামকৃষ্ণভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ১৮৮৫ খিস্টাব্দে ‘তত্ত্বমঞ্জরী’ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে এই পতিতাদের পক্ষ অবলম্বন করে সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। তিনিই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি পত্রিকার মাধ্যমে এ বিষয়ে আন্দোলন শুরু করেন।
সাত
আসলে এ সময়টাই ছিল একটা সংস্কারের যুগ। শ্রীরামকৃষ্ণের মত ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল―বিশেষ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা গৌণভাবে যুক্ত কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। এই যুগ পরিবর্তনে মেয়েরা প্রার্থনা করছিলেন একটু সুখ, একটু স্বস্তির জীবনের জন্যে। একটু সম্মানের জন্য করছিলেন প্রার্থনা। নারীহিতৈষী ব্রাহ্মসমাজ তাদের প্রার্থিত সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এসেছিল। সে সময়ের নারীপ্রগতি বলতে ব্রাহ্মসমাজকে বোঝাত বলে মেয়েরা, বিশেষ করে যাঁরা অসহায়, পতিত―তাঁরা একে এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা পতিতা মেয়েদের উদ্ধারের জন্য নানা ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন ঢাকা শহরের পতিতার কন্যা লক্ষ্মীমণি সৎভাবে জীবনযাপন করতে চাইছিলেন। চাইছিলেন একটু লেখাপড়া শিখে আলোকপ্রাপ্তা হতে। কিন্তু তাঁর পতিতা মা চাইছিলেন মেয়ে তাঁর বৃত্তিতেই উপার্জন করুক। সেজন্য―‘তাহার জননী প্রথমে প্ররোচনা অনুরোধ প্রভৃতি করিয়া অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বেচারিকে একটা পুরুষের সঙ্গে একঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া রাখিল। আঁচড়, কামড় হাত পা ছোঁড়ার দ্বারা যতদূর হয়, লক্ষ্মী সমুদয় করিয়া সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিল।’ তারপর সন্ধেবেলায় একটু ফাঁক পেতেই ব্রাহ্মশিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর মা মামলা করেছেন এবং হেরে গেছেন। লক্ষ্মীমণি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এখান থেকে এক ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে বিয়েও হয়েছে তাঁর। এমন বহু পতিতা ও পতিতা কন্যা বিবাহিত হয়েছিলেন সে সময়ে ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে এবং তাঁদের সন্তানসন্ততিরা খুব উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভদ্র জীবন যাপন করেছিলেন। প্রয়াত যোগানন্দ দাস মশায়ের কাছে এমন বহু পতিতার কথা আমি শুনেছিলাম। সে সব অপ্রকাশ্য ভেবে বর্ণনা করতে বিরত হলাম। লক্ষ্মীমণিও ঢাকার ব্রাহ্মযুবক নবকান্তবাবুর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। হরিনাভিতে তখন বাস করতেন শিবনাথ। তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন লক্ষ্মীমণিকে। দরিদ্র অবস্থার মধ্যে ছিলেন শিবনাথ। কিন্তু চার বছর কন্যাস্নেহে তাঁকে পালন করলেন। আমরা লক্ষ্মীমণির লেখা এক চিঠি তুলে দিচ্ছি। তা থেকে প্রকাশ হবে ব্রাহ্মসমাজ পতিতা নারীদের জন্য কিরকম চিন্তাভাবনা করেছিল―
মান্যবরেষু,
নিশিকান্তবাবু বিলাত যাইবার সময় আমাকে শিবনাথবাবুর বাসায় রাখিয়া গিয়াছেন, একথা আমি পূর্বেই আপনাকে জানাইয়াছি। অল্প কয়েকদিন হইল আমি শিবনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে আসিয়াছি।…… পূর্বের ন্যায় এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। ইঁহাদের ভালবাসায় আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। শিবনাথবাবুর সততায় আমি অনেক সময় ভাবি তিনি মানুষ না দেবতা। রাগ নাই, সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই, আপন পর ভেদ নাই; আমাকে ঠিক নিজের কন্যার মত ভালবাসেন। হেমের লেখাপড়ার জন্য তাঁর যেমন যত্ন, আমার জন্যও তদ্রূপ যত্ন করেন। কলিকাতায় থাকিতে একদিন কোন এক ব্রাহ্ম বাড়ি হইতে সপরিবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়া যাইতে তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া যান; এজন্য শিবনাথবাবু কাহাকেও সে বাড়ি যাইতে দেন নাই এবং নিজেও সে কার্যে যোগ দেন নাই। এরূপ সাধু লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে আমি আর কোন সুখ চাই না।
আপনার স্নেহের চিরদুঃখিনী
কুমারী লক্ষ্মীমণি
শুধু কি শিবনাথ শাস্ত্রী একা ? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি সকলেই সহানুভূতির হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দেশের কাজে পতিতারাও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য এঁদের চেলাচামুণ্ডারা সুযোগসন্ধানী হয়ে পতিতাদের ভোগ করতেও সচেষ্ট হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী এ ব্যাপারে অবশ্য একটুখানি সংরক্ষণপন্থী ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, কুমারী মানদা দেবীর ‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’ পতিতাজীবনের এক অপূর্ব বিশ্বাসযোগ্য দলিল এবং চরিত-সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত।
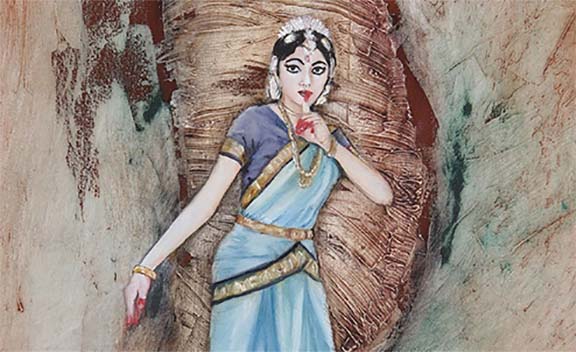
আট
উনিশ শতক পেরিয়ে বাংলা সাহিত্য যখন বিশ শতকে সাবালক হয়ে উঠল, তখন সে পরিচিত হয়েছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতার সঙ্গে। ফলে বাংলা সাহিত্যেও একটা নব আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল। এর ফলে এক শ্রেণীর আধুনিক লেখক পতিত, অবহেলিত, দলিত শ্রেণীর জন্যে বিশেষ সহানুভূতি অনুভবের করছিলেন। ফলে নিপীড়িত দরিদ্র জনসমাজ সাহিত্যে রীতিমতো ঠাঁই পাচ্ছিল। এর সঙ্গে এসেছিল উগ্র দেহসর্বস্বতা আর এসেছিল প্রখর বাস্তববোধ। এই অনুভব পথ বেয়েই পতিতারাও সাহিত্যে বিশেষ সহানুভূতি পেতে আরম্ভ করেছিল। একে অনুকম্পা ভাবা উচিত হবে না। শরৎচন্দ্রের কথা যদি ধরি তবে তো সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ীরা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছে বলতে পারি। নারীর মূল্য এবং সতীত্বের বিশেষ ব্যাখ্যা তাঁর মধ্যে নবমূল্যায়ন পেয়েছিল।
তার আগে রবীন্দ্রনাথের কথা আমরা বলেছি, বিশেষ করে ‘পতিতা’ কবিতার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘বিচারক’ গল্পটিতে এই ‘পতিতা’দের কথা এক নতুন ভঙ্গিতে নিবেদিত হল। ক্ষীরোদা ছিল বারনারী। আটত্রিশ বছরের বন্ধনহীন সংসারে যখন সে জারজ শিশুটিকে নিয়ে সব জ্বালা জুড়োবার জন্য কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরতে চেয়েছিল, অভাগার কপালে আরও দুঃখ এসে জমা হয়েছিল। সে মরেনি, মরেছিল শিশু। ফলে ক্ষীরোদাকে ফাঁসির হুকুম দিলেন বিচারক মোহিতমোহন, যিনি একদা এক বিধবা নারীকে নিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি সেজেছিলেন বিনোদচন্দ্র। আজ মোহিতমোহন বিচারক! ফাঁসির আসামীর কাছ থেকে প্রহর যখন আংটি নিয়ে নিচ্ছিল তখন জজ সেই আংটি হাতে নিয়ে হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। এই আংটি বিনোদচন্দ্র ওরফে মোহিনীমোহনই সেই বিধবা ওরফে আজকের বারনারী ক্ষীরোদাকেই দিয়েছিলেন। এখনও সেই নির্বোধ নারী প্রবঞ্চক মোহিনীমোহনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। হায় পতিতা!
কিন্তু কি শরৎচন্দ্র, কি রবীন্দ্রনাথ কেউই অত্যাধুনিক বাঙালি সাহিত্য সংসারের মানুষ নন। সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের ধনিয়া, যে বুকের দুধ দিয়ে একদিন ধনীপুত্রকে বাঁচিয়েছিল, তাকেই যেতে হল বেশ্যা পল্লীতে স্থান নিয়ে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আসতে হল পথে, ‘যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।’
প্রবোধ সান্যালের ‘রাত্রি’ গল্পের নায়িকা টগর বেশ্যা। বেশ্যার ছেলে শশীর সঙ্গে সে আসনাই করেছে। কিন্তু এদের প্রেমেও যে শুদ্ধতা প্রার্থিত হতে পারে তা বুঝতে পারি, যখন শুনি শশী বলছে ‘চল না কোথাও বেরিয়ে পড়ি, এই কুকুরের জীবন, এই গলির ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ আর অন্ধকার ছেড়ে চল্ না কোথাও চলে যাই―যাবি? বেশ্যারও বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার দাবি আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সে কথা শোনাতে লাগল।’
একথা ভেবেই গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘মঞ্জরী’ গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন ‘সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনা অথবা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই হয়ত দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে এবং এমন যদি কেহ উদারহৃদয় মহানুভব থাকেন, যাঁহারা তাহাদের অপরাধকে মার্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার তাহাদিগকে আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে, প্রেমময়ী নায়িকারূপে ফিরিয়া পাইতে পারেন।’
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝি একথা মনে রেখেই তাঁর ‘ডালিম’ গল্প লিখেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ছিল। তিনি ইতিপূর্বেই ‘বারবিলাসিনী’ কবিতায় লিখেছিলেনঃ
নাহি প্রাণ মধুদেহে মোর
নাহি সুখ নাহি লজ্জা
জীবন বিলাস সজ্জা
কাজল নয়নে, ঘুম ঘোর―
চাও পান্থ আঁখিপাতে, লও ঘুমঘোর।
মোহভরা মধুদেহ মোর।
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘অভিনেতা’, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘শিউলি ও কুসুমের গল্প, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হেরফের’ উপন্যাস….’
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ‘অভাগিনী’ গল্প পতিতাদের জীবনের বেঁচে থাকা দিকগুলিকেই তুলে ধরেছে। অচিন্ত্যকুমারের ‘প্রাচীর ও প্রান্তর’ উপন্যাসের বারবনিতা কিটির রুগন সন্তানের জন্য যে উদ্বেগ ও কাতর উৎকণ্ঠা তা সংগ্রামময় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উপর একটা করুণ ভাব-মহিমা সঞ্চার করেছে সন্দেহ নাই। তবে রবীন্দ্রনাথেই প্রথম পতিতা নারীর প্রতি সহানুভূতি ও বেদনা স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সন্দেহ নাই। তাঁদের সুখদুঃখ, আচার ব্যবহার, রেশমি শাড়ি ও পরিপাটি সাজসজ্জার আড়ালে সময় সময় বুকের মধ্যে যে দীর্ঘশ্বাস জমা হয়ে ওঠে তাতে তাঁদের ছলাকলার জন্যে রাগ না হয়ে প্রাণে সমবেদনা জাগে।
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ‘শুভা’ উপন্যাসটির কথা অনেক পাঠকের মনে পড়বে। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় শুভার মনে প্রশ্ন জেগেছিল―‘সে কি ―হাজার হাজার লোকের মত পথে দাঁড়াইতে পারে না? ―কিসের ভয়?? যে অপমানের ভয়, সে অপমান তো ঘরে থেকে রোজই হবে।’ প্রেমহীন সহবাস তো গণিকাবৃত্তিরই নামান্তর― ‘ঘরে থাকিলেও শরীর বেচিয়া খাইতে হইবে বাহিরেও না হয় তাহাই হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটাকে সার্থক করিবার একটা অবসর চাই।’ তবুও মান বিলিয়ে শরীর-পণ্যে জীবনধারণ করাটা তার পক্ষে খুব একটা সহজ হয়নি। এই যে সামাজিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া এজন্য পুরষশাসিত সমাজের একটা দায়িত্ব থেকেই যায়।
উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘তুরুপ’, সোমনাথ সাহার ‘অভিনেত্রী’ বিনয় চক্রবর্তীর ‘অভিনেত্রী’ এমনি হাজারো গল্প উপন্যাসের। প্রফুল্ল রায়ের ‘তাপসী’ তো এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সব গল্প উপন্যাসে নারীত্বের আক্ষেপ অনুশোচনা বেশি সন্দেহ নেই। কিন্তু বারবনিতাদের মুক্তির পথে অন্ধকার গলি থেকে আলোর পথে আনার একটা মহৎ চিন্তাও ছিল। তবু বর্তমান সমাজেও কিছু তর্ক, কিছু সমস্যা থেকেই যায় এই আলোর জগতে তাঁদের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে।
পাঠক হয়ত কৌতূহলী হতে পারেন, পতিতা সমাজ আধুনিক বাঙালি লেখকদের এই সহানুভূতিকে কতখানি গ্রহণ করেছিলেন? একথা জানার একমাত্র উপায় শিক্ষিতা পতিতা মানদা দেবীর বই। তা থেকে আমরা তুলে দিতে পারি বিশেষ এক অংশঃ
‘তাঁহারা কুলটা ও পতিতা নারীর কোন কোন চরিত্র এমনভাবে দেখাইয়াছেন যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন বেশ্যারা অসতী হইতে পারে―কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের আদর্শে হীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরলচিত্ত, ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত দয়ার্দ্রহৃদয়, দানশীল হইয়া থাকে, তখন তাহারা ঘৃণার পাত্র হইবে কেন? দোষ সমাজের―পতিতার নহে।
‘এই সকল উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য তরুণ যুবক যুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা ‘শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী’ পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল― “শুভা’ পড়িয়া ‘শুভা সঙ্গিনী’র’ মত অভিনেত্রীর সন্ধানে বাহির হইল। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি, বাঙ্গলার তরুণ যুবকের দল ক্রমশ অধিক সংখ্যায় কলুষ সংস্পর্শে আসিতছে। পতিতা নারীর জীবনের এই চিত্রকে নব্য সাহিত্যিকের দল রিয়ালিস্টিক আর্টের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্বনাশী বিষ ছড়ান হইতেছে।…আমার আত্মচরিত লিখিতে যাইয়া এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমাদের মত পতিতা নারীর জীবন যে অসংযম ও অসাবধানতার ফল, তাহা সমাজের প্রায় সকল স্তরে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমার অভিপ্রায় ও নিবেদন।’
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মানদা হয়তো এই সত্য অনুভব করেছিলেন কিন্তু সবাই কি সাজানো, সবাই কি ফাঁকি?