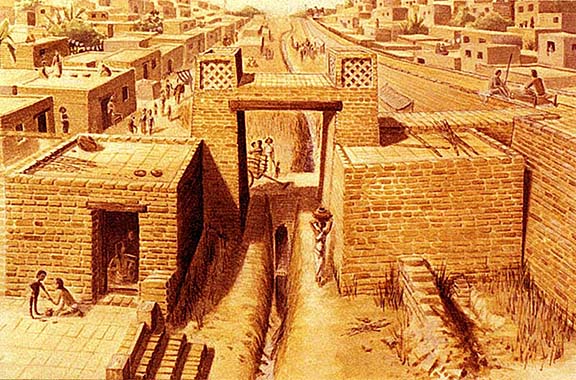
সিন্ধুসভ্যতার প্রাণিকুল নিয়ে বিরাট ধোঁয়াশা আছে। কুকুর, বেড়াল, হাঁস, মুরগি, শুয়োর, ভেড়া, গরু, মহিষ, ষাঁড়, খরগোশ, মাছ, বাঘ, গণ্ডার, উট, হাতি তো বটেই, পৌরাণিক ইউনিকর্নও আছে।
বোঝাই যাচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। সঙ্গে পশুপালনও ছিল। আধুনিক ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। অনেকে গোঁজামিল দেওয়ার জন্যে যতই রকেট সায়েন্সের আমদানি করুন না কেন, প্রাপ্ত তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যসামগ্রীর চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কৃষি ও পশুপালন ছিল সিন্ধু উপত্যকার মানুষের মূল জীবিকা।
গৃহপালিত পশু যেমন ছিল, তেমনি বন্যপশুও ছিল। কিন্তু অবাক করেছে তথাকথিত ইউনিকর্নের উপস্থিতি। এই মাইথোলজিক্যাল জীবটি কেন সিন্ধু সভ্যতার সময় ফলক ও সীলমোহরে উৎকীর্ণ হল, তা বোঝা সহজ নয়। তবে এই ধরনের দেখতে প্রাণী সিন্ধু উপত্যকায় সেকালে ছিল কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে হবে। এটি কুঁজবিহীন বন্য বলদ বা নীল গাইয়ের কোনও গোত্র হতেও পারে। তবে একটি শিং কেন? আসলে পাশ থেকে দেখার ফলে দুটি শিংয়ের একটিতে অপরটি সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গেছে। এটি মাথার নিখুঁত প্রোফাইল ভিউ। প্রকৃত-প্রস্তাবে দুই শিংওয়ালা প্রাণীই এটি। এই ধারণা যে মোটেই অমূলক নয়, তা হাতির প্রোফাইল ভিউয়েই স্পষ্ট। কোনও কোনও হাতির দুটি দাঁত দেখা গেলেও দুয়েকটি ক্ষেত্রে একটি মাত্র দাঁত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রেও একটি দাঁত ঢাকা পড়েছে। ম্যামথের ছবি সিন্ধুসভ্যতার শিলালিপিতে পাওয়া যায়নি। তাই ইউনিকর্ন নয়, কোনও কুঁজবিহীন দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীর (বুনো বলদ বা নীলগাই) প্রকৃত প্রোফাইল ভিউকেই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ ইউনিকর্ন বলে ভুল করেছেন।
জীবজন্তুর গতিবিধি বা চালচলন যে কোনও সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। যে সব জন্তুর মাথার একটিমাত্র শিং দেখা যাচ্ছে, তাদের গতি সম্পূর্ণভাবে বাঁদিক থেকে ডানদিকে বা ডানদিক থেকে বাঁদিকে এরং নিরন্তর সে যাত্রা। কোনও আঁকাবাঁকা পথে তারা যাচ্ছে না, এই প্রতীকে সেই অর্থই বোঝানো হচ্ছে।
বুনো ষাঁড় ও হাতির যাতায়াত যে কৃষির ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ভুক্তভোগীরা সকলেই জানে। দলে দলে হাতির পাল দলমা পাহাড় ছেড়ে যখন ধানজমি বা কলাবাগানে নেমে আসে, তখন ফসলের সমূহক্ষতি হয়, কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই এই চিহ্ন উৎকীর্ণ করে দেশবাসীকে সচেতন করা হত আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। যখন একটি দাঁত বা শিং দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তখন রাস্তা দিয়ে দূরদূরান্তরে যেতে ব্যস্ত হাতি বা বুনোষাঁড় বোঝানো হয়েছে।
যখন হাতির ও ষাঁড়ের দুটি শিংই দেখা যাচ্ছে, তখন স্থির ও স্থবির হাতির পাল ও বুনো ষাঁড়ের দলকে বোঝানো হচ্ছে।
যেখানে কুকুর-বেড়াল, হাঁস-মুরগি, ভেড়া-খরগোশ দেখানো হয়েছে, সেখানে লোকের বসবাসের জায়গা প্রমাণিত হয়। পাড়া, মহল্লা, গ্রাম, জনপদ আছে সেখানে।
যেখানে বাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো ষাঁড়ের ছবি উৎকীর্ণ, সেখানে অরণ্যসংকুল ভূমির ধারণা করা যায়।
মাছের ছবি কিন্তু বেশ রহস্যময়।
ইংরেজিতে একটি কথা আছে, ‘The fish follows the water and the fisherman follows the fish.’। অর্থাৎ এখানেও সেই গতায়ত পুনঃপুনঃ।
জীবজন্তুর যাত্রাপথ অঙ্কিত করতেই যেন সিন্ধুসভ্যতা বা হরপ্পাসভ্যতার প্রাণীদের মোটিফ তৈরি করা হয়েছিল।
সিন্ধু সভ্যতায় ঘোড়ার ছবি পাওয়া যায়নি। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পরও মেলেনি ঘোড়ার কোনও চিহ্ন। আমরা জানি আর্যরা ঘোড়া এনেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। সিন্ধুসভ্যতা যে প্রাক-আর্য বা প্রাকবৈদিক, তা ঘোড়ার অনুপস্থিতি থেকেই বোঝা যায়।

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদড়োতে যে নরকঙ্কাল গুলি পাওয়া গেছে, তাদের খুলির হাড় দেখে অনুমান করা যায় যে তখন সেখানে, মানে হরপ্পা বা সিন্ধুসভ্যতার বিস্তারের মধ্যে, অনেক জাতি বসবাস করত। সিন্ধুসভ্যতার অন্তিম অবস্থায়, মানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর খননের একদম ওপরের স্তর থেকে মোট ৩৭টি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই নরকঙ্কালগুলির মধ্যে বেশীরভাগই আদি অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড।এদের ললাট অনুন্নত এবং নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। বেশ কিছু করোটি পাওয়া গেছে যেগুলি দ্রাবিড়ীয় বা বর্তমান ভারতের আদিম অধিবাসীদের অনুরূপ মানুষের পরিচয় দেয়। কিছু মোঙ্গলয়েড এবং মাত্র গোটা দুই ককেশিয়ান গোত্রের মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই দ্রাবিড়ীয় এবং অস্ট্রালয়েড কঙ্কালের আধিক্য এবং মাত্র দুটি ককেশিয়ান বা আর্য গোষ্ঠীর কঙ্কালের অস্তিত্ব আমাদের খুব সুদৃঢ় ভাবেই একথা জানাচ্ছে যে, সিন্ধুসভ্যতার জনক যদি আর্যরা হত, তাহলে ৩৭টি নরকঙ্কালের মধ্যে ৩১টি দ্রাবিড়ীয় ও অস্ট্রালয়েড কঙ্কালের বদলে অন্তত সমসংখ্যক ককেশিয়ান কঙ্কাল পাওয়া যেত। যে দুটি ককেশিয়ান বা আর্য কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তা থেকে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋগ্বেদ বা তার সমসাময়িক যুগে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে যে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তার বহু আগে থেকেই দফায় দফায় বেশ কিছু আর্যদের আগমন ঘটে এই সিন্ধুসভ্যতায় এবং তাঁরা কালক্রমে সিন্ধুসভ্যতারই অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। এঁরা অশ্বের ব্যবহার জানতেন না। এই ককেশিয়ান নরকঙ্কাল দুটি তাঁদেরই। আবার কেউ কেউ এঁদের আর্মিনীয় বা আর্মেনয়েড বলে চিহ্নিত করেছেন।
দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দক্ষিণভারতে এসেছিল প্রথমে। তারা ক্রমশ উত্তরভারতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান-আফগানিস্তান পর্যন্ত তারা বিস্তারলাভ করে। আর্যরা ভারতে ঢুকে দ্রাবিড়দের মুখোমুখি হয়। তাদের মধ্যে সংঘাতও হয়, মিলনও হয়। তবে দ্রাবিড় রক্ত আর্য ধমনীতে বওয়ার আগেই আর্যদের রক্তে ভেজাল ঢুকেছিল। অবিভক্ত ভারতে প্রবেশের আগে আল্পীনীয়, আর্মানীয় ও দিনারীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যরক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।
তাই, যতই একটি লবির পক্ষ থেকে সিন্ধুসভ্যতার গায়ে বৈদিক লেবেল সেঁটে দেওয়া হোক না কেন, আসলে সিন্ধুসভ্যতা আদিদ্রাবিড়ীয়। সিন্ধুলিপির উদ্ধারকার্যে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁদের এদিকটা মাথায় রাখতে হবে। তবে কয়েকশো বছর ধরে চলা সিন্ধুলিপিকে Decipher বা Decode করার প্রচেষ্টা বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছে। বেশিরভাগ রিসার্চ পেপারই কানাগলিতে গিয়ে পথ হারিয়েছে। অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো অনেক আজগুবি থিওরি আন্তর্জালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বিভাষিক লিপি, Rosseta stone না আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই এই বিপত্তি। মিলিয়ে দেখার উপায় নেই। সবটাই তাই আন্দাজ ও অনুমানভিত্তিক গবেষণা। অন্ধকারে পথ হাতড়াতে ব্যস্ত সবাই।