
কোশী-শিলিগুড়ি রোড, পাকা রাস্তার ধারে বিশাল বটগাছ। তার কাছেই তাৎমাটুলি। তাৎমারা গরিব নিম্নবর্গের মানুষ। তাদেরই পাড়ায় বৌকাবাওয়া ছোট্ট ঢোঁড়াইকে বড়ো করে তুলছেন। ঢোঁড়াই বাপ-মা মরা তাৎমা ঘরের ছেলে। বৌকাবাওয়া সাধক প্রকৃতির। সেদিন ভোরে দাঁতন করতে করতে ঢোঁড়াইকে জাগিয়েছেন বাওয়া। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পাড়ার রবিয়া কী চিৎকারই না করছে। তার বাড়িতে ছুটে গিয়ে বাওয়া এবং ঢোঁড়াই দেখে, রবিয়ার উঠোন ভরে গেছে পাড়ার লোকে। নিচু চালের ছাঁচতলা থেকে একটা বিলিতি কুমড়ো ঝুলছে। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেইখানটায়। মাচার কুমড়োর গায়ে গানহি বাওয়ার আবির্ভাব হয়েছে। তাৎমারা গোস্বামী তুলসীদাসজির কথা বুঝতে পারে। আর শোনে গানহি বাওয়ার কথা। তাঁকে সাক্ষী রেখে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীকাঠের মালা পরিয়ে দিলেন বাওয়া। আজ থেকে ঢোঁড়াইকে রোজ চান করতে হবে। মাছ-মাংস খাওয়া চলবে না। পান-সুপুরির গুড় দিয়ে পুজো করতে হবে গানহি বাওয়ার।
বাংলার ১৩৫৫ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২৬ ভাদ্র দেশ পত্রিকার ১৬ টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’, প্রথম চরণ। ১৩৫৭ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০ ভাদ্র দেশ পত্রিকায় এই উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণ প্রকাশিত হলো। ১৯৫১ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স সতীনাথ ভাদুড়ীর এই অত্যাশ্চর্য উপন্যাসের দুটি খণ্ড প্রকাশ করে। কুমড়োর চালে গানহি বাওয়া আর কেউ নন, মহাত্মা গান্ধী। ঢোঁড়াইচরিত মানস-এর মতো আর কোনও উপন্যাস বাংলা কিংবা ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় কখনও লেখা হয়েছে কি না, এই নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান বিখ্যাত লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র প্রমুখ বহু বিশিষ্টজন।
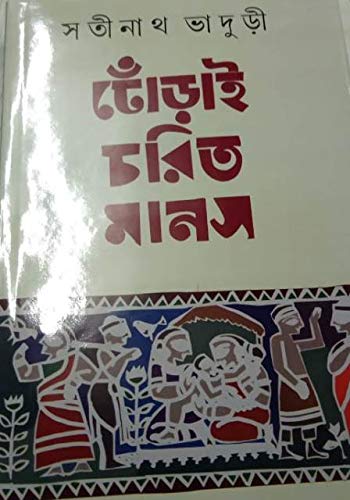
সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম ১৯০৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ণিয়া জেলার ভাট্টাবাজারে। পড়াশোনা করেছেন পূর্ণিয়া জেলা স্কুল, পাটনা কলেজ এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর পড়াশোনার বিষয় অর্থনীতি। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় প্রথম ছোটগল্প ‘জামাইবাবু’ প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। ১৯৪০ সালে গান্ধীজির সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে ছয় মাস কারাবরণ করেন। একই সঙ্গে সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন ১৯৪২ সালে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফের গ্রেফতারি। ১৯৪৭ পর্যন্ত বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। কিষাণগঞ্জে কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশভাগ এবং দাঙ্গায় চরম ব্যথিত সতীনাথ ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ছাড়েন। ১৯৪৫ সালে তাঁর জাগরী উপন্যাস প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জাগরী-র ইংরেজি অনুবাদ দ্য ভিজিল প্রকাশ করে UNESCO। ১৯৫০ সালে জাগরী উপন্যাসের জন্য প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। জাগরী উপন্যাসটিও গান্ধীজি, কংগ্রেস এবং এক পরিবারের কাহিনি।
চিত্রগুপ্তের ফাইল, অচিন রাগিণী, সংকট, দিগভ্রান্ত— এগুলি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। গণনায়ক, চকাচকি, বৈয়াকরণ, মুনাফা ঠাকরুন, বমি কপালিয়া প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প।
জীবদ্দশায় জাগরী, অচিন রাগিণী, সংকট প্রভৃতি উপন্যাসের জন্যেই তিনি খ্যাতনামা হন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঢোঁড়াইচরিত মানস উপন্যাসটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসিক তো বটেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের বিচারে আরও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতীয় জনমানসের, বিশেষ করে দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে গান্ধীজির প্রভাব যেভাবে এই উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে, তা ইতিপূর্বে কল্পনাতীত ছিল। গরিব নিরক্ষর ভারতবাসী, যাঁরা স্কুল-কলেজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি পরিষেবা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত, কোনওক্রমে যাঁরা জীবনধারণ করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে রামচরিত মানস জানেন, সমাজের সেই নিম্নবর্গের মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে গান্ধীজির বার্তা। ঢোঁড়াই তাদেরই একজন।
১৯১৭-১৮ সাল নাগাদ আহমেদাবাদ এবং বোম্বাইতে দুটি সভায় লোকমান্য তিলক এবং মহাম্মদ আলি জিন্নাহ প্রমুখের উপস্থিতিতে গান্ধীজি বলেন, স্বরাজ তখনই সম্ভব যখন এদেশের লক্ষ কোটি কৃষক জনসাধারণ সংগ্রামে যোগ দেবেন। আমাদের ঘরের মহিলারা আন্দোলনে অংশ না নিলে কোনও কর্মসূচি ব্যাপক আকার গ্রহণ করতে পারবে না। গান্ধীজি নিজে বিহারের চম্পারণ, গুজরাতের খেড়া প্রভৃতি গ্রামীণ অঞ্চলে স্কুল গড়ে তোলার এবং সত্যাগ্রহীদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত হন, সঙ্গে নেন স্ত্রী কস্তুরবাকে। ক্রমশ পরিচিত হন অতীব পিছিয়ে পড়া দেশবাসীর সঙ্গে। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেন। তাই জীবদ্দশাতেই ওই তাৎমাটুলির মতো হাজার হাজার গ্রামীণ অঞ্চলে গানহি বাওয়ার আবির্ভাব হয় নেহাতই অকিঞ্চিৎকর লাউ-কুমড়োর মাচায়। আর সেই আখ্যান শোনান সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো অসামান্য কথাকার। ১৯৬৫ সালের ৩০ মার্চ সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রয়াণের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ লেখেন, আমাদের মতো রাজনীতি করিয়েদের চেয়ে গান্ধীজিকে ঢের বেশি চিনেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো লেখকরা। কারণ তাঁদের বিচরণ অনুভবের ভূমিতে।