
১. উইলিয়াম কেরি (William Carey) (১৭৬১-১৮৩৪)
যে সব বিদেশি বাংলা ও বাঙালির আত্মার আত্মীয় হয়েছিলেন, উইলিয়াম কেরি তাঁদের অন্যতম। ১৭৬১ সালে ইংল্যাণ্ডের নর্দানটনশায়ারে তাঁর জন্ম। তিনি ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হন। ‘ব্যাপটিস্ট সোসাইটি ফর প্রোপাগেটিং দ্য গসপেল অ্যামাং দ্য হিদেন’ সংগঠনের সদস্য হিসেবে তিনি ভারতে আসেন ১৭৯৩ সালের ১৩ জুন। মুনশি রামরাম বসুর কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি শ্রীরামপুর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্র্যান্ট প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলিত হন এবং ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও প্রেস স্থাপন করেন। ১৮০১ সালে তিনি নবনির্মিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দেশীয় ভাষার শিক্ষক ও পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই কলেজই বাংলা গদ্যের সূতিকাগার। কেরি রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, তারিণীচরণ শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতদের বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রেরণা দেন। নিজেও রচনা করেন দুটি বই — ‘কথোপকথন’ ও ‘ইতিহাসমালা’।
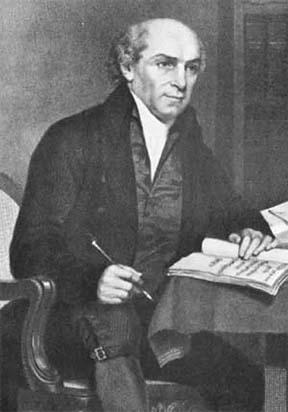
কেরি যুক্ত ছিলেন স্কুল সোসাইটিতে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় কলকাতায় গড়ে ওঠে কৃষি উদ্যান সমিতি।
দ্রষ্টব্য.
উইলিয়াম কেরি : জীবন ও সাধনা : সুশান্ত সরকার। কেরি সাহেবের মুনশি : প্রমথনাথ বিশী। উইলিয়াম কেরি : সজনীকান্ত দাস। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ : নিখিল সুর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। Memoir of William Carey DD : Eustace Carey . The Life of William Carey : George Smith.
২. রামমোহন রায় (Ram Mohan Roy) (১৭৭২/৭৪ –১৮৮৩)
হুগলির এক সম্পন্ন পরিবারে রামমোহনের জন্ম। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, আরবি-পারসি-সংস্কৃত-ইংরেজি ভাষায় নানা গ্রন্থপাঠ তাঁর সংস্কারমুক্ত, যুক্তিপ্রবুদ্ধ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেছিল। এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, যার অপরিহার্য উপাদান আত্মমর্যাদাবোধ। এই আত্মমর্যাদাবোধের প্রেরণায় তিনি ভাগলপুরের কালেকটর স্যার হ্যামিলটনের ঔদ্ধত্যকে প্রতিহত করেছিলেন।
রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন দেশের অনৈক্য ও অনুন্নতির মূলে আছে জাতি, ধর্ম, আচারগত বিভাজন। তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মূলে ছিল ঐক্য ও সংহতি স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৬ সালে আত্মীয় সভা, ১৮২১ সালে ইউনিটারিয়ান সমিতি, ১৮২৫ সালে বেদান্ত কলেজ, ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসভা (পরে যার নাম হয় ব্রাহ্ম সমাজ) স্থাপন করেন। নারীজাতির দুর্দশাও যে দেশের অগ্রগতির বাধা তা অনুভব করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে শুরু করেন আন্দোলন। ১৮২৯ সালে রদ হয় এই নারীঘাতী প্রথা।

সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮২৩ সালে লর্ড আমর্হাস্টকে লেখা চিঠিতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় না করে পাশ্চাত্য শিক্ষা — বিশেষ করে গণিত, বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা — প্রসারে জোর দিতে অনুরোধ করেন। হিন্দু কলেজ ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন। বাংলা ভাষাচর্চার গুরুত্বও অনুধাবন করেন। তিনি চাইতেন এদেশের রাজপুরুষরাও বাংলা ভাষা শিক্ষা করুন। তাই ১৮২৬ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘বেঙ্গলি গ্রামার ইন দ্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ’। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের অন্যতম রূপকার তিনি। তাঁর রচনার মধ্যে আছে বেদ-উপনিষদের অনুবাদ; সতীদাহ-সহমরণ –ধর্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্কমূলক পুস্তিকা; ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’, ‘ব্রহ্মসংগীত’ ইত্যাদি মৌলিক রচনা। রামমোহন ‘সম্বাদ কৌমুদী’, ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’, ‘মিরাৎ-উল-আখবার’ প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছিলেন।
প্রখর ছিল তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। পাশ্চত্যদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে তিনি যে আবেদন পাঠান, তাকে ‘অ্যারিওপ্যাজিটিকা অব ইণ্ডিয়া’ বলে উল্লেখ করেছেন সোফিয়া ডবসন কলেট। ১৮২৭ সালে জুরি রেগুলেশনে যে ধর্মীয় বিভাজন রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তিনি তার প্রতিবাদ করেন। উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত আন্দোলনেও রামমোহন সক্রিয় ছিলেন।
দ্রষ্টব্য.
মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন সমীক্ষা : দিলীপকুমার বিশ্বাস। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রামমোহন ও ব্যাক্তি স্বাধীনতা : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। রামমোহন চর্চা : ইতিহাসে বঞ্চনা ও অবহেলা : নির্মলা বাগচী। রামমোহন রায় : সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ : প্রদীপ বক্সী। Life and Letters of Raja Rammohan Roy : S, D,Collet . Last Days of Raja Rammohan Roy : M. Carpenter . Life and Letters of Raja Rammohan Roy (edt.) : Biswas and Ganguli
৩. তারিণীচরণ মিত্র (Tarinicharan Mitra) (১৭৭২-১৮৩৭)
উর্দু, হিন্দি, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত তারিণীচরণ ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্তানি বিভাগে দ্বিতীয় মুনশি পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি এই বিভাগের প্রধান মুনশি হন। ১৮১৭ সালে যে ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ গঠিত হয়, তার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সাধারণ সদস্য থেকে কর্মদক্ষতার গুণে তিনি এই সোসাইটির সম্পাদক হয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগিতায় তিনি ছাত্রদের জন্য ‘নীতিকথা’ নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ উদ্যোগ তিনি তিনি গ্রহণ করছিলেন।
তারিণীচরণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু এবং ‘ধর্মসভা’র সমর্থক। ১৮৩০ সালে সতীদাহ প্রথার সমর্থনে যে আবেদন পাঠানো হয়, তিনি তাতে স্বাক্ষর করেন। সে আবেদনের হিন্দি ও বাংলা অনুবাদ তিনিই করেছিলেন। জনসাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিদেশি শাসকের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি।
দ্রষ্টব্য.
তারিণীচরণ মিত্র (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২ খণ্ড) : The Government Gazette, 15th May, 1817. Social Ideas and Social Change in Bengal (1817-1835) : I. Riddhi.
৪. ডেভিড হেয়ার (David Hare) (১৭৭৫-১৮৪২)
জন্মসূত্রে বিদেশি হলেও ডেভিড হেয়ার বাংলা ও বাঙালির পরমাত্মীয়। স্কটল্যাণ্ডের এক গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৮০০ সালে কলকাতায় আসেন তিনি। কলকাতায় শুরু করেন ঘড়ির ব্যবসা। দীর্ঘ আঠারো বছর তিনি নিযুক্ত ছিলেন এই ব্যবসায়ে। কিন্তু তাঁর মনের তৃপ্তি ছিল না। তিনি চাইতেন এদেশের মানুষের জন্য কিছু করতে। তাই ১৮২০ সালে তিনি তাঁর ঘড়ির ব্যবসা সহকারীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে দেশের উন্নতি হতে পারে। ১৮১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টকে তিনি একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। সেই প্রস্তাবানুসারে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। ১৮২৫ সালে ডেভিড হেয়ার এই কলেজের পরিচালন সমিতির ডাইরেক্টর হন। স্কুল সোসাইটিরও সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। ১৮১৮ সালে স্কুল সোসাইটি যে অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন, তিনি ছিলেন তার ইউরোপীয় সম্পাদক। আরপুলি বাংলা স্কুল ও পটলডাঙার ইংরেজি স্কুলের পঠন-পাঠনের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। স্কুল সোসাইটি যে সব দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান ছাত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করত, ডেভিড হেয়ার তাদের নানারকম পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতেন। ১৮২৪ সালের ১৮ নভেম্বর স্কুল সোসাইটিকে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে দেশের আলোকপ্রাপ্ত ছাত্ররাই দেশের মঙ্গল করতে পারে। আলোচনা ও বিতর্কে ছাত্রদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতেন তিনি। নিয়মিত যাতায়াত করতেন ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘জ্ঞানোপার্জিকার সভা’য়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুত্ব দিতেন দেশীয় ভাষা শিক্ষাকে। বিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদকেও উৎসাহিত করতেন তিনি। হিন্দু কলেজের কাছে হিন্দু পাঠশালার ভিত্তি প্রস্থর তিনি স্থাপন করেন ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন। ১৮৩৫ সালের ১ জুন যে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তার পেছনেও ডেভিড হেয়ারের অবদান ছিল। শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারেও তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন।

নিজে খ্রিস্টধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি এদেশে খ্রিস্টান মিশনরিদের ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন। এই কারণে খ্রিস্টান মিশনরিরা তাঁকে পছন্দ করতেন না। এমন কি খ্রিস্টান সমাধিস্থলে তাঁর দেহকে সমাধিস্থ করতে দেওয়া হয় নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও বিভেদমূলক কাজের প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন। ১৮৩৯ সালে ইংল্যাণ্ডে যে ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ গঠিত হয়, তার সমর্থনে কলকাতার সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন।
দ্রষ্টব্য.
ডেভিড হেয়ার : প্যারীচাঁদ মিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্র বাগল। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী।। Life and Tims of David Hare : Sarojesh Mukherjee
৫. রসময় দত্ত (Rasmay Dutta) (১৭৭৯-১৮৫৪)
কলকাতার রামবাগানের এক ধনী অভিজাত পরিবারে রসময় দত্তের জন্ম। সংস্কৃত, আরবি, পারসি ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। এ দেশে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ১৮১৯ সালে দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য যে ‘হিন্দু কলেজ পাঠশালা’ স্থাপিত হয়, সেখানে তিনি ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগী। তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশন ও সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন কিছুকাল। ‘কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি’ ও ‘কলকাতা স্কুল সোসাইটি’র সদস্য হিসেবে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
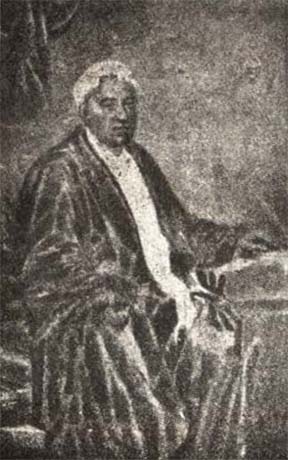
তবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল। তাঁর বিরুদ্ধতার জন্য ‘গৌড়ীয় সমাজে’ রাজনৈতিক আলোচনা হত না। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। কলকাতার ভিতরে ডাকমাশুল প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন তিনি, এই দেশকে ইংরেজের উপনিবেশে রূপান্তরিত করারও বিরুদ্ধতা করেছেন তিনি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন, কারণ তাঁর মতে সংবাদপত্র হল সাধারণ মানুষ ও সরকারের মধ্যে এক সেতুবিশেষ।
দ্রষ্টব্য.
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। The Modern History of Chiefs, Rajas and Zaminders (part-2) . Selections from Bengaliana by Shoshee Chunder Dutt (edt, by Alex Tickell) [ক্রমশ]