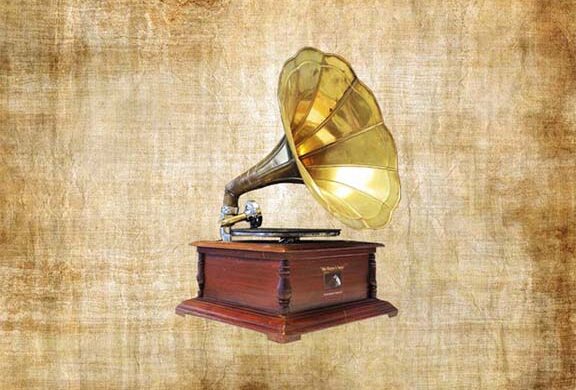
দশ
এর পরবর্তী যুগে বাংলা কাব্যসংগীতের নবজাগরণ ঘটে রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) ওরফে নিধুবাবুর টপ্পা গানের অবদানে (‘এ কি তোমার মানের সময়? সমুখে বসন্ত!)। লক্ষ্ণৌ নিবাসী গোলাম নবী ওরফে শোরী মিঞা (১৭৪৯-১৭৯৯) টপ্পা গানের সূচনা করেন। নিধুবাবু ১৮ বছর ছাপরায় ছিলেন ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত। সেখানেই তিনি গোলাম নবীর টপ্পার তালিম পান। সেই টপ্পার আদর্শে একটু বাঙালিয়ানা মিশিয়ে নিধুবাবু নিজস্ব ঢঙের টপ্পা রচনা শুরু করেন ১৭৯৪ সালে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরেই।
তাঁর স্বরচিত গীতিসঙ্কলনগ্রন্থ ‘গীতরত্ন’ দীর্ঘায়ু এই সংগীতকারের ৯৭ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় — যাতে কয়েকটি আখড়াই ও ব্রহ্মসংগীতসহ ১০৩টি রাগে রচিত সর্বমোট ৫৫৪টি গান আছে, যার প্রায় সবই টপ্পা। এর বাইরে আরও ৬৩টি গান সংগৃহীত হয়েছে এবং বাকি বহু গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে বাংলা গানের এই টপ্পাসম্রাট সংস্কার সাধন করে প্রচলিত আখড়াই গানকেও উল্লেখযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।
তিনি হিন্দুস্তানি টপ্পার ক্ষিপ্র গতি ও অলঙ্করণ পদ্ধতি ত্যাগ করে মধ্যলয়ে আন্দোলিত তান সহযোগে একপ্রকার মর্মস্পর্শী পায়নরূপ সৃষ্টি করেন। নিধুবাবু প্রবর্তিত এই গানের ধারা পরবর্তী বিংশ শতকজুড়েও বাংলার গীতপরিমণ্ডলকে অনুরক্ত করে রাখে। শ্রীগুপ্ত তাঁর টপ্পা গানের বাণীতে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যক্তিগত চেতনাকে বিকশিত করে তোলেন। বলা হয় যে তাঁর গানেই আধুনিক যুগের রোমান্টিক চেতনার প্রথম উদ্ভাস ঘটে। তিনিই প্রথম নাগরিক কাব্যসংগীত রচয়িতারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। রামনিধি গুপ্ত নিরঙ্কুশ মানবপ্রেম, একান্ত ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ এবং হৃদয়মন্থী এক ধরনের বিষণœ সুরলহরীর সাহায্যে বাংলা কাব্যসংগীতের আধুনিক যুগের পত্তন করেন। এ গানে বাংলার নিজস্ব রুচি ও মেজাজের প্রভাব স্পষ্ট। মিতায়তন কবিতার ভাবগর্ভতার মধ্য দিয়ে হৃদয়-ছোঁয়া সুরের মোটা দানার মসৃণ তরঙ্গে ফুটিয়ে তোলা আবেদনেই বাংলা টপ্পা গানের সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।
তাই এই চিত্তাকর্ষক গানের পরবর্তী স্বনামধন্য রচয়িতাদের সৃষ্ট অনেক জনপ্রিয় টপ্পাও নিধুবাবুর নামে প্রচলিত হতে দেখা যায়, যেমন শ্রীধর ভট্টাচার্য (১৮১৬-?) ওরফে শ্রীধর কথকের ‘ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে’। নিধুবাবুর নামে চলে কালীদাস চট্টোপাধ্যায় (১৭৫০-১৮২০) ওরফে কালী মির্জার অনেক টপ্পাও, যেমন ‘তুমি জান সই, আমি যত সই, এত কে পারে’, (‘সংগীতরাগ কল্পদ্রুম’) — যিনি বস্তুত টপ্পা গানের গায়ক ও রচয়িতা হিসেবে নিধুবাবুরও পূর্ববর্তী।
এর পরের পর্বে উদ্ভব হয় কবিগানের। ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর বক্তব্য অনুযায়ী আখড়াই ও কবিওয়ালার গান বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে উদ্ভূত হয়েছিল প্রায় একই কালে। প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন দুই দলের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে কবিগান পরিবেশিত হত। কবিগানের আঙ্গিকে একটা মজাদার ভঙ্গি ছিল। গানেরও ছিল একাধিক পর্যায়। যেমন আগমনী বা উমা-সংগীত, বিরহ, সখীসংবাদ, খেউড়। যদিও মৌলিকতার অভাবদোষে দুষ্ট, ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রায় দেড়শো বছর ধরে কবিগান বাংলাদেশে পুরোদমে প্রচলিত ছিল।
এই মর্যাদাহীন গান সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ ‘লোকসাহিত্য’ নামক প্রবন্ধে বলেন, ‘ভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন।’ তৎকালীন সমাজের নিম্নগামী রুচির অপ্রতিহত প্রভাব ও চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এই গান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবিওয়ালাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। এসব সত্ত্বেও কবিগানের ব্যাপক প্রচলন এবং দীর্ঘ স্থায়িত্ব গানের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে লোকপ্রিয়তার শক্তির জানানি দেয়।
টপ্পার পর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আরেকটি গীতধারারূপে কীর্তনের প্রচলন হয়। মূলত উচ্চস্বরে ভগবানের নামলীলা ও গুণসমূহের অনুশীলনের নাম কীর্তন। কীর্তন বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের একটি গীতরীতি। চৈতন্যদেবের পূর্বেই ভগবদভক্তি বিষয়ক এই ধরনের কীর্তনের রীতি প্রচলিত ছিল। সেকালে ‘গীতগোবিন্দ’ তো কীর্তনের ঢঙেই গীত হত। কারও কারও মতে প্রাচীন প্রবন্ধ গান থেকেই কীর্তনের উৎপত্তি। সত্যজিৎ রায় বলেন, ‘চৈতন্যদেবের আমলে রাগ-সংগীতকে গড়েপিটে বাঙালি করে কীর্তন গানের সৃষ্টিতে একটা প্রথম শ্রেণীর সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্তনে বাঙালিয়ানা তার ভাবে, ছন্দে, সুরে, অলঙ্কারে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে।’ পদাবলি কীর্তনে বাঙালির মর্মকথা ধ্বনিত। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের এত বেশি সংখ্যক গান কীর্তনের সুরভঙ্গিতে আধারিত।
পরবর্তী পর্বে ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে বাংলাদেশে ব্রহ্মসংগীতের উদ্ভব ঘটে। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের পুরোহিত রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ছিলেন ব্রহ্মসংগীতের প্রবর্তয়িতা। বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম, ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মচিন্তাকে অন্তর্মুখী নিবিড় ও প্রাণময় করার জন্যই ব্রহ্মসংগীতের সৃষ্টি। সকল সংস্কারের সংকীর্ণতাকে রামমোহন একাধারে দার্শনিক এবং নান্দনিক আবেদনে সমৃদ্ধ গানের ঝরনাধারায় ধুয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বহু খ্যাত-অখ্যাত গীতিকারদের ব্রহ্মসংগীত রচনায় বাংলা কাব্যগীতির একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় রচিত হয়েছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতগুণী যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রমুখ বহু শীর্ষ সংগীতকার ব্রহ্মসংগীতের সুর-সংযোজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি স্বশ্রেণির উন্নততম মানের বলেই এখনও তাঁর নিজের সংগীতভাণ্ডারের জনপ্রিয়তম অংশে বিরাজ করে। মোটকথা, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সমন্বয়ে ধ্রুপদী আঙ্গিকে রচিত ব্রহ্মসংগীত-শীর্ষক প্রকরণটি বাংলা গানের মহাফেজখানায় একটি বিশেষ সময়ের দলিল হিসেবে স্থায়ী সম্পদরূপে সংরক্ষিত থাকবে।
অষ্টাদশ শতকের শেষে, আনুমানিক ১৭৭৪ সালে বাংলা লোকগানের আঙিনায় লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০)-নামে এক বিরল প্রতিভাশালী বাউলসাধক ও সংগীতকারের আবির্ভাব ঘটে। এই মহাত্মার রচিত বাউল গান বাঙালির গানের ভাণ্ডারের এক অবিস্মরণীয় সম্পদ। লালনের গানে সবার উপরে মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে। বিভেদের সকল বেড়াকে ভেঙে দিয়ে গান কত গভীরভাবে মানুষের মনকে স্পর্শ করে তা একবার চৈতন্যদেব দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লালনের গানে সেই লক্ষণ পুনর্বার দেখা যায়। লালন শুধুমাত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকে না, কালে কালে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম হয়ে ওঠে। গানের এই ধারাটি শাস্ত্রীয় আচারসর্বস্ব মৌলবাদের প্রতিপক্ষে বস্তুবাদী মানবতাবাদের জয় ঘোষণা করে।
অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ, রামনিধি, রামমোহন প্রমুখের অবদানে বাংলার গানের ডালি সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও শতকটির মধ্যভাগ থেকে অন্যান্য শিল্পসাহিত্যের মতো গানের জগতেও একটা অবনমন দেখা দেয়। অবনমনের এই দুষ্কালে খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, কবিগান ব্যাপকভাবে বাংলার জনচিত্তকে গ্রস্ত করে রেখেছিল। গ্রামীণ মানুষ তো বটেই, কলকাতার শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকও দীর্ঘদিন ধরে এই অমার্জিত, চটুল গানে অত্যন্ত আমোদ বোধ করতেন। এই অবক্ষয় গ্রাস করে রাখে উনবিংশ শতকের প্রথমাংশেরও অনেকটা কাল।
প্রসঙ্গত লক্ষেèৗর নবাব ওয়াজিদ আলি শা’র (১৮২২-১৮৮৭) কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আজকের বাংলা গানের যে কালচার তাতে এই সংগীতগুণীর অবদান কম নয়। তাঁরই সৃজনশীলতার পথ ধরে বাংলায় গজল, ঠুংরি, কাওয়ালি ইত্যাদির প্রসার ঘটেছিল। তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশ থেকে ১৮৫৬ সালে তাঁকে কলকাতায় নির্বাসিত করেন লর্ড ডালহৌসি। নবাব তাঁর নাচ-গানের গোটা দলটাই সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং নির্বাসিত জীবনেও নৃত্যসংগীত চর্চায় মগ্ন থেকে বাংলার সংগীতভুবনে একটি বিশেষ মাহাওল বা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।
চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, মঙ্গলকাব্য, নগরসংকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কবিগান, টপ্পা, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ব্রহ্মসংগীত, বাউল ইত্যাদি সকল শ্রেণির গীতধারার রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে মিলেমিশে একাকার আজকের বাংলা গান। ফলে আধুনিক বাংলা গানে এমন এক অন্তর্লীন গুণপনা বর্তেছে যা মানব-হৃদয়ের তন্ত্রীতে এক অপ্রতিরোধ্য তরঙ্গ তোলে। অবশ্য হালের গানের এই মেলামেশার পালা শুরু হয়েছিল আদিম গান থেকেই। তাই আজকের আধুনিক বাংলা গানও এমন যে, তার দেহে যে-কোনও সাংগীতিক অলঙ্কার যেন অনায়াসেই মানিয়ে যায়। তাই অফুরান বৈচিত্র্যে ভরা এ গান সংগীতের শ্রেণিসচেতনতা মানে না। সুরে শুরু এবং সুরেই সারা — কথার ক্ষেত্রেও এই গানের প্রান্তর যেন তেপান্তর। [ক্রমশ]