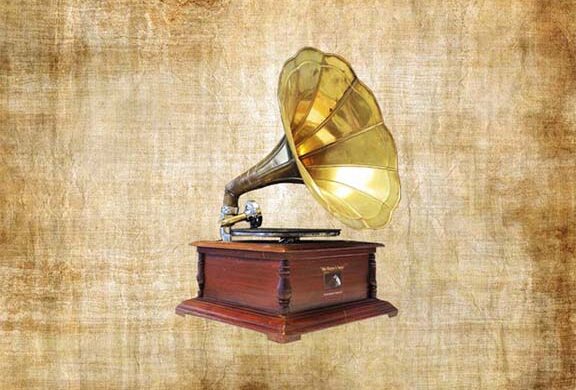
নয়
সিদ্ধাচার্যগণ দশম-একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই সময় সাধারণ লোকের মধ্যে গানের যে রীতি প্রচলিত ছিল সে রীতি অবলম্বনেই চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলা ভাষায় লেখা হলেও, চর্যাগীতিগুলিতে অবহট্টের নিদর্শন বিদ্যমান। চর্যাগানে একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনচারিতার নানা বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন চোলাই মদের ব্যবসা, নৌকো চালানো, পশুপাখি শিকার, মাছ ধরা, দই বেচা থেকে শুরু করে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ, ডোম, গুরু-গোঁসাই, নর-নারীর প্রেম ইত্যাদি। এই ছিল পরবর্তীকালের ঐশ্বর্যময় বাংলা কাব্যগীতির সূচনা। বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের বাউল গানেও এইসব চর্যার প্রভাব লক্ষণীয়।
এর পরের অধ্যায় দ্বাদশ শতকের ‘গীতগোবিন্দ’। রাধাবিরহের বিষয়কে কেন্দ্র করে গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যটি রচনা করেন জয়দেব। এতে মোট চব্বিশটি গান রয়েছে। গানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বনিঝংকার ও ছন্দোলালিত্য। গীতগোবিন্দের গানগুলিতে গুর্জর, বসন্ত, মালব, গৌড়, ভৈরবী প্রভৃতি দ্বাদশ রাগ এবং একতাল, রূপক, অষ্টতাল প্রভৃতি পাঁচটি তালের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালের অশেষ বৈভবের বাংলা গান নানাভাবে ‘গীতগোবিন্দ’র আবেদন ও অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে।
চতুর্দশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যের প্রচলন ও প্রসার ঘটে। মঙ্গলকাব্যগুলির সেই ধারা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জনচিত্তকে রসাবেশে আবিষ্ট করে রেখেছিল। ধর্মের অলৌকিক মহিমায় আচ্ছাদিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে স্থাপিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে একাধারে দেবদেবীর মাহাত্ম্য আর ধর্মের এক ভীতিজনক দিক — দুটি বিষয়ই অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের ধর্মাশ্রিত জনজোয়ার বাঙালির জনজীবনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করা ঘটনা। চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি সকল সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানবমিলন-ধর্মের মহাপ্লাবন এনেছিলেন। এখানে প্রচলিত ধারার দেবদেবী বিষয়ক ভক্তিরসের কোনও স্থান ছিল না। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর একমাত্র আরাধ্য। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে জনজীবনে উন্নত রুচির সহায়কের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বৈষ্ণবসাহিত্য ও সংগীত উৎকর্ষের চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। চৈতন্যের ভক্তিরসে দেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। চৈতন্যদেব এবং তাঁর শিষ্য-শিষ্যা দ্বারা প্রচারিত সংকীর্তনের প্লাবনে পদাবলি গান সাধারণের সাধনার বিষয়রূপে গণ্য হয়েছিল। সেই সাধনার প্রেক্ষিতে মানব-মিলনধর্মের
চর্চা বাংলার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পটভূমিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল। মানবধর্ম এবং পদাবলি গান — এই দুয়ে মিলে সমগ্র দেশকে সম্পৃক্ত এবং জনসাধারণকে আলোড়িত করেছিল।
এই পরিবেশেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বড়– চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতজনেরা মনে করেন, লেখকের নাম নিয়ে মতভেদ থাকলেও। প্রাচীন পাঁচালি কাব্যের আধারে বিন্যস্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বস্তুত নাট্যগীতি। চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মধ্যকালীন বাংলা ভাষার অবিকৃত রূপটি দেখা যায়। অনন্তাবতার বলরামের মথুরায় নীত হবার পর থেকে শুরু করে কৃষ্ণের মথুরাগমন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ, নানা ছলে উভয়ের মিলন, রাধার প্রেমে বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত।
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃতির পট বদলের সূচনা দেখা দেয়। ফলে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে রুচি-বৈভবের অবনতি ঘটে চলে। ঐতিহাসিক মূল্যায়নে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজে নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময় ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম্য অর্থনীতিতে ভাঙন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব, কলকাতার পত্তন, ইংরেজিমনস্ক ব্যবসায়ী-মুৎসুদ্দিদের আর্থিক উত্থান, প্রাচীন কাব্যধারার অবসান ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার সামাজিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের ঝাপটা এসেছিল।
ইতিমধ্যে ১৭৬০ সালে বাংলা গানের প্রথম আধুনিক গীতিকার রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’ মূলত নরনারীর দেহঘটিত মিলন বর্ণনায় সমৃদ্ধ হলেও মাতৃভাষায় সহজ, সরল বা প্রাঞ্জল উপস্থাপনার গুণে তৎকালীন নাগরিক জীবনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল — (‘কী বলিলি মালিনী! ফিরে বল বল/তোর রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥’)।
বাংলা গানের সমসাময়িক অপর প্রবাদপুরুষ হলেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) — (‘মা হওয়া কি মুখের কথা/শুধু প্রসব করলে হয় না মাতা ॥’)। আদিরস, নরনারীর প্রেম ইত্যাদি বিষয়ের প্রভাবকে সযতেœ এড়িয়ে এই মাতৃভক্ত মজেছিলেন বাৎসল্যরসের একমুখী সংগীতসাধনায়। আত্মমগ্ন মাতৃ উপাসনা এবং মানববৃত্তিপ্রধান আধ্যাত্মিকতার মহিমামণ্ডিত অপার্থিব গীতিকবিতার স্রষ্টারূপে রামপ্রসাদ প্রাতঃস্মরণীয়। কারণ তিনি একান্তই নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও সুরশৈলীতে সমগ্র বাংলাদেশকে চিরকালের মত বিমোহিত করে গেছেন। তাঁর প্রসাদী গানের প্রভাব বাংলা গানের পরবর্তী সকল স্রষ্টার ওপরই লক্ষণীয়, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ওপরও (‘প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে/রাঙা চরণতলে নেচে নেচে ॥’)। [ক্রমশ]