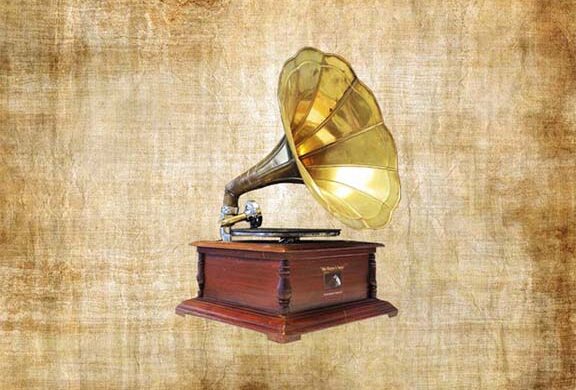
সাত
পরিবর্তনশীল সমাজের গতিময়তায় অনেক সময় ছন্দপতন ঘটে থাকে। তাই বলে গতি কখনওই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে না। অতীতকে সঙ্গী না করে বর্তমান এগোতে পারে না। এই প্রক্রিয়াতে গানের ক্ষেত্রেও অতীত নানাভাবে মিশে থাকে। সেই আদিমাবস্থা থেকে সমাজের সঙ্গে গানের গাঁটছড়া বাঁধার কাজটা সম্পন্ন করেছিল প্রাচীন মানুষ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধনকে যুগোচিত চেতনায় আরও মজবুত করে তুলেছে মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের মানুষ।
যুগে যুগে সমাজ-অঙ্গের নানা পরিবর্তনের প্রভাব সংগীতের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়ভাবেই বর্তায়। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব তো কখনওই এড়িয়ে যাবার নয়। তাই বোঝাতেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — ‘সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে। সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।’ (সংগীত)।
মধ্যযুগের প্রথমদিকের পরেপরেই ভারতবর্ষে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। স্বাভাবিকভাবে এই পর্বের গানও মূলত মুসলিম প্রভাব ও ভাবধারায় উন্নত হয়েছিল। প্রধানত উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করে মুসলিম গীতধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে অসাধারণ সংগীতগুণী আমীর খসরুর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁরই বিস্ময়কর প্রতিভাবলে ভারতীয় সংগীতের পরিবারে প্রবন্ধ ও ধ্রুপদের সঙ্গে মিলল নতুন কয়েকটি গীতধারা — কাওয়ালি, তারানা, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, হোরি, চৈতী, মান্দ, গজল, গীত ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই ছিল বিজ্ঞানসম্মত কৌশলসর্বস্ব গানবাজনা — যাতে হৃদয়ের আর্তি থেকে বেশি প্রকট হত কালোয়াতি।
মূলত রাজা-রাজসভা, নবাব-বাদশা প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় উস্তাদদের পারদর্শিতা প্রকাশ এবং উচ্চাঙ্গের সংগীতবোধ-সম্পন্ন শ্রোতাদের রসাস্বাদনের জন্যেই এই সব গীতধারার চর্চা হত। ফলে সে যুগে গীত পরিবেশন এবং চর্চার ক্ষেত্রে উস্তাদদের আধিপত্য এবং রাজকীয় অর্থেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। এর সঙ্গে রাজা ও রাজসভার সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নও ছিল বিশেষভাবে জড়িত। মোটকথা, গানের চর্চার ক্ষেত্রে প্রেরণার একটা বিরাট উৎস ছিল মর্যাদার যুদ্ধ ও রাজানুকূল্য।
জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার উদ্যাপিত কালোয়াৎ বা একালের সেলিব্রিটি হবার জন্যে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনচারিতায় অভ্যস্ত উস্তাদগণ একটা নির্দিষ্ট উচ্চবিত্তের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেই সংগীতচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সকল কারণে মুসলিম প্রভাবিত মার্গসংগীতের ধারাও সর্বস্তরের শ্রোতার মনোরঞ্জনের উপযুক্ত ছিল না। তবে শুধু শাস্ত্রীয়সংগীতের গভীর কর্ষণই নয়, দেশীয় গানের ব্যাপক প্রসারও এই সময়ের গানের পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছিল।
উত্তর ভারতীয় সংগীতের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতগুণীরাও মধ্যযুগে সংগীতকে এক গৌরবোজ্জ্বল স্তরে উন্নীত করেছিলেন। তাঁদের অবদানস্বরূপ রাগমালিকা, পদম্, কীর্তনম্, কৃতি প্রভৃতির উদ্ভবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কিন্তু উত্তর এবং দক্ষিণের এই সময়ের প্রচলিত গীতরীতিগুলি ছিল বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন ও পদ্ধতির অনুসারী। তাই এই জাতীয় গান সর্বস্তরের মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারেনি। উস্তাদি গানের শিল্পীগণের অবস্থান ছিল সাধারণ শ্রোতাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে বা আওতারই বাইরে।
যে-কোনও মৌলিক শিল্পের মতো সংগীতেরও চরম এবং পরম সার্থকতা রসিকজনের হার্দিক পরিতৃপ্তিতে। শ্রোতা বিনে গান মিছে। সার্থক গান শ্রোতাকে সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে বাধাবন্ধনহীন অসীমে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দান করে। সেই মুক্তি শুধু মস্তিষ্কসৃষ্ট গান দিতে পারে না, দিতে পারে কেবল হৃদয়যুক্ত গান। তাই গানের বিকাশ বা সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর জন্মস্থান এবং শ্রোতার রুচির ওপর তার প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবজ্ঞাত হলে চলে না। শ্রোতাসাধারণ গ্রহণ না করলে সংগীতের আবেদন একসময় ব্যর্থ হয়, তার অগ্রগতিও হয়ে যায় স্তব্ধ।
উত্তর ও দক্ষিণী সংগীতজ্ঞরা ভারতবর্ষীয় সংগীতের যে-ভিত রচনা করে দিয়েছিলেন, আজকের বাংলা গানও সেই ভিতের উপরেই পারফর্ম করে যাচ্ছে — কথাটা যতই কষ্টকল্পিত শোনাক না কেন। মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতগুণীরা ক্ষণকালের আভাস হতে ফুটিয়ে তুলে সাজিয়ে গুছিয়ে চিরকালের তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গানের বিবিধ সম্ভার — যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক বাইশটি শ্রুতির শনাক্তি, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর বিন্যাস, উপস্থাপনার সময়চক্র এবং প্রয়োগকৌশল প্রভৃতি।
বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী আমীর খসরু উদ্ভাবিত স্বর-ব্যবস্থার ফলে দরবারের ক্রিয়াত্মক গানের আসরে শুদ্ধ ও কোমল স্বরযুক্ত সপ্তকের প্রচলন সম্ভব হয়। এই স্বর ব্যবস্থার প্রয়োগ মুসলিম ঠাটপদ্ধতির উদ্ভাবনেও সহায়ক হয়। ঠাট দ্বারা রাগ-রাগিণীর বর্গীকরণ, পুরুষ রাগের স্বরকাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে স্বরের অল্পত্ব-বহুত্ব ঘটিয়ে অংশ-স্বর ও গ্রহ-স্বরের প্রচলন এবং বিশেষত খেয়ালের প্রবর্তন প্রভৃতি মুসলিম-অবদানের কথা উপমহাদেশের সংগীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ সংগীতকলার এসমস্ত পুষ্টিবিধায়কের শুভ প্রভাব উপমহাদেশীয় সংগীতের সকল শ্রেণির সঙ্গে বাংলা গানেও নানাভাবেই বর্তেছে — সেসব আপাতদৃষ্টিতে দুর্নিরীক্ষ্য হলেও।
আট
সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে সামাজিক পরিবর্তনের পথ ধরে সাংগীতিক রূপান্তরও স্বভাবতই ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াতেই নবাব-বাদশাদের আনুকূল্যনির্ভর দরবারি ও পেশাদারি শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল। কারণ মূলত সমাজের ওপরতলার মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত উচ্চাঙ্গ সংগীতশাস্ত্রীদের গান সমাজের অপেক্ষাকৃত নিচে অবস্থানকারী বৃহত্তর গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।
এর পর ছিল ইউরোপীয়দের আগমনকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রভিত্তিক শাসনের কারণে পরাধীন ভারতবর্ষবাসী দেশজ সংস্কৃতিকে আগলে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তরঙ্গকে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগে শাস্ত্রীয় সংগীতের যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল ক্রমশ তা জনমানস থেকে দূরে সরে যেতে থাকে বিস্মৃতির দিকে।
পরিবর্তিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থায় শ্রোতাসাধারণ আঞ্চলিক ভাষা ও লোকজ সুরভিত্তিক গানের প্রয়োজন বেশি করে উপলব্ধি করতে লাগল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রতিকূলতা ছিল নানাবিধ। সামাজিক উত্থান-পতন, গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরণ, জয়যাত্রা
কখনও অবক্ষয় — অতঃপর বিলুপ্তির কিনার থেকেও আবার বেঁচে ওঠা। আদিম যুগের অপরিণত গান তো বৈদিক এবং বেদান্ত যুগে অনেকটাই উন্নত হয়েছিল। তবু সময়ের ব্যবধানে মধ্যযুগের সংগীতের প্রেক্ষাপটে এসে দেখা গেল সে-গানের অনেক রূপ ও আঙ্গিকই জীর্ণ পরিধেয়ের মতো পরিত্যক্ত হয়েছে অযত্ন, অথবা সযেেত্নই।
মধ্যযুগের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতধারা কখনওই উপমহাদেশের বৃহত্তর লোকসমাজকে বা সমাজের লোকায়ত জীবনাচরণকে স্পর্শ করেনি। যে-কোনও জাতি বা দেশের নরনারীর হৃদয়ের আকুতি লোকগীতিতে সহজ সরলভাবে প্রকাশ পায়। তাদের আশা-নিরাশা আনন্দ-বেদনা লৌকিক গায়নে এবং স্থানীয় বাদনে মূর্ত হয়ে ওঠে। নিত্যকার জীবন সংগ্রামের বাণী সুরের ছোঁয়ায় গান হয়ে মানবমনকে উদ্বেল করে — যেমন বৈষ্ণবের কীর্তন, মাঝির ভাটিয়ালি, মৈষালের ভাওয়াইয়া। তাই মধ্যযুগের শেষ পর্বে গানের নব নব রূপায়ণের ফলপরিণামে নানা ধরনের লোকগান বা পল্লীগীতির উদ্ভব ও প্রসার ঘটে।
বর্তমান ও অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে মার্জন ও সংশোধন করার জন্যও প্রয়োজন ভালোমন্দভেদে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার। মোটামুটিভাবে মধ্যযুগ থেকেই এই যোগসূত্র জোরালো হতে থাকে। এর প্রমাণ মেলে চর্যাগানে। বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম সংগীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন সর্বপ্রথম সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম অনুভূতি পরিচায়ক চর্যাগীতিগুলিতেই পাওয়া যায়। [ক্রমশ]