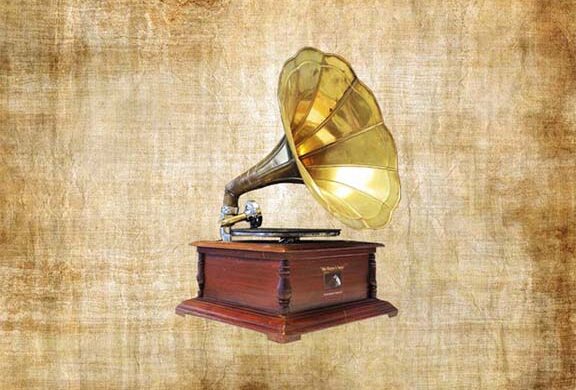
পাঁচ
নিয়মনিষ্ঠ এবং বর্ণসচেতন যাজ্ঞিক পুরোহিত, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণদের আধিপত্যবর্জিত গান বৌদ্ধ যুগে বিভিন্ন সংগীতজ্ঞ রাজা এবং সংগীতমনস্ক সাধারণ মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় বিকাশ লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা, সুরপ্রয়োগ ও গায়নপদ্ধতি একটা সমবায়ী ভূমিকা পালন করেছিল। বেদান্ত যুগের তুলনায় বৌদ্ধযুগ থেকে গানের একটা গুণগত পার্থক্য স্পষ্টতই লক্ষণীয়। এই পার্থক্যের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত জনপ্রিয় সুর, গানের সরল গঠন, ভাষার সহজবোধ্যতা, সমাজের গ্রহণবর্জন প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি শ্রোতার রুচির গুরুত্ব ছিল প্রধান।
চালুক্যবংশের রাজা এবং মানসোল্লাস গ্রন্থের রচয়িতা তৃতীয় সোমেশ্বরের (খ্রি. ১১২৭-১১৩৭) পুত্র ছিলেন জগদেকমল্ল। সংগীত চূড়ামণি নামক গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে দেশজ বা আঞ্চলিক গানগুলি সংগীতের নানাবিধ গুণ ও লক্ষণযুক্ত হয়ে ক্রমশ উন্নতরূপে আর্য ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ‘প্রকীর্ণ’ নামে। পরবর্তীকালে আরও উন্নত এবং পরিমার্জিতরূপে পরিবেশিত প্রকীর্ণ গানকে ‘বিপ্রকীর্ণ’ সংগীত নামে অভিহিত করা হয়। গুপ্তযুগের শুরুতে ‘বিপ্রকীর্ণ’ শ্রেণীর কিছু কিছু গানে গান্ধর্বসংগীতের সুকঠিন সাংগীতিক বিধি সন্নিবিষ্ট করে সংগীত পণ্ডিতেরা সৃষ্টি করেন ‘প্রবন্ধ’ নামক ‘অভিজাত’ ধরনের এক প্রকার দেশি গান। চর্যাগানের উৎসও এই প্রবন্ধ গান।
প্রবন্ধ গানে বিভিন্ন পদ, তাল ও ছন্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা পরিমিতিবোধের প্রকাশ ছিল। এ গানে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার হত। রাগের উদ্দেশ্য হল একটা সুনির্দিষ্ট সাংগীতিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে কথা ও সুরের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করে মানুষের মনোরঞ্জনের নিশ্চয়তাবিধান। এই পরিকাঠামোর প্রথম স্তর হল ‘আলাপ’, যাকে বলা যায় পরম শুদ্ধ সংগীত। ভাষাহীন আলাপে শ্রোতা পরম শুদ্ধরূপে কোনও রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। আলাপের পর বিস্তার। বিস্তারের স্তরে শ্রোতার মনে ভাব স্থায়ী আসন পাতে। ভাব স্থায়ী হবার আগে রসের সঞ্চার হয় না! আবার ভাবকে নির্দিষ্টরূপে প্রকাশের জন্য ভাষার প্রয়োজন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে সুর ও কথার একটা সম্মোহনী
দোলায় শ্রোতার মন মেতে ওঠে। সার্থক হয় গান।
এখানে উল্লেখ্য যে, কথা ও সুরের যথার্থ আত্মীয়তা বা মেলবন্ধনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের মাধ্যমেই এদেশীয় সংগীতের প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে। যুগে যুগে বিভিন্ন সংগীতগুণী তাঁদের উপলব্ধ জ্ঞান, অনুভূতি ইত্যাদির দ্বারা যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত গানের সৃষ্টি করেছেন — সেই সৃষ্টির মধ্যে পূর্বাপর অনুক্রমে পারম্পর্য রক্ষিত হয়। কিন্তু সেই পারম্পর্য কতটা রক্ষিত, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উপমহাদেশীয় সংগীতের ইতিহাসে বাংলা গান ‘রাগে’র জন্মক্ষণ থেকে সুদীর্ঘকালীন বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, যার সর্বশেষ প্রজন্মের নাম আধুনিক বাংলা গান। তাই বলা যায় যে, সাংগীতিক ঐতিহ্যের এই শাস্ত্রীয় ধারা থেকে কখনও বিযুক্ত না হওয়াটা বাংলা গানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।
ফিরে যাই প্রবন্ধ গানে। পণ্ডিত এবং সংগীতশাস্ত্রীদের রচনা থেকে আমরা প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের কথা জানতে পাই। সেই শ্রেণিবিভাগের ফলে আজ আমরা ধ্র“পদ গান এবং সেই গানকে অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী প্রভৃতি অংশে সাজাবার অবকাশ পেয়েছি। বাংলায় প্রথম ধ্রুপদ গানের প্রচলনের ক্ষেত্রে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজার অবদান আছে। তিনি দিল্লি থেকে বিলাস খাঁর শিষ্য বিখ্যাত ধ্রুপদগুণী মিশ্রি সিং ঢাড়ীকে বাংলায় নিয়ে আসেন, সম্ভবত ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষে ধ্রুপদের প্রবর্তন এবং প্রসারের ক্ষেত্রে নায়ক গোপাল এবং নায়ক বখশুর নাম চিরস্মরণীয়, যাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি হলেন মিয়া তানসেন। তাঁর কন্যাবংশীয় উস্তাদদের কাছ থেকেই বাংলা তার ধ্রুপদ গান পেয়েছে।
ধ্রুপদ গান প্রসঙ্গে চিরকালই অবশ্য-স্মর্তব্য থাকবেন মহাসংগীতকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহু ধ্রুপদাঙ্গ গানে রবীন্দ্রসংগীতের কালজয়ী ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। তিনি কিন্তু ধ্রুপদকে অনুকরণ করেননি, করেছিলেন অনুসরণমাত্র। এই মহাবাগ্মেয়কারের হাতে বাণীর মহিমায় ও ভাবের সৌরভে গানগুলি এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছে যে তাতে শ্রোতা চিরকালই অভিভূত হতে থাকবেন। আঙ্গিককে অক্ষুণ্ন রেখে, মনোমত বাণীর সংযোজনায় গানের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি তাঁর সৃজনে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। কথা ও সুরের যুগলসম্মিলনে কবির ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলি তৃতীয় এক ভাবের ভাষা নির্মাণ করেছে। তান-বোলতান-ঠাট-বাট বর্জিত সেই গানগুলি যতটা নির্ভার-নিটোল ততটাই সারগর্ভ। প্রাচীন যুগের শেষ প্রান্তের সুপরিণত গান ছিল প্রবন্ধ, যার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী গানে।
ছয়
প্রবন্ধ গানের পরেই গুপ্তযুগে গানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়নের এক চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। এই উন্নতি ছিল মূলত বাদ্যযন্ত্রকেন্দ্রিক। বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসে গুপ্তযুগের একটা বড় অবদান ছিল — জীবজন্তুর নাড়ী-নির্মিত তন্ত্রীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে ধাতুনির্মিত সূক্ষ্ম তারযুক্ত নানাবিধ বীণার ব্যাপক প্রচলন ও প্রসার। একমাত্র তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রেই সমস্ত শ্রুতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকাশ সম্ভব। তাই গানের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই প্রকার বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব অপরিমেয়।
সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত সংগীতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গানে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা সর্বজনগ্রাহ্য। বিশেষ করে তাঁর বীণাবাদন বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর ঈর্ষার কারণ ছিল। তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তও শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। গুপ্ত রাজাদের অবদানে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা গান গান্ধর্ব সংগীতের লক্ষণাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে উপমহাদেশীয় সংগীতকে বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ করেছিল। ইতিমধ্যে প্রচলনে চলে আসা নাটকে ও নৃত্যে এসব তারযন্ত্রসমৃদ্ধ সংগীতের অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় — যা রঙ্গনটীদের কলানৈপুণ্য, কলামাধুর্য, অঙ্গভঙ্গি ও রস পরিবেশনকে নানা কলেবরের নানা ঝংকারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল।
আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে শিক্ষাকার নারদ, ভরত, কোহল, দত্তিল, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর প্রমুখ সংগীতগুণীর অবদানে উপমহাদেশীয় সংগীত ক্রমশ স্তর থেকে স্তরে উন্নীত হয়েছিল। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী পরবর্তীকালের গানের পৃষ্ঠপোষকগণ সংগীতের ঐতিহ্যকে যথাযথ মর্যাদায় লালন করেছিলেন। নৃত্যের সৌন্দর্য এবং গানের মাধুর্য
প্রকাশের জন্য নর্তক-নর্তকী এবং গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। এই সকল নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে রাজকীয় প্রেরণায় সংগীতের উন্নয়নে গুপ্তরাজত্বকালে এক নবযুগই প্রবর্তিত হয়েছিল।
পরিশীলিত শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপক চর্চার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কলাকুশলী, শিল্পী ও সর্বস্তরের মানুষের প্রাণোচ্ছল অংশগ্রহণ। গান্ধর্বযুগের পরবর্তী গানের প্রেক্ষাপটে
রাজা-রাজড়া, শিল্পী-শ্রোতা প্রমুখের সমবেত প্রচেষ্টায় সংগীতের আলোকচ্ছটা যেন উপমহাদেশের সমগ্র অধিবাসীকেই উদ্ভাসিত করেছিল। এতখানি যে, গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম স্বদেশি সংগীতের সঙ্গে বিদেশি সংগীতের সংমিশ্রণ ঘটে। [ক্রমশ]