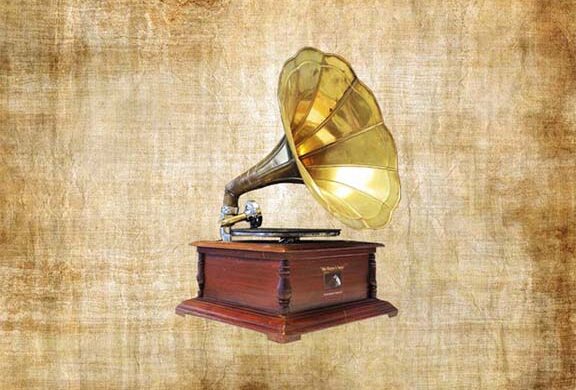
তিন
বৈদিক যুগের শেষভাগ থেকে নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে প্রসারিত হওয়ার প্রেরণায় গানে রূপান্তর ঘটল। পুরোহিত এবং যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের চর্চার আঙিনা ছেড়ে গান সাধারণের জীবনে সংক্রামিত হল। সেই গান ব্যাপকতা লাভ না করলেও বিজ্ঞানমনস্ক সংগীতসাধক গান্ধর্ব গুণীদের প্রতিভাবলে গান্ধর্বসংগীতের উদ্ভব হয়েছিল — সামগানের সাংগীতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লৌকিক গানের সংমিশ্রণের ফলেই।
শোনা যায় হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী কান্দাহার বা গান্ধার দেশের অধিবাসী গন্ধর্বরা ছিলেন সংগীতের জন্মগত সাধক। যে গান সকলের শেখার বা গাইবার অধিকার ছিল না, সেই গান ক্রমে সকলের গান হয়ে উঠেছিল। শ্রুতিমতে, গান্ধর্বগুণীদের অবাধ যাতায়াত ছিল দেবকুলে এবং মনুষ্যসমাজে। ফলে তাদের গান পুষ্ট হয়েছিল সংগীতচর্চার সেই সুবিস্তৃত পরিসরে। ঘটেছিল দেবসমাজ ও লোকসমাজের সাংগীতিক ঐতিহ্যের সুসমন্বয়।
সামগানের সাংগীতিক ঐতিহ্য মূলত তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক ছিল। তাই সেই অলৌকিক গানে মানুষের মনের ‘সাধারণ অবস্থা’র প্রকাশ ঘটত না, ফলে গানও মানবিক হয়ে উঠত না। লৌকিক সুরমিশ্রিত গান্ধর্ব গানই কালে কালে মানুষের গান হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। কারণ এ গান বৈদিক সংগীতের স্তোম, স্তোত্র, ঋক, সাম গাথা প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামগানের সাংগীতিক উপাদানের সঙ্গে লৌকিক গানের সামাজিক উপকরণের সংমিশ্রণ এবং গান্ধর্বগুণীদের কল্পনাবৃত্তির কৌলীন্য মিলে সমাজের প্রয়োজন এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকল সংগীতমনস্ক ব্যক্তির গাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠেছিল গান্ধর্বগান।
এটা সাধারণ জ্ঞান যে, অনুকরণে শিল্প ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী গান্ধর্বসংগীতজ্ঞগণ তাই বৈদিক গানের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, ভাব, রস, সহজ ভঙ্গি ইত্যাদির অনুসরণে সৃষ্টি করেছিলেন গান্ধর্বগানের — অনুকরণে নয়। এর সঙ্গে দেশি বা আঞ্চলিক গানের বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত হয়ে গান্ধর্বগানে এসেছিল এক নতুন মাত্রা। সভ্যতার আদিযুগের ফসল গান্ধর্বগান উপমহাদেশীয় সংগীতের ক্রমবির্বতনে এক অত্যুজ্জ্বল পর্ব।
বিবর্তনের বর্ণিত প্রক্রিয়াটিতে লক্ষণীয় যে সংগীত স্বভাবতই দেশি হয়ে যেতে চায়, কারণ সংগীতের জন্য কান পেতে থাকে জনপদের হৃদয়। একই কারণে মার্গসংগীত উঠে যায় শাস্ত্রের পাতায়। ইতিহাস-সেরা সংগীতাচার্য শার্ঙ্গদেবও বলেছেন — যা সমসময়ে মঞ্চে গীত ও শ্রুত হয় তাই ‘পারফর্মিং মিউজিক’ কিংবা ক্রিয়াত্মক সংগীত বা ক্রিয়াসিদ্ধ সংগীত। বাকি সবই শাস্ত্রীয় সংগীত বা তত্ত্বীয় সংগীত।
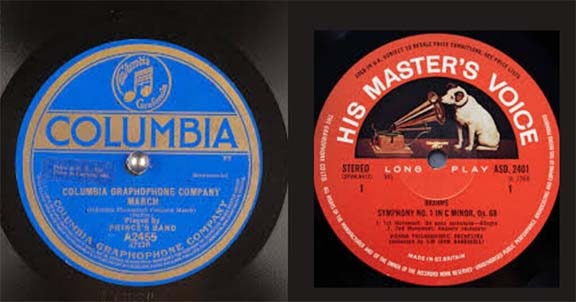
চার
সমাজের পালাবদল পরিবর্তন আনে মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য বৃত্তি সংগীতেও। এ পরিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে বেদান্ত-যুগে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে সমাজের নানা ক্ষেত্রে একটা ভিন্নমাত্রার রূপান্তর লক্ষ করা গেল। এই পর্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ছিল ধর্মীয় আধিপত্য থেকে দৈনন্দিনের যাপিত জীবনে মানুষের মুক্তির আকুলতা। বেদান্তযুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের শৃঙ্খল মোচনে উদগ্রীব এই নতুন চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন ‘পরিব্রাজক’ ও ‘শ্রমণ’ নামে পরিচিত দুই সন্ন্যাসীগোষ্ঠী।
প্রখ্যাত ভারতবিদ ব্যাসামের মতে ভারতবর্ষের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা এই বৌদ্ধযুগ থেকে ক্রমে নগরকেন্দ্রিক হতে থাকল। শ্রম-বিভাজনের ফলে নানা শ্রেণির মানুষের জীবনচারিতা, চিন্তাধারা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দিতে লাগল। এই রকম এক সামাজিক পটভূমিতে বৈদিক অনুশাসন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নানাবিধ অবিচার-অত্যাচার ইত্যাদির অবসানকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নতুন নাগরিক গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। রক্ষণশীল সনাতনধর্মে বিশ্বাসীদের সঙ্গে প্রগতিশীল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উদার আদর্শগত এই ব্যবধানের ফলে শ্রেণিশাসিত মানুষ নতুন পথের সন্ধান পেল।
বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সমাজে মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য ছিল ‘মুক্তি’। সেই সত্যকে মানুষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তার প্রকাশ ঘটেছিল। ফলে সে সময় রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে গিয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধযুগের সাংগীতিক বিকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃতিতে উচ্চমানসম্পন্ন গান্ধর্ব-গানের উদ্ভব এবং সমৃদ্ধি ঘটেছিল ঠিকই। তবু তার আকর্ষণক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা সীমাবদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই।
তবু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে চর্চিত গান্ধর্বগান ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই গান্ধর্বগানও বিলুপ্ত হয়েছিল সকলের গেয় বা অনায়াস চর্চার উপযুক্ত ছিল না বলে — গান যেহেতু একাকী গায়কের নয়। লৌকিক সুরসমৃদ্ধ হলেও গান্ধর্বগানের চর্চাও ছিল দেবাঙ্গনকেন্দ্রিক। সংগীতশাস্ত্রে উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন গন্ধর্বগুণীরা বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে গান্ধর্বসংগীত পরিবেশন করতেন মূলত মন্দিরে। ভাষার সীমাবদ্ধতাও পরবর্তীকালে গান্ধর্বগানের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ ছিল।
দেবাঙ্গনের গান নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ধারণ করার পর্যাপ্ত অবকাশ না থাকায়। অথচ বৈদিকযুগের গানের তুলনায় বৈদিকোত্তর গান্ধর্বগান আলঙ্কারিক গুণে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু সেই অলঙ্কার বা বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণের ক্ষমতা তো সবার ছিল না। এখনও সকলের নেই উচ্চাঙ্গসংগীতের জটিল কারুকার্য আয়ত্ত করার দক্ষতা। তাই আঙ্গিকের দিক থেকে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধর্বগান শ্রোতার বাঞ্ছিত আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত রয়েই গিয়েছিল। এককথায় বলা যায় গান্ধর্বগানও জনচিত্তের উপযোগী গান হয়ে ওঠেনি।
বৌদ্ধযুগে সংগীতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গান্ধর্বসংগীতের ক্রমিক অবলুপ্তি এবং দেশি বা আঞ্চলিক গানের শ্রীবৃদ্ধি ও আভিজাত্য অর্জন। গৌতম বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধ রাজাদের কল্যাণে জনপ্রিয় দেশজ বা আঞ্চলিক সুরগুলি কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ‘দেশি রাগ’ হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করে। প্রসঙ্গত মতঙ্গমুনি (খ্রি. ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী) তাঁর ‘বৃহদ্দেশী’ গ্রন্থে বলেছেন :
‘তত্রাদৌ, স্বরবর্ণাবিশিষ্টেন
ধ্বনিভেদন বা পুনঃ।
রজ্যতে যেন সচ্চিত্তং স রাগঃ
সম্মত সতাম ॥
অথবা, যোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্ত
স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রক্তকো জনচিত্তানাং স রাগঃ
কথিতো বুধৈ ॥’
বিশেষজ্ঞগণ সংজ্ঞাটির অর্থ করেছেন — স্বর ও বর্ণের বিশিষ্ট প্রয়োগ অথবা সুসঙ্গত ধ্বনিভেদ দ্বারা যদি ‘সৎচিত্ত’ ব্যক্তিদের মন রঞ্জিত করা যায় তবে তাকে ‘রাগ’ বলতে হয়। অথবা স্বরবর্ণ বিভূষিত এইরূপ বিশিষ্ট ধ্বনি যদি ‘জনচিত্ত’ রঞ্জকের কারণ হয়, তবে পণ্ডিতগণ তাকেও রাগ বলবেন। উল্লিখিত সংজ্ঞাটি থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ‘জনচিত্ত’ বলতে সাধারণ শ্রোতাদের কথা বোঝানো হয়েছে। এঁদের মন এবং কান — কোনওটাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা তৈরি নয়। ‘সৎচিত্ত’ কথাটি দ্বারা সংগীত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী শ্রোতার কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতানুযায়ী ‘সৎচিত্ত’বান শ্রোতা বা সংগীতগুণীরা মার্গ-রাগের প্রতি অনুরক্ত। প্রতিপক্ষে ‘জনচিত্ত’বান শ্রোতা তথা গণমানুষ আসক্ত দেশি রাগের প্রতি। সারকথা — দুধরনের শ্রোতা দুধরনের রাগ দ্বারা রঞ্জিত হন। বিভাজনটি এখনও বলবৎ আছে।
সনাতন ধর্ম প্রচলিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত। ফলে উদারতাই এই নবধর্মের বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ঐতিহ্যের স্বাভাবিক আভিজাত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের কৃত্রিম অহংকারের পরিবেশে সংস্কৃত ভাষাকেন্দ্রিক সংগীতচর্চা কখনওই
ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-মূর্খনির্বিশেষে সাধারণের হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সমাজে দেশজ সংস্কৃতি মূলত প্রাকৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে স্থান-কাল-পাত্রভেদে অনায়াস এবং অবাধ চর্চার আনুকূল্যে বিকশিত হয়েছিল প্রাণবন্তভাবে। তাই এই পর্বে গান্ধর্বসংগীত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে স্মর্তব্য যে — গান্ধর্ব সংগীতের মুন্সিয়ানা, সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক সংগীতশাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আত্মস্থ করেই বৌদ্ধ যুগের সংগীত পুষ্ট হয়েছিল।
বৌদ্ধযুগের অমূল্য জাতকগুলি থেকে আমরা সমকালীন নৃত্য, গীত, বাদ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে পারি। জাতকগুলির মধ্যে সাংগীতিক বর্ণনার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মৎস্য-জাতক, গুপ্তিল-জাতক, বিশ্বম্ভর জাতক প্রভৃতি। এর মধ্যে মৎস্য-জাতকে ‘মেঘগীতি’ এবং গুপ্তিল-জাতকে ‘উত্তম’ ও ‘মধ্যম’ মূর্ছনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল বর্ণনা থেকে বৌদ্ধযুগে, সৃজনশীল এবং পূর্বোক্ত গীতিধারাগুলি থেকে পৃথক, উন্নত এক সাংগীতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। [ক্রমশ]