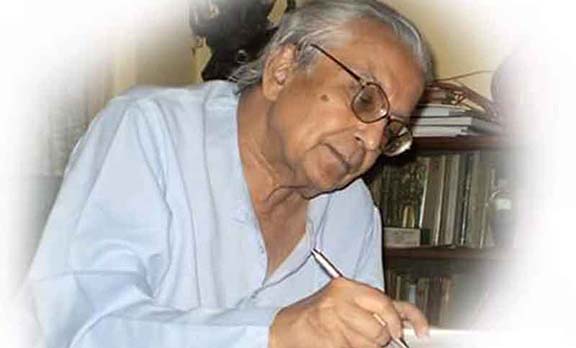
তুলসীতলার আজলকাজল মায়ামদির নিরাপত্তা থেকে একবার বেরিয়ে পড়লে ইহমানুষের কপাল থেকে বাবস্তুদেবতার আশীর্বাদ চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায়, তার বরাতে তখন চলতে থাকার চালচিত্তির ছাড়া অন্যতর কোনো বিধিলিপি আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন থেকেই সম্ভবত শুধুমাত্র ভাষাই হয়ে ওঠে মানুষের একমাত্র আবাসন। এই মানবদরদি বীজমন্ত্র, সংবেদী সুধীজন ভালো করেই জানেন, স্বয়ং দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার প্রণীত। এই জানাটুকু, তৃপ্ত ঝিলের ওপর ঢিল ছুঁড়লে যেমন ক্রমশই পরম্পরাঘনিম বৃহত্তর বৃত্তাংশ তৈরি হতে থাকে, একটি অনাহত প্রত্যয়ের প্রতিশব্দ হয়ে আর থাকে না, কিছু-কিছু প্রশ্ন তুলবার সুযোগ এনে দেয়। আমরা তখন স্পষ্ট করে জেনে নিতে চাই, প্রজ্ঞাপ্রবীণ দার্শনিক হাইডেগার কি জানতেন নাহোমারের বাড়িঘর বলতে কিছুই ছিল না। আর দান্তেকে গৃহী হওয়া সত্ত্বেও গৃহ পরিহার করতে হয়েছিল।
লি-পো আর তু-ফু পথহারা সেই যুদ্ধবিগ্রহের
তিরিশ মিলিয়নের মতো মানুষকে যা গিলে ফেলেছিল
অয়রিপিদিসকে লোকজন মামলা দিয়ে ভয় দেখিয়ে চলেছিল
আর চেপে ধরা হয়েছিল শেক্সপীয়রেরও টুঁটি।
ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁকে শুধু শিল্পসরস্বতীই নয়
পুলিশরাও খুঁজে বেড়াত
লুক্রেশিয়াসকেও যেতে হয়েছিল নির্বাসনে
আর হাইনেকেও কিনা এবং অবিকল সেই মতোই
ব্রেশ্টকেও ভিড়ে যেতে হয়েছিল ডেনমার্কের ছন-ছাউনির আড়ালে।
(‘কবির দেশান্তর’, বের্টোল্ট ব্রেশ্ট)
হাইডেগার স্পষ্টই জানতেন। তা সত্ত্বেও এক সময় তিনি নাৎসি ফ্যুরারের বর্বর ইহুদি হনন এবং নির্বাসনের সমর্থনে বড়োই বিহবল হয়ে পড়েছিলেন, নাহলে কেনই-বা তিনি জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি অথচ ইহুদি পাউল সেলানকে পথে-চলে-যেতে-যেতে কবিসুলভ স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকেই একরকম প্রবুব্ধ করেছিলেন, সেই জিজ্ঞাসা কিন্তু দ্ব্যর্থ-দ্যোতক, অমীমাংসিত থেকে যায়।
জর্জ বুশ যখন গাল্ফ যুদ্ধ প্রযোজনা করেন, বিশেষত তখন থেকে, নিতান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অঙ্গীকার থেকেই বলছি, ‘স্বদেশ থেকে কেমন বিতাড়িত’ কতো যে কবি মাতৃভাষাকে সম্বল করে বিশ্বভুবনে কীর্ণ হয়ে গিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই কোনো। ব্রেশ্টের ভাষাতেই বলি :
দেখেছি সাত স্বদেশ থেকে কেমন বিতাড়িত
হয়েও তারা ভুলে যায়নি পুরনো পাগলামি :
ওদের মধ্যে বদ্লে যাবার মাধ্যমে স্বস্থিত
রয়েছে যারা, তাদের নিয়েই সপ্রশংস আমি।
সত্যের সৌজন্যে এখানে কবুল করতে চাই, অধুনা জার্মানিতে বসবাসরত অনাবাসী এই কবিদের সঙ্গে – কেউ আজ ট্যাঙি-ড্রাইভার কেউ-বা মজুর কিংবা
পার্ট-টাইম ডাকহরকরা—সারাদিনমান আমার ওঠা-বসা। বেশিরভাগ সময়েই আমার ডেরায় জমে ওঠে আমাদের মুশায়েরা। আমাদের এই কবিসম্মেলনে, বলা বাহুল্য, অনুবাদ-কবিতাই হয়ে ওঠে প্রিয় একটি মাধ্যম। অনেক সময় এঁদেরই আর্তিঅনুরোধে আমায় পরিবেষণ করতে হয় কখনো-বা, যৌথ উদ্যোগে তাঁদেরই সহায়তা নিয়ে, কোনো বিশ্বকবিতা, প্রায়শই শরণার্থীর নিয়তি নিয়ে লেখা কোনো কবিতা, যেমন ব্রেশ্টের, আজও, কিংবা আজই, যা আমাদের নখাগ্র পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক :
আমার দেশবাসীদের কাছ থেকে পালিয়ে
পৌঁচেছি এখন ফিনল্যান্ডে। গতকাল পর্যন্ত
যেসব বন্ধুকে চিনতামই না তারা
পরিচ্ছন্ন ঘরে পেতে দিল কয়েকটা ধবধবে বিছানা
লাউডস্পীকারে থেকে-থেকে অতি উচ্ছন্নে-যাওয়া
নাৎসিদের বিজয় ঘোষণা।
কৌতূহলবশে ভূম-লের মানচিত্র খুলে ধরি।
উপরের ল্যাপল্যান্ড থেকে উত্তুরে মেরুসাগর পর্যন্ত
দেখতে পাচ্ছি এখনো যেন একটা দরজা খোলা
আমার শ্রোতারা চমকে ওঠে, বলে, ‘তোমার মাতৃভাষায় কবিতাটা তর্জমা করবে তো?’ দু-চারজন, হয়তো তেমন মৌলবাদী নয়, বলতে চায়, ‘আচ্ছা, জার্মানির কোনো কবি কি আমাদের – যেমন পারসিক – ভাষাঞ্চলের কোনো মহাকবির সন্ধানে অমন করে বেরিয়ে পড়েননি?’ সঙ্গে-সঙ্গে বলটা টেনিসজাল ছাপিয়ে আমার উঠোনে এসে পড়ল। বাগ্মীর শৌর্যে আমি বলতে থাকলাম :
‘কেন? যোহান হেবাল্ফগাঙ ফন গ্যোয়েটে? তোমরা ভেবে দ্যাখো, ১৮১৪ নাগাদ ইয়োরোপের উপর থেকে নেপোলিয়নের কব্জি আল্গা হয়ে এলে তিনি পুব জার্মানিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজদরবার থেকে এক লহমায় বেরিয়ে পড়লেন তাঁর জন্মশহর পশ্চিমমুখী ফ্রাংকফুর্টে, সঙ্গে নিলেন য়োসেফ ফন হামার-পুর্গস্টালের জার্মান তর্জমায় পারস্যের মহাকবি হাফিজের (১৩২৫-৯০) কাব্যগ্রন্থ দিভান। ইয়োরোপের বাইরে না গেলেও, অথবা তাঁর দিক থেকে তার দরকার না পড়লেও, হঠাৎই পুঁথিপট খুলে এক জায়গায় আবিষ্কার করলেন কোরানের একটি বচন (২/১৪২) : ‘আলস্না তো পুব আর পশ্চিমের। ইচ্ছে করলেই তিনি সঠিক পথে সমস্ত-কিছুই চালনা করেন।’ ব্যস, তারই অনঘ অভিঘাতে গ্যোয়েটে লিখে ফেললেন অনবদ্য চার লাইন :
ঈশ্বরের নিজস্ব এই প্রাচী।
ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতীচী।
যা-কিছু রয় উত্তরে ও দক্ষিণ অঞ্চলে
শান্তি নিয়ে জুড়িয়ে আছে তাঁরই তো করতলে।
আমি আমার বাঙ্ময়তা নতুন খাতে নিয়ে যাওয়ার মুখে আবুল মাহ্মুদ, জালালুদ্দীন রুমী-র পাঁড় ভক্ত, বলে উঠল : ‘তাতে কী হলো? তুমি কি গ্যোয়েটের ওই সংবেদনের সমাচার তোমার মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছ?’ অভিমানিত আমি আত্মরক্ষার কাঠগড়ায় ভর করে বলে উঠলাম : ‘মাহ্মুদ, গ্যোয়েটের হাফিজপ্রাণিত প্রাচী-প্রতীচীর মিলনবেলার পুঁথি (West-oestlicher Divan/ ১৮১৯) বাংলায় তর্জমার কাজ আমি আজ রাতেই শুরু করে দেব, তুমি আমার উপর ভরসা রাখো।’ মাহ্মুদ তখন : ‘তা তো হলো, কিন্তু ইয়োরোপে বসে কীভাবে একজন মহাকবি প্রাচ্যের আস্বাদ পাবেন! তাঁকে তো শরণার্থী হয়ে আমাদের দেশে আসতে হবে—তাই না?’ আবারও, গ্যোয়েটের ভাবপ্রতিমা বজায় রাখতে চাওয়ার আপ্রাণ প্রয়াসে আমি তাকে বলি : ‘জানো তো আবুল, কলকাতায় ছিল টিপু সুলতানের (১৭৪৯-৯২) প্রাচ্য গ্রন্থাবলির বহুবিখ্যাত লাইব্রেরি। গ্যোয়েটে সশরীরে সেখানে গিয়ে হাফিজের দিভান-সংক্রান্ত যাবতীয় পুঁথি অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। তখনকার দিনে যখন-তখন বার্লিন-কলকাতা করা সম্ভব ছিল না। এখনো কি আছে? জানো না, ফ্রাংকফুর্ট থেকে আজও যদি আমি যে-কোনো মুহূর্তে সরাসরি কলকাতায় চলে যেতে চাই, তার কোনো উপায় নেই। দুবাই অথবা দিলিস্নতে গিয়ে দিনের পরে দিন কাটিয়ে, যদি কপালে থাকে, সবশেষে মা গঙ্গার পায়ে তুমি জলাঞ্জলি দিতে পারবে নিজেকে!’
সহনশ্বরদের কবিতাউৎসব থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে বিবিক্ত করে আমার খুব কাছের কোনো কবির সাযুজ্যে চলে আসি। শুধু গ্যোয়েটের কাছে মন্ত্রশিষ্যত্ব পরিগ্রহণ করলে তো চলবে না, বিশ্বসংসারে আরো অনেক কবি বিদ্যমান যাঁরা গ্যোয়েটের চেয়েও অনেক দুরবগাহ ভাষাশিল্পী। এঁদের মধ্যে হ্যোল্ডারলীন, হাইডেগারের প্রিয়তম, একজন। অস্তিত্বের শেষ ছাবিবশ বছর দিব্যোন্মাদ দশায় তিনি যেসব আখর বুনে গিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার কোনো তুলনা নেই, যেমন :
তবুও মানুষ তার কুঁড়ের ছাউনিতেই থেকে যায়, তার পরনে
কুণ্ঠিত বেশবাস, অন্তর্মুখী, নিবিড় অভিনিবেশে, রক্ষা করে সত্তার
চৈতন্য, যেরকম যাজিকা আধান করে স্বর্গীয় আগুন, এই
বুঝি মানুষের বোধ। তার মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা আর ভুল
করবার চিন্ময় শক্তি ও প্রতিপূরণের ক্ষমতা দৈবত, সব
বিভূতির মধ্যে ভয়ঙ্কর, ভাষার অধিষ্ঠান, যা মানুষকেই
দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সৃজনরত, বিধ্বংসী, অধোগামী,
এবং অনন্ত জীবনে ও শিক্ষয়িত্রী আর জননীর কাছে
পুনরাবর্তনময় তার ভঙ্গি ও বিন্যাস, আসলে সে কে, কীই বা
তার উত্তরাধিকার, আর শিক্ষাদীক্ষা, মা’র কাছে অর্জনলব্ধ
সেই পারমিতা, সেই প্রেম সব-কিছু আগ্লিয়ে যা রাখে।
মন্ত্রমুগ্ধতায় আমি মাথা নিচু করে থাকি। এই তাহলে ভাষার আবাসন যা মাতৃভাষাকে ভেঙে-ভেঙে নির্মিত হয়েছে, তার অর্থ : মানবভাষার ভাঙনের উপরেই ভিত্তি পায় কবির ভাষা এবং সেইখানেই কবির আবাস। অনিবার্যতই মনে পড়ে যায় বিনয় মজুমদারকে আর তাঁর শেষ কয়েকটি বছর। বুক ভেসে যায় চোখের জলে। কিন্তু আমার সমস্যাটা তো অতো অব্যবহিত ক্যাথার্সিসেই চুকেবুকে যাবার নয়, আমাকে যে কবিতাটা বাংলায় ভাষান্তরিত করতে হবে। কীভাবে সেটা করে উঠব! হ্যোল্ডারলীন তো এখানে জার্মান ভাষার নিয়মকানুন অন্বয় সমস্তই ভেঙেচুরে নটরাজের খেলায় উন্মাতাল। বিনয়ের মর্জিমেজাজও অনেকটা এই ধাঁচেরই, তবু যে তিনি ছন্দ ও মাত্রা বজায় রেখেই লিখে চলেছেন। হ্যোল্ডারলীনের কবিতাটি শনাক্ত করতে গিয়ে তবু শেষ পর্যন্ত দেখি, তলডুবুরির রুদ্ধশ্বাস সতর্কতায় আমি তার নিভৃত ছন্দোলিপি তৈরি করতে পারি যাতে কবিতাটিকে থেমে থমকে স্ক্যান করা যায়, আর তৎক্ষণাৎ তাকে আমার মাতৃভাষায় তর্জমা করে বসি। অনাবাসীর এই দায় যে স্বভাষা ও প্রদত্ত বিশ্বভাষার মধ্যে অনবরত সেতু বাঁধতে হয় তাকে – গৃহবাসীর কাছে কারো এমন কোনো প্রত্যাশা নেই বলে সে ভুলে ভরা প্রাত্যহিক স্বভাষা ভাঙিয়ে দিবিব বেঁচে বর্তে থাকে। অনাবাসীকে সেতু সন্ধিতেই রাত কাটাতে হয়, কেননা কোথায় কে জানে কখন সাঁকোর কোন্ খাঁজটা অকেজো হয়ে পড়লে নতুন পদ্ধতি লাগিয়ে তার মেরামতি করতে হবে যে!
কোনো-কোনো মহান্ কবি আবার অনাবাসী অনুবাদককে তাঁর কাজটা সহজ করে দেওয়ার মর্মে যেন সচেষ্ট থাকেন। যেমন রিলকে। দুর্গ থেকে দুর্গ, পান্থভবন থেকে পান্থশালার সঞ্চারপথে স্বরচিত দুর্জ্ঞেয় বাঁচার গহবর থেকে তিনি, ততটাই ভ্রাম্যমাণ অনুবাদকের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এই তো আমি, অর্ফিউস, প্রেমিক ও শিল্পীর অন্তিম সমীকরণ, আমার নারীকে ঈশ্বরীর জায়গায় উন্নীত করে দিতে চাইছি :
যেন সদ্য সুকুমারী, নির্গত হয়েছে ভাগ্যবতী
কণ্ঠসংগীত আর বীণাযন্ত্রের মধ্য থেকে,
ঝলে উঠল স্বচ্ছ ওই বসন্তের উত্তরীয় তার,
আমার শ্রবণে গিয়ে শয্যা পেতে রইল শ্রীমতী।
ঘুমোলো আমার মধ্যে। সমস্ত-কিছুই নিদ্রা তার :
যে সমস্ত গাছ আমি প্রশংসা করেছি, অনুভূত
এই ব্যবধান, এই অনুভবে জেগে-থাকা মাঠ…
আমার বিস্ময় যত—সবি তার ঘুমের শিকার!
কবির হাত থেকে লুফে নিই এই দিব্যাবদান, তিনিও আমার এই বাস্কেট-বল-খেলুড়েপ্রতিম সপ্রতিভতাকে সানন্দ প্রশ্রয় দেন, আর আমি বুঝে নিতে পারি, মূলত সনেটের ঠামেই তিনি যে এই কবিতাটি লিখতে চেয়েছেন। ব্যস, তক্ষুনি আমার আরব্ধ দায়ভাগ চরিতার্থ হয়ে গেল। যে-কথা এখানে এখুনি বলতে চাই সেটা হলো এই যে, বাংলায় লেখা চতুর্দশপদীর ঐতিহ্য আমার আবহমান মজ্জায়-মজ্জায় অনুস্যূত হয়ে লেগে আছে বলেই রিলকের ‘অর্ফিউসের প্রতি সনেটগুচ্ছ’ অনায়াসেই আমি বাংলাভাষায় অন্তর্বৃত করে নিতে পারলাম তো? তাহলেই বোঝা যায়, অনাবাসী অনুবাদকও এক-একটি স্বর্ণিল সময়সুযোগে মূল ভাষার কবিকে তৃতীয় বিশ্বের অঙ্গনে টেনে নিয়ে এসে বেশ কিছুদিন বাঁচামরার অধিকার বর্তিয়ে দিতে পারেন। বাংলা ভাষায় রিলকের এই সনেটের পুনর্বাসন ঘটিয়ে আমার এরকম একটি অলীক আত্মপ্রসাদ ঘটেছিল।
এই আলেখ্যের প্রথমাংশেই এরকম একটি আভাস দিয়েছিলাম, জগৎজোড়া শরণার্থীদের সান্নিধ্যে আমি ঋদ্ধ হয়েছি। আজ আমি যখন কোনো নতুন-লেখা বাংলা কবিতার মূল্যাঙ্কন করতে চাই, তখন-তখনই মধ্যপ্রাচ্য কিংবা উত্তর আফ্রিকা থেকে শরণাগত নবীন কোনো কবির সঙ্গে তড়িঘড়ি শলাপরামর্শ করে জেনে নিই, এই পদ্যটা কবিতা হয়ে উঠেছে তো? শুধু সাম্প্রত বাংলা কবিতা কেন, ধ্রম্নপদী জার্মান কবিতার উত্তরণ নিয়েও তার সঙ্গে নিরন্তর বাদবিসংবাদ চলে আমার। ফলত, এটাই স্বাভাবিক, রিলকের এই অনবদ্য সনেট নিয়ে আমি সেই আবুল মাহ্মুদকে তার যাথার্থ্যগুণ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, আবুল বলে উঠল, ‘দ্যাখো, তোমার ওই হ্যোল্ডারলীন বা রিলকের এই সব লেখালেখি যে মহান্ তা নিয়ে আমি একবিন্দু সন্দিহান নই। কিন্তু, তুমিই বলো, অলোকরঞ্জন, আজ আমাদের ধ্বংসবিধুর এই বিশ্বপটে এসব কবিতা আমাদের একফোঁটা কাজেও লাগবে বলে এখনও তুমি কি মনে করো?’
তাকে আমি বোঝাতে চাই, একমাত্র অনুবাদের মুহূর্তেই কোনো কবি ও কবিতার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করা যায়। আবুল যেহেতু রাত্রিদিন আরব ভাষায় জার্মান কবিতা তর্জমা করে চলেছে, তাকে আমি এই মর্মে উদ্দীপিত করতে চাই, উৎসভাষাকে স্বভাষায় আনতে গিয়ে কীরকম বিপস্নব ঘটে যেতে পারে। এই সূত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই পূর্বসূরি সতীর্থ, পরা-শরণার্থী হবাল্টার বেঞ্জামিনের ‘অনুবাদকের দায়িত্ব’ (Aufgabe des Übersetzers) প্রবন্ধটিকে আমাদের নন্দনতত্ত্বের মানদ- হিসেবে ধরে নেওয়ার কথা তার কাছে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজেরই কাছে ব্যক্ত করি : উৎসভাষাকে নিজের ভাষায় উন্মুক্ত করে দেওয়াটাই আমাদের আসল কাজ। আমাদের লক্ষ্যক্রম হলো অনুবাদ্য ভাষার ধাঁচ ও ধরন স্বভাষায় ঢুকিয়ে দেওয়া এবং সেই মুক্তিবোধের গরজে নিজের ভাষার বহুব্যবহৃত শতজীর্ণ বেড়াগুলোর সমাপ্তিসাধন। এসব কথা যখন বলছি, কলকাতামুখী আমার ফ্লাইটের বড়ো জোর দেড় ঘণ্টা দেরি।
বুকপকেটে আমার স্বপ্রবাসী হাইনরীশ হাইনে-র ‘জার্মানি : এক শীতার্ত রূপকথা’ (Deutschland : ein Wintermärchen)—দেশে গিয়েই তার বাংলা ভাষ্য আমায়, বইমেলার মুখে, প্রকাশ করতে হবে যে :
ছিল বিমর্ষ নভেম্বরের মাস,
দিনগুলো আরো হয়ে এল ম্রিয়মাণই,
বাতাস ঝরাল গাছগাছালির পাতা,
সে সময় আমি চললাম জার্মানি।
আর যেই আমি পৌঁচেছি বর্ডারে,
শুনতে পেলাম দারুণ ধুকধুকুনি
বক্ষি আমার, এমন-কি মনে হলো
চোখে জল ঝরা শুরু হবে এক্ষুণি।
যেই শুনলাম জার্মান কথা বলা
বড়ো অদ্ভুত লাগল চেতনাটায়;
আর কিছু নয়, মনে হলো মনোরম
রক্ত হৃদয়ে ছায়।
গান গাইছিল কিশোরী বীণাবাদিনী
হয়তো সে-গান আন্তর অনুভূত,
যদিও বেসুরো, তবু তার বাজানোয়
সত্যিই আমি হয়ে গেছি আপ্লুত।
নেতাজি সুভাষ হাওয়াই বন্দরে উপনীত হয়েই বুঝতে পারলাম, হাইনের এই কবিতাটা যেন আমার। শুধু ‘জার্মান’ শব্দটা ‘বাংলা’য় বদ্লে নিলে এই স্তবকগুলি পুরোপুরি আমারই কি হয়ে যেত না? এমন-কি বিমানবন্দরে এক বঙ্গরঙ্গিলা পপ-গায়িকার ভুল ভাষায় বাংলা উচ্চারণ আমায় সেই গোধূলিতে মনে করিয়ে দিয়েছিল, আমার এথনিক ও আত্মিক উত্তরাধিকার আ মরি বাংলাভাষা ক্ষয়ে যেতে-যেতেও থিরথিরে জোনাকিপুঞ্জের মতো এখনো যেন জেগে রয়েছে, আর, আমি জানি, আমার আসা-যাওয়ার চলাচলের মধ্য থেকেই, এমন-কি যখন আমি স্থবির হয়ে যাব, তখনও লুপ্তপ্রচল আমার মাতৃভাষার সংস্কারসাধন, বেঞ্জামিনের সস্নেহ সতর্কীকরণের রক্ষাকবচ আঁকড়িয়ে ধরে, আমার নাভিশ্বাসের মুহূর্তেও সজাগ হয়ে থাকবে।
আমি জানি, আমার এই এষণা অনেকের কাছে দুঃসহ স্পর্ধিষ্ণু বলে মনে হতেই পারে। তবু আমি হাল ছাড়িনে। আমি তো আদৌ উদ্বাবস্তু নই। তবু সাহস পাবার জন্যে খুলে ধরি আমার আর-এক পূর্বসূরি বের্টোল্ট ব্রেশ্টের ‘নির্বাসনের জার্নাল’। তিনি তখন
যখন-তখন আমার মতো দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারেন না, মার্কিন প্রবাসের মুখে নাৎসি পিশাচেরা তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে যে! এমন সন্ধিক্ষণে ফিনল্যান্ডের সাময়িক পুনর্বাসনের পর্বাঙ্গে তিনি স্বদেশ থেকে বিতাড়নের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলতে চেয়ে, পরিকল্পিত অ্যানেস্থেসিয়ার মতো, সে দেশের নিসর্গের গুণগান করেছিলেন : ‘এই প্রকৃতি খুবই সমৃদ্ধ, বৃহৎ সৌন্দর্যের কী-এক সমাহার; মাছভরা জলাশয়, সুন্দর গাছভরা অরণ্যানী, তাদের মধ্যে বার্চ আর বেরির মাদকতাগুণ ওতপ্রোত হয়ে আছে।’
কিন্তু আমার অন্যতম এই পূর্বাচার্য তো শুধুমাত্র নিসর্গের মোহিনী মায়ায় মজে যাওয়ার জন্যই মানবজন্ম পরিগ্রহ করেননি। তাই, আচম্বিতে তিনি তাঁর মনোরম্য নিসর্গসম্মোহ খারিজ করে দিয়ে জলে ভাসতে-ভাসতে খেয়াঘাটের মাঝিকে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন তুলে খুঁচিয়ে মারেন :
সে শুধায় নেয়েকে যে বেয়ে চলে কাঠের তক্তায় :
এ বুঝি কাঠ যা ছাড়া ক্রাচলাঠি হয়না কখনো?
আর দ্যাখে এক জাতি, দু-ভাষায় রয়েছে মৌন।
(‘ফিনল্যান্ডের নিসর্গ’/ Finnische Landschaft)
আর আমি বুঝে নিতে পারি, দিব্যদর্শী এই কবি আমার সংকটেরই স্বরলিপি বুনে দিতে চাইছেন, বলতে চাইছেন, দুই বাংলার মধ্যে আছাড়িবিছাড়ি খেয়ে একই ভাষা কীরকম দু-ভাষায় দীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন, এবং সেই দুই ভাষাতেও দ্বিভাষাভাষীরা আর বাংলায় কথা বলতে পারছে না। এ অবস্থায় নিতান্ত অনাবাসী আমি কি হাইনে তর্জমার মাধ্যমে আমার বাংলাভাষার জন্যে খুব নতুন-কিছু করে উঠতে পারব?