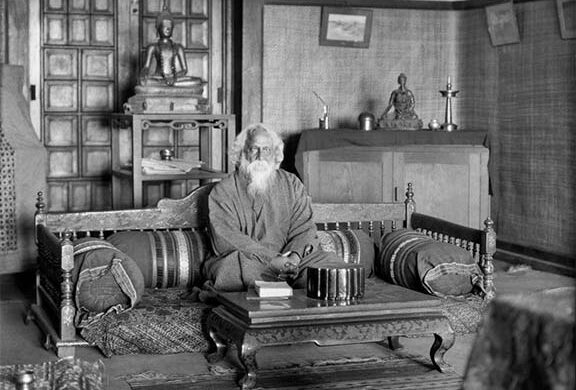
পৃথিবীর সভ্য জগতের সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের বাইরে তাঁকে স্মরণ করা হবে প্রধানত বিশ্ব-নাগরিকরূপে, বাঙলার বাইরে ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁকে স্মরণ করা হবে প্রধানতঃ ভারতীয় কবিরূপে এবং আমরা বাঙালী তাঁকে স্মরণ করবো প্রধানতঃ বাঙালী কবিরূপে।
এ কিছু বিচিত্র নয়। জর্মানির সাধারণ জনের পক্ষে জানা কঠিন যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস গোত্রের লোক কিংবা ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি সরকারী খেতাব বর্জন করেন—অর্থাৎ তাঁর খাঁটি ভারতীয় রূপ তার চোখে পড়বে না। সে প্রধানতঃ স্মরণ করবে সেদিনের কথা যেদিন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, সে জাতি-সমাজে অপমানিত এবং সেদিন ‘টাগোর তাকে শুনিয়েছিলেন ‘পরাজিতের গান’—‘দি সং অব দি ডিফীটেড।’ ঠিক সেই রকমই চীন স্মরণ করবে, জাপান যেদিন তাকে পদানত করবার চেষ্টায় রাজ্য লোলুপ ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে সেদিন রবীন্দ্রনাথ চীনের হয়ে জাপানকে তার স্বধর্ম, তার সত্য ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।
স্পেন কিংবা নরওয়ে ঠিক এ-ভাবে দেখবে না। তবে তারাও দেখবে তাঁর বিশ্ব-নাগরিক রূপ, তাঁর বিশ্বকবি রূপ।
‘হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি।
***
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
***
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।’
টীকা টিপ্পনির সাহায্যে যদি বা ফরাসী কিংবা তুর্ক এ কবিতাটির মূল অর্থ ধরতে পারে সে হবে কবিতাটির তথ্যের বা জ্ঞানের দিক, এবং সেই যদি তার কাম্য হয় তবে এ কবিতা না পড়ে ভারতবর্ষের যে কোনো প্রামাণিক ইতিহাস পড়লেই তার জ্ঞান সঞ্চয় হবে অধিকতর। এ কিছু নূতন নয়, আমরাও পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসের অনেকাংশ এই ভাবেই পড়ে থাকি। পক্ষান্তরে যে কোনো শিক্ষিত ভারতীয়, যার হৃদয় মন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যাগত আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন, তার কাছে কবিতাটি অনুভূত হবে রস স্বরূপে। আরেকটি সরলতর উদাহরণ দি —
মুখে তার লোধরেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।১
এ কবিতাটি পড়ে বিদেশীর জ্ঞান সঞ্চয় হবে, ভারতীয় রমণীর প্রসাধন সম্বন্ধে, কিছুটা রস যে পাবে না সে কথা বলি না, কিন্তু যে রসিক কালিদাসের নায়িকাদের সঙ্গে সুপরিচিত তার হৃদয়ে অনুভূত হবে এক অভূতপূর্ব আনন্দ—প্রাচীন দিনের আধা-চেনা গন্ধের সঙ্গে মিলে গিয়েছে আজকের দিনের চেনা-গন্ধ, ঠাকুরমা তাঁর সিন্দুক খুললে প্রাচীন দিনের কর্পূর-মঞ্জরীর গন্ধ যখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তখন যদি আজকের দিনের ভরা আষাঢ়ের নব মালতীর সুবাস তার সঙ্গে মিশে যায়। ইংলণ্ডের ঠাকুরমাও সিন্দুক খুললে তার থেকে বেরোয় প্রাচীন দিনের ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, সঙ্গেও মিশে যায় আজকের দিনের ডাফোডিলের গন্ধ। বুঝি, কিন্তু রস পাইনে।
অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতোত্তর কবি সেখানে তিনি বিশ্বকবি। তাঁর ‘ডাকঘরের’ অমল মানবাত্মার প্রতীক, রাজার চিঠি ভগবদ্প্রেমের অনুপ্রেরণা। সকলেই জানেন প্যারিস বার্লিন ভিয়েনায় সে নাটক কী পরিমাণ সর্বজন প্রিয়। ‘বিসর্জন’ কি সে পরিমাণ রসসৃষ্টি ওসব জায়গায় করতে পারবে?
এবারে অবাঙালী অথচ ভারতীয়দের কথা নিন।
‘আমরা গেঁথেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা—’ প্রতি শরতে রবীন্দ্রনাথ এই কাশের প্রতীক্ষা করেছেন। জর্মানির মিউনিক শহরে সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল দেশের কথা—
‘ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীল গগনে
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে।’
এবং দেশের স্মরণে গানটি শেষ করছেন,
‘আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে৷৷
এই কাশ নিতান্তই বাঙালী কবির আদরের ধন। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় যখন আমি শান্তিনিকেতনে পড়তুম তখন এক গুজরাটি ভদ্রলোক আশ্রম দর্শনে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাশ কি বস্তু? সৌভাগ্যক্রমেই তিনি শরৎকালেই এসেছিলেন। দেখিয়ে দিলে তিনি পরম যত্নে আঁটি আঁটি কাশ বাঁধতে লাগলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালে পর তিনি বলেন তিনি পূর্ব আফ্রিকা গাঁধী আশ্রম থেকে এখানে এসেছেন, হিন্দী অক্ষরে ছাপা ‘গীতাঞ্জলিতে’ কাশের উল্লেখ দেখে তাঁর কৌতূহল হয়েছিল, এবারে গুজরাতে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।২
আমরা যে রকম ইংলণ্ডে গিয়ে প্রিমরোজ ডেজির সন্ধান করি। এবারে আরেকটি উদাহরণ নিন —
“ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে,
ভাবখানা মনে আছে—বউ আসে চতুর্দোলা চ’ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।”
মোতির মালা আর সোনার চরণচক্র পায়ে পরে নববধূ অন্যান্য প্রদেশেও যায়, যদিও ঠিক চতুর্দোলা চড়ে যায় কিনা জানিনে, কিন্তু ঐ ‘আমকাঁঠালের ছায়ে’ যে অত্যন্ত ঘরোয়া বাড়ির চেনা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে যে শ্যাম স্নিগ্ধতার ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠলো—তার সঙ্গে কনট্রাস্ট, ধনীর চতুর্দোলার ভিতর অষ্ট-অলঙ্কার ভূষিতা গরবিনী বধূ।
আমকাঁঠালের ছায়ায় দীন গ্রাম অর্ধসুপ্ত—এমন সময় গম্ গম্ করে,
—বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে।”
এই যে ভেজা সবুজের কাজল মায়ার সজল আঁখি—আমাদের বাঙলার গ্রাম, সেটি রসরূপে জানা না থাকলে কি চতুর্দোলা আরোহিণীর (ওরকম বধূ বাঙলার বাইরেও অজানা নয়) সম্পূর্ণ রূপ অন্য প্রদেশ দেখতে পাবে?
এবারে শেষ দৃষ্টান্ত দিই গঙ্গা নদীকে ভারতবর্ষের সব দেশই পবিত্র পুণ্যতোয়া বলে মানে। বাঙালী তাকে মা গঙ্গা বলে, উত্তর প্রদেশে বিহারেও গঙ্গামাঈ বলা হয়। কিন্তু বাঙলা কাব্যে আমরা মা গঙ্গাকে যতখানি মা বলে চিনেছি হিন্দী কাব্যে তো সে রকম ধারা পাইনি।
“নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।”
এভাবে মায়ের দিকটা বাঙালী দেখেছে বেশী—পশ্চিমারা দেখেছে তার পুণ্যের দিক। আর গুজরাটী মারাঠীরা—অর্থাৎ যাদের দেশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাননি—তারা তো আমাদের এ দিকটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।
আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বালির পোল পেরবার সময় এক মুসলমান গঙ্গাকে নমস্কার করাতে আরেক মুসলমান বললে, ‘তুই হিদুদের এসব মানিস নাকি?’ সে বললে, ‘দূর! গঙ্গার আবার জাত কি? গঙ্গা হিন্দু নাকি?’ তারপর সে ছোট খাটো বক্তৃতা দিয়ে বোঝালে, গঙ্গাকে আল্লা বা আল্লার অংশ বলে স্বীকার করা তার পক্ষে পাপ।
অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান পুণ্যের দিকটা অস্বীকার করে শুধু মায়ের দিকটা দেখেছে।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথ, ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে আমারা বাঙালীরাও চিনি, কারণ বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে এবং আমরা ভারতীয়ও বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাঙালীত্ব যেন আমরা না ভুলি। বিশ্বকবি রূপে, ভারতীয় কবি রূপে তিনি তাঁদের সামনে সাম্য মৈত্রী প্রচার করেছেন, উপনিষদের বাণী নূতন করে শুনিয়েছেন, মানবাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার যোগ, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, মানুষের চরম আদর্শ কি এসবই প্রচার করেছেন দার্শনিক রূপে, দ্রষ্টা রূপে এবং কিছুটা কবি রূপে। ‘কিছুটা’ ইচ্ছা করেই বললুম, কারণ মাতৃভাষায় যে বস্তু রসস্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে অনুবাদে তার অধিকাংশই লোপ পায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, —ব্যঙ্গের ইঙ্গিতটুকু বাদ দিয়ে—
“সেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী সেথায় তুমি মানী,
সেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা।”
কিন্তু বাঙালীর কাছে তিনি অন্যরূপে ধরা দিয়েছেন;
“সেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ,
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ,
সেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
সেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
সেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপন ভোলা রসের রচনাতে।”
আরেকটি সামান্য উদাহরণ দি। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ছাত্রেরা যে দুটি বৈদিক মন্ত্র যথাক্রমে সকালে ও সন্ধ্যায় উচ্চারণ করে তার সান্ধ্য মন্ত্র :
“যো দেবো অগ্নৌ যো অঙ্গু যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ
য ওষধিযু, যো বনস্পতিযু, তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।
যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবকে বারবার নমস্কার করি।”
এই শাশ্বত দর্শনে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি সেই দেবেরই স্মরণে বলেছেন,
“তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী।”
যে ‘ছলনাজালকে’ রবীন্দ্রনাথ যৌবনে মায়া-মিথ্যা কিংবা পাপবিদ্ধ আবিল দৃষ্টির বিকার বলে মনে করতেন, শেষ মুহূর্তে সেই ‘ছলনাজাল’-কেও তিনি সেই ব্রহ্মের অন্যতম বিকাশ বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন—যে ব্রহ্ম অগ্নিতে, সলিলে সর্বত্র বিরাজমান।
এই দর্শনই একদা রাজপুত্র দারা শীকুহ ও জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারকে মনের শান্তি দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে এইটেই কেন্দ্র এবং ইয়োরোপে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে এই দর্শনেই তিনি বার বার ফিরে এসেছেন।
কিন্তু প্রশ্ন, এই ব্রহ্মকে কি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা যায়, আমাদের ‘পরাণে’ তাঁর ‘চরণে’ কি প্রেমের ফাঁসি বাঁধা যায়?
রবীন্দ্রনাথই বার বার তাই ঋষিকে স্মরণ করে বলেছেন, —
‘যতো বাচ্যে নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’
‘মনের সহিত বাক্য যাঁকে না পেয়ে নিবৃত্ত হয়।’
তাই যদি হয় তবে তাঁর সঙ্গে প্রেমের মিলন হবে কি করে?
এখানে এসে দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ মরমিয়া বাঙালী কবিরূপে বাঙলায় গাইলেন, —
“আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে।
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণ ধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কক্ষ হারায়।
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে৷”
আর তারই সঙ্গে কবি
“শ্রাবণ আকাশে দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে —
স্বপ্নে উড়িছে তার কেশরাশি পূরব পবন দেখে।”
যে দেব অগ্নিতে জলেতে ছিলেন দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের ভূমাদর্শনে, তাঁর স্থলে প্রিয়া প্রক্ষিপ্ত (প্রোজেক্টেড) হয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা। কিংবা কি বলবো, ব্রহ্ম ও প্রিয়া এক হয়ে গিয়েছেন? এবং কবির জলছলছল আঁখিও মেঘে মেঘে বিচরণ করতে করতে তার সঙ্গে এক হয়ে গেল? তাই —
“শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।”
রবীন্দ্রনাথ যখনই উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বিশ্বজনকে শুনিয়েছেন তারা শুনেছে একাগ্র মনে বিস্মিত চিত্তে, কিন্তু সেই দর্শনের মধুরতর বিকাশ যা বাঙলাতে হয়েছে বাঙালী কবি দ্বারা তার রস কি তারা আস্বাদন করতে পেরেছে?
অথচ একথা তো কেউ দেশে বিদেশে অস্বীকার করবে না যে রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম পরিচয় কবিরূপে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একদিন যদি বিশ্ববাসীর প্রয়োজন মিটে যায়, কবিরূপে তাঁর প্রয়োজন বাঙালীর কাছে অফুরন্ত।
আমার বক্তব্য, ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশ তথা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যে যে যেমন যেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথকে বুঝেছে এই একবর্ষ ব্যাপী পর্বে তারা সেই ভাবে তাঁর চিন্ময়মূর্তি গড়বে—তাদের চিন্তা জগতের প্রতিমা লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে—প্রাণপ্রতিষ্ঠা, প্রশস্তি, বন্দনা রচনা করবে তাদের খরবুদ্ধি তীক্ষ্ণ চিন্তাবৃত্তি দ্বারা, হয়তো বা তাঁর কবিত্বেরও উল্লেখ থাকবে যেখানে তিনি বিশ্বকবি।
এঁদের সংখ্যাই বেশী—বাঙলা দেশ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর তুলনায় কতটুকু—এবং এঁদের
“কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি
কেহ-বা রাজার সুহৃদ সহায়
কেহ বা রাজার জ্ঞাতি।”
এবং আমার মনে হয় কবিত্ব যদিও প্রথম স্থান পেয়েছে, সে আসবে সর্বত্রই সর্বশেষে।
বাঙলা দেশে সেটা যেন না হয়।
বিশ্বজন যখন রবীন্দ্রনাথকে তার অকুণ্ঠ সম্মান জানাবে তখন যেন বাঙালী আমরা না ভুলি, বুদ্ধদেব যখন দিগ্বিজয় করে কপিলবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন তখন যশোধরা তাঁকে দয়িত বল্লভ রূপেই পেতে চেয়েছিলেন। আমরা তাঁকে বাঙালী কবি রূপেই চিনব।
দুঃখিনী মাতার পুত্র যখন রাজ সম্মান লাভ করে তখনো মায়ের কাছে সে ছেলে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার ছেলে।
আর বিশ্বজন যদি তাঁকে বিশ্বকবি বলে রাজমুকুট পরিয়ে দেয় তখন যেন স্মরণ রাখি তিনি সার্থক বাঙালী কবি হয়েছিলেন বলেই বিশ্বকবি হতে পেরেছিলেন, তিনি বিশ্বকবি হওয়ার ফলে বাঙালী কবি হননি।
টীকা :
১. হস্তে লীলাকমলমলকে বাল-কুন্দানিবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডু তামাননে শ্ৰীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে-শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্ৰ নীপং বধূনাম্॥
২. গুজরাতে কাশ আছে কি না জানিনে তবে আধুনিক গুজরাতী কাব্যে তার উল্লেখ দেখিনি। ভদ্রলোকের নাম নরসী ভাই প্যাটেল। পরবর্তীকালে ইনি বিশ্বভারতীতে কিছুকাল জর্মন ভাষা ও সাহিত্য পড়ান।
খুব ভালো লাগলো 👍❤️🙏