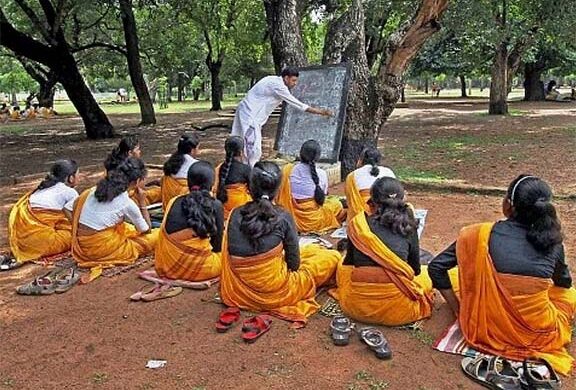
উনিশ.
বেলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। একাত্তরে শান্তিনিকেতনে দেখা হলে বেলা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি সেই সন্জীদা যে আমাকে চিঠি লিখেছিল ঢাকা থেকে? মনে পড়ল, ওপারের ছাত্রী সংঘের সাধারণ সম্পাদক বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। ঢাকাতে ‘ছাত্রী সংসদ’ নামে একটি সংগঠনের সম্পাদক ছিলাম আমি। বেলা লিখেছিলেন, আমাদের সংগঠনকে ওঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। আমি একমত হইনি। ভিন্ন রাষ্ট্রের সংগঠনের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হতে হবে কেন? তখন তো আমরা পাকিস্তানের অধিবাসী। সেই পত্রোত্তরের কোনো জবাব দেয়নি বেলা। বলবেই বা কী! তো সেই চিঠির কথাই সে বলছিল।
শান্তিনিকেতনে সুনীলদা, নৃপেন, শচীনদের সঙ্গে আগে একবার দেখা হয়েছিল। এবারে নৃপেন — বেলারা বাড়িতে ডেকে খাওয়াল। ভাব জমে গেল আরও। নৃপেন শান্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলেও বন্ধুত্ব বজায় ছিল। কলকাতায় ওদের বাসাতেই উঠতাম আমি শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে। বেলাও শান্তিনিকেতনে কোনো কাজে গেলে আমার ঘরেই উঠত। মহাভাব হয়ে গেছিল আমাদের। একবার অনেক দিন শান্তিনিকেতন যাওয়া হয়নি বলে জানতেই পারিনি বেলা কবে মরে গেছে! নৃপেন ঢাকায় এসে এক রাতে আমার বাসায় খেতে এল। ‘বেলা কেমন আছে’ জিজ্ঞেস করতে নৃপেন বলল,
‘ও তো চলে গেছে’!
নৃপেন বেঁচে আছে এখনো। ওপারে গেলে বারকয় দেখা হয়েছে। তবে ইদানীং প্রয়োজন ছাড়া কলকাতায় যাওয়া বা কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা চলে না তো আর!
কুড়ি.
‘ধ্বনি থেকে কবিতা’ লিখবার সময়ে কতজনের কত সহায়তা যে পেয়েছি, কী বলব! দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমান্য অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর) এসেছিলেন রতনকুঠিতে। বিশ্বভারতীর কাজে। উনি একদিন আমার ঘরে চলে এলেন। নিরহংকার সুজন আমাকে বললেন, ‘কী লিখছ, শুনি?’ ‘নিরুদ্দেশ যাত্রার ধ্বনি’ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে তখন। শোনালাম। খুব মন দিয়ে শুনলেন। বললেন, কী ধ্বনি কতবার ব্যবহার হয়েছে তা যদি গ্রাফ এঁকে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তো বক্তব্য অনেকখানি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। কিছু কঠিন নয় গ্রাফ করা। ঢাকার শিল্পীবন্ধু ইমদাদ হোসেনের ছেলেকে দিয়ে গ্রাফ করিয়ে নিলাম। ছাপাবার সময়ের টেকনোপ্রিন্টের অরিজিৎ কুমার নানা সমস্যা দেখাতে থাকলে কলকাতার শমীন্দ্র ভৌমিককে দিয়ে আবার কী সব আঁকাজোকা করানো হয়েছিল। অরিজিৎ কুমার কিছুতেই গ্রাফ ছাপবেন না, কেবলই আপত্তি। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল
তাই।
শান্তা-অসিতের কন্যা এত্তটুকুন ‘সোনাই’ — ও কেমন করে আমার কাজে সাহায্য করেছে, বলি। সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে’ গানটির কথার কাব্যসৌন্দর্য গানে যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখছিলাম। অজানা গানটি স্বরলিপি দেখে তুললাম। সুরটা আয়ত্ত হতে চায় না। গাইতে না পারলে সুরের যথাযোগ্যতা বিচার করব কী করে! দিনভর চেষ্টার পরে রাত ৯টা নাগাদ মোটামুটি গাওয়া যাচ্ছে মনে হলো। অমনি ছুটলাম শান্তার বাড়ির দিকে। ঢুকেই ঘোষণা দিলাম একটা গান গাইব, শুনুন। বসবার ঘরে সোনাইও দাঁড়িয়েছিল তখন। আমার জিজ্ঞাস্য ছিল গানের বাণীর বেদনা সুরে সেভাবে প্রকাশ পেয়েছে কি না। সে কথা বলিনি ওঁদের। গান শেষ হতেই হু হু করে কান্নায় উচ্চকিত হলো সোনাই! অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শান্তাকে আমার প্রশ্নের বিষয়ে বললাম। স্মিতমুখে শান্তা বলল, ‘উত্তর তো পেয়ে গেছেন, তাই না?’
একুশ.
কানাই সামন্ত মশাই বলতেন, বিশ্বভারতীকে বলে তাদের কোনো মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করানো যায় না। শততম বার একই ভুল ছেপে যাবে। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাতেও ভুল সংশোধনের অসম্ভব দেখেছি আমি। রবীন্দ্রভবনের সনবাবুর টেবিলে বসে একটি চিঠি দেখছিলাম আমি। চিঠিটি এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব বইতে চিঠিটি ছাপা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার বিষয়ে চিঠিতে অভিমত জানানো হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম ছাপা হয়েছে ‘এম এ আজান’। ‘আজান’ নাম কখনো শুনিনি বলে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। হঠাৎ খামের গায়ে হাতের লেখায় পত্রপ্রেরকের নামটি চোখে পড়ল। ‘এম এ আজম’। অমনি মনে পড়ে গেল, আমার মায়ের এক কুটুম্বের (ছোট বোনের স্বামী) ওই নাম ছিল। হোমরাচোমরা ধরনের ভদ্রলোককে তেমন ভালো লাগত না আমার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে লেখাপড়া করছি শুনে উনি আমাকে কটকট করে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু বিরূপ কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, বাংলা ভাষায় মুসলমানি শব্দ ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো জবাব দিতে পারেননি। দুইয়ে দুইয়ে চার হিসাব করে নামের রহস্যটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সনৎবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সঙ্গে সঙ্গে। প্রবাসী পত্রিকাতে এই চিঠি ছাপা হয়েছিল। পত্রিকা সংশ্লিষ্টরাই ‘আজম’কে ‘আজান’ বানিয়ে ফেলেছেন বুঝতে পারা গেল। তারপর থেকে ওই ভুল ছাপা হয়ে এসেছে নির্বিচারে।
কানাই সামন্ত মশাই বললেন, ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ নামে শব্দতত্ত্ব বইয়ের নতুন সংস্করণ বার হচ্ছে, এই সময়ে তুমি অন্যতম সম্পাদক শুভেন্দুশেখরকে চিঠি লেখো, ওরা ভুলটা শুধরে নেবে। লিখলাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে গবেষণার কাজ করি বলে উনি আমার নামটি জানতেন।
চিঠির কোনো জবাব এল না।
বহুদিন বাদে পূর্বপল্লীতে সত্যেন রায় মশাইয়ের বাসায় গিয়ে এক বিকেলে শুভেন্দুশেখরবাবুর দেখা পেলাম। ওঁদের কথার মাঝখানে কথা না বলে ধৈর্য ধরে বসে রইলাম। সুযোগ হলে বললাম, ‘আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম…।’ উনি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, কিন্তু তখন বইটা ছাপা হয়ে গেছে বলে আর কিছু করা গেল না।’ ফুরিয়ে গেল।
আরও পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপা হয়। অনেক আশা নিয়ে বই খুলে দেখলাম যথাপূর্বং…, যেমনকার ‘আজান’ তেমনি আছে।
গানের স্বরলিপির ব্যাপারেও কোনো ভুল নিয়ে প্রশ্ন করে কোনো জবাব পাইনি। ভুলের কোনো সুরাহা পাওয়ার আশা সত্যিই বৃথা। [ক্রমশ]