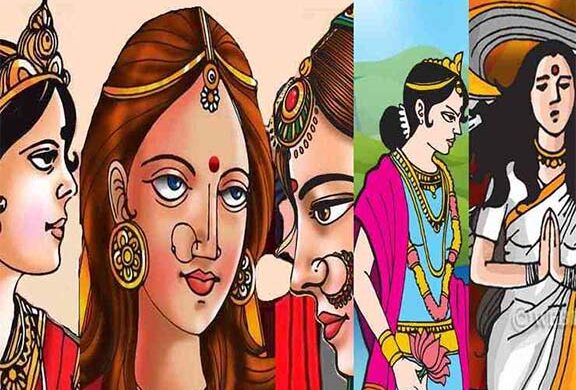
দেবযানী
ইন্দ্রপুরে দেবতাদের পরম পূজনীয় পুরোহিত ছিলেন আচার্য বৃহস্পতি, অন্যদিকে অসুর সাম্রাজ্যে পূজনীয় ছিলেন আচার্য শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য ছিলেন মৃতসঞ্জীবনীর আবিষ্কারক। এই মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র দিয়ে তিনি মৃতদের জীবিত করে তুলতে সমর্থ হতেন। তাই অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধে অসুরেরা হয়ে উঠতে লাগলো অদম্য কিন্তু দেবতারা তখনো সমুদ্রমন্থন করে অমৃত পান করেননি এবং তাঁরা মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্রও জানতেন না। দেবতারা তখন বিকল্প উপায় না দেখে অনেক যুক্তি-পরামর্শ করে বৃহস্পতির পুত্র কচকে অনুরোধ করলেন শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এবং মৃতসঞ্জীবনীর গোপন মন্ত্র শিখে আসার চেষ্টা করতে। এটা না হলে দেবলোক হয়ে যাবে অসুরালয়। কচ দেবতাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং অসুররাজ্যের রাজধানীতে গিয়ে শুক্রাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। সেই সময়ের নিয়ম ছিল, কোনো ব্রাহ্মণগুরু কোনো ব্রাহ্মণশিষ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। তাই শুক্রাচার্য কচকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। কচ শুক্রাচার্যের গৃহে বিদ্যাচর্চা শুরু করলেন। তখনকার নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী গুরুগৃহের নানারকম দৈনন্দিন গৃহকার্যে সাহায্য করে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। ধীরে ধীরে সদালাপী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও রূপবান কচ শুক্রাচার্যের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যে পরিণত হলেন। আস্তে আস্তে দেখা গেল, কচ কেবল তাঁর গুরুর নয়, গুরুর বিদুষী কন্যা দেবযানীর মনও জয় করে নিয়েছেন। কচের সুমধুর সংগীত আর অপূর্ব চিত্রকলার প্রতি দেবযানীর মুগ্ধতা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হলো। কচের ব্যবহারেও প্রতিনিয়ত দেবযানীর প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালোলাগা প্রকাশ পেত। অসুরেরা ইন্দ্রপুরবাসী কচের এখানে আসা মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল, কচকে দেবতারা পাঠিয়েছে মৃতসঞ্জীবনীর গুপ্তবিদ্যা শিখে নেওয়ার জন্য। ফলে অসুরেরা মিলে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল কীভাবে কচকে ধ্বংস করে ফেলা যায়, যাতে তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে দেবকুলে ফিরে যেতে না পারেন। একদিন শুক্রাচার্যের গরুদের মাঠে চরাতে নিয়ে গেলে অসুরেরা কচকে মেরে ফেলে ও তার দেহ টুকরো টুকুরো করে কুকুরকে খাইয়ে দেয়।
ওদিকে গবাদিপশুগুলো একা একা কচকে ছাড়াই ফিরে এলে দেবযানীর মন তার প্রেমাস্পদের অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। তিনি তাঁর বাবাকে তাঁর আশঙ্কার কথা জানালেন। একমাত্র কন্যার দুঃখে বিচলিত শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে জীবিত করে তুললেন। কচ আরেকবার জীবন পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে গুরুসেবা করতে লাগলেন। একদিন দেবযানী কচের কাছে আবদার করলেন এক বিশেষ ধরনের ফুল এনে দিতে তাঁর খোঁপার জন্য, ওই ফুল শুধু এক গভীর অরণ্যেই পাওয়া যায়। ফুল আনতে গেলে অসুরেরা আবার কচকে হত্যা করলো। এবার তারা কচের হাড়-মাংস মন্ড বানিয়ে তা সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু শুক্রাচার্য আবারো কচকে জীবিত করে তুললেন দেবযানীর অনুরোধে। অসুরেরা তৃতীয়বারের মতন কচকে হত্যা করার আগে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কচের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে সেই ছাই সোমরসের সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে খাইয়ে দিলো। সূর্য অস্ত গেলে গবাদিপশুগুলো একা একাই ফিরে এলো, কিন্তু কচের দেখা নেই। শুক্রাচার্যের মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যার প্রয়োগে শুক্রাচার্যের পাকস্থলীতে থাকা ছাই থেকে কচ পুনরায় জীবন লাভ করলেন, কিন্তু সেখান থেকে বের হতে পারছিলেন না। শুক্রাচার্য বুঝতে পারলেন তিনি যদি কচকে জীবিত বের করতে চান তাহলে তাঁকে বরণ করতে হবে মৃত্যু। এ-কথা শুনে দেবযানী আবার কাঁদতে শুরু করলেন, কারণ পিতার জীবনের বিনিময়ে তিনি প্রেমিকের জীবন ফেরত চান না। যে-কোনো একজনের মৃত্যুই তাঁর কাছে নিজের মৃত্যুর সমান।
শুক্রাচার্য এই সমস্যারও সমাধান করলেন। তিনি কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শেখালেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর কচ তাঁকে জীবিত করে তুলতে পারেন। শুক্রাচার্যের পাকস্থলী থেকে বের হয়ে কচ শুক্রাচার্যকে জীবিত করে তুললেন। এরপরও কচ আরো বহু বছর শুক্রাচার্যের গৃহে বিদ্যাচর্চা করলেন। অবশেষ এলো বিদায়ের দিন। গুরুগৃহে শেষদিন কচ শুক্রাচার্যের কাছে এলেন বিদায়ী আশীর্বাদের জন্য। কচের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলে দেবযানী কচকে তাঁর ভালোবাসার কথা জানালেন এবং তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। কিন্তু কচ বললেন, আমি পুনর্জীবিত হয়েছি তোমার বাবার পেট থেকে সুতরাং তিনি আমার মাতৃসমান আর তুমি আমার বোন, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না। কচের এহেন উত্তরে দেবযানী অত্যন্ত বিচলিত ও দুঃখিত হয়ে বললেন, তুমি বৃহস্পতিপুত্র কচ আর আমি শুক্রাচার্যকন্যা, আমরা কোনোভাবেই ভাইবোন নই, আমাদের বিয়েতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কচ প্রস্ত্তত ছিলেন না দেবযানীকে গ্রহণ করতে। কেননা তিনি ইন্দ্রপুর থেকে একটি বিশেষ কর্মসম্পাদনের জন্যে এসেছেন, নিজে বিবাহ করার জন্যে নয়। সে-কর্ম সম্পন্ন হয়েছে, ফলে তাঁর ফেরার পালা এখন। কচের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রোধান্বিত দেযযানী কচকে অভিশাপ দেয় – ‘কচ, আমার নিষ্পাপ ভালোবাসাকে তুমি যেভাবে অপমান করলে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি কখনো এই মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা ব্যবহার করে কাউকে জীবনদান করতে পারবে না।’ এই অভিশাপ শুনে কচও রাগান্বিত হন এবং দেবযানীকে অভিশাপ দেন, ‘তোমার এই আচরণ অন্যায়, দেবযানী, আমিও বলছি – কোনো ব্রাহ্মণ-পুত্র কখনো তোমায় বিয়ে করবে না, আর আমি হয়তো এই বিদ্যা ব্যবহার করে কাউকে জীবিত করতে পারব না; কিন্তু আমি আমার ছাত্রদের এটা শেখাতে পারবো, যারা এটা প্রয়োগ করবে।’ দেবযানীর ভালোবাসা উপেক্ষা করে কচ চলে গিয়েছিলেন ইন্দ্রপুরীতে তাঁর কর্তব্যপালনে।
এরপর বহু বছর কেটে যায়। দেবযানীর একসময়ের খুব ঘনিষ্ঠ সখী অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা হঠাৎ হিংসা করে একদিন দেবযানীকে এক গভীর কূপের ভেতর ফেলে দেয়। এই অন্যায় কাজের জন্য অসুররাজ শর্মিষ্ঠাকে চিরদিনের জন্য দেবযানীর দাসী করে দেন। ওদিকে ভরত বংশের মহারাজা যযাতি একদিন শিকার করতে বেরিয়ে শুক্রের কন্যা দেবযানীকে সেই কূপের নিচ থেকে উদ্ধার করেন। কচ বিদায় নিয়ে স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পর বহুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে অথবা কচের উদার বরে (রবীন্দ্রনাথের লেখনীর জোরে), ‘তুমি সুখী হবে; ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে’ কিংবা মহাভারতমতে কচের অভিশাপে (কখনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে হবে না), ততদিনে দেবযানী সত্যি সত্যি কচের প্রেম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। আর তাই ক্ষত্রিয়রাজ সুপুরুষ সাহসী যোদ্ধা যযাতির প্রেমে পড়ে যেতে সময় লাগে না দেবযানীর। যযাতি প্রথমে রাজি না হলেও পরে সম্মতি দেন। এর কিছুকাল পরে যখন শুক্র দেবযানীর সঙ্গে যযাতির অসবর্ণ বিয়ে দেন, তখন তিনি যযাতিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, দাসী শর্মিষ্ঠাকে যযাতি যেন কখনো বিয়ে না করেন। যযাতি সেই সাবধানবাণী না মেনে গোপনে শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করেন। দেবযানীর গর্ভে যযাতির দুই পুত্র – যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র – দ্রুহু্য, অনু ও পুরু জন্মলাভ করে। শর্মিষ্ঠার গোপন বিবাহের কথা দেবযানী জানতে পারার পর শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হন। পরে যযাতি শাপ প্রত্যাহারের জন্য শুক্রকে অনেক অনুনয় করায় শুক্র বললেন, যযাতি ইচ্ছে করলে কারো সম্মতি নিয়ে নিজের জরা অন্যকে দিয়ে তাকে জরাগ্রস্ত করে তার যৌবন নিজে ভোগ করতে পারবেন। যযাতি স্থির করলেন তাঁর নিজের যে-পুত্র যযাতির জরা নিয়ে যযাতিকে তাঁর যৌবনদান করবেন, তাঁকেই তিনি রাজ্য দেবেন। পাঁচ পুত্রের মধ্যে শুধু কনিষ্ঠ পুত্র যযাতির জরা নিতে রাজি হলেন। পুত্র পুরুর যৌবনভিক্ষা নিয়ে যযাতি সহস্র বছর ধরে নারীসঙ্গ ও বিষয় ভোগ করে রাজত্বশাসন করে শেষ পর্যন্ত পুরুকে রাজত্ব দিয়ে বনবাসে চলে যান।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বিদায় অভিশাপ’ কবিতায় কচ-দেবযানী উপাখ্যানের শেষটুকু বদলে দেন। দেবযানীর অভিশাপটি অক্ষত রেখে তিনি কচকে মহৎ বানিয়ে তাঁর মুখ থেকে দেবযানীকে অভিশাপ দেওয়ার পরিবর্তে আশীর্বাদ দেওয়ালেন। ‘আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে; ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে…’। রবীন্দ্রনাথ কর্ম ও দায়িত্বকে ভালোবাসার ওপর স্থান দেন এবং কচকে দেবযানীর থেকে মহৎ করার প্রচেষ্টা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৯ সালে শর্মিষ্ঠা নামে পাশ্চাত্য শৈলীতে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক, যার ভেতর বহু তৎসম শব্দসহ দীর্ঘ অনেক সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতার সঙ্গে প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের সংযোজন করে আধুনিকমনস্ক মধুসূদন দত্ত দেবযানী, যযাতি ও শর্মিষ্ঠার ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি এবং তার সংশ্লিষ্ট জটিলতা বিশ্লেষণ করেছেন এই নাটকে। মহাভারতে বর্ণিত কাহিনির ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এই নাটকের চরিত্র ও ঘটনাবলিতে রয়েছে মহাকবির কল্পনাশক্তির ও কাব্যক্ষমতার স্বাক্ষর। সাম্প্রতিককালে অর্পিতা ঘোষ-রচিত এবং দেবযানী নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে কলকাতায়, যার ভেতর দেবযানীর পছন্দের পাত্রের কাছে দু-দুবার করে তাঁর প্রেম নিবেদন করা ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঘটনা রয়েছে, রয়েছে দেবযানীর অসবর্ণ বিয়ের সংবাদ। সবচেয়ে বড় কথা, এই নাটক দেখায়, দেবযানীর মতো মানুষরা নিজের অজান্তেই যুগ-যুগ ধরে অন্যদের দ্বারা কীভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছেন।