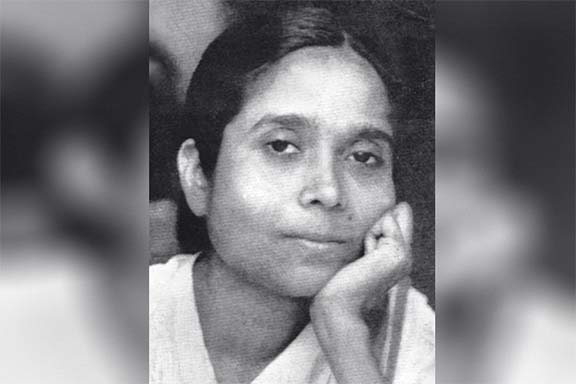
ব্রিটিশ বিরোধিতা ও জমিদারী বিরোধিতার পাশাপাশি সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস নারীর বিদ্রোহী চেতনারও প্রতিরূপ। নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে উপস্থাপনে সাবিত্রী রায় দৃঢ়চেতা। নিজের জীবনে যেমন নারীত্ব তাঁর কোন বাধা হয়ে দাড়ায় নি তেমনি তাঁর নারী চরিত্রকে তিনি সততা ও ন্যায়ের পথে — আদর্শ ও দেশপ্রেমের পথে নিতে কোন প্রতিবন্ধকতা রাখেন না। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই এ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। স্বরলিপি ও পাকা ধানের গান-এ তা হয়েছে বিস্ময়করভাবেই স্বচ্ছ। ত্রিসোতা-র পদ্মার বিদ্রোহী চেতনা অনেক বেশি সংহতরূপে প্রকাশ পায় স্বরলিপি-র সাগরী ও শীতার ভেতর দিয়ে। এরা দুজনেই সাধারণ ঘরের মেয়ে, কিন্তু দুজনেই আবার অসাধারণ তাদের ভাবনা ও আদর্শবোধে। পার্টির নির্দেশকে মাথা পেতে নিতে সাগরী তার স্বামী রথীকে ত্যাগ করলেও তার ভালবাসাকে কলুষিত করে নি। যখনই বুঝেছে পার্টিনেতৃত্ব তার ব্যক্তিজীবনকে ক্ষতি করতেই উপায় খুঁজছে সে প্রতিবাদ করেছে, কলঙ্কের কালি কপালে মেখে চলে গেছে কৃষক এলাকায় আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে। আর এভাবেই একসময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটে সাগরীর। শীতাও কি কম! ভালবাসলেও তার বিয়ে হয় নি পৃথ্বীর সাথে। বিয়ে হয়েছিল যে দেবজ্যোতির সাথে তার মৃত্যুতে বিধবা শীতার একমাত্র আশ্রয় হয় শিশুসন্তান মিঠু। কিন্তু পরে বোঝা যায় সেও এক ছাইচাপা আগুন। তাই শাশুড়ির মৃত্যুকালে সে শ্বশুরের ভিটাতে গিয়েও সেখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে পলাতক কমরেডদের। তারই আশ্রিয় ছিল নিখিলেশ পার্বতীর স্বামী যে কিনা হাজং বিদ্রোহের সময় পুলিশের গুলিতে আহত হয়। শুধু কি তাই! নিজেও তো চেষ্টার ক্রুটি করে নি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এড়াতে। পাকা ধানের গান-এর দেবকীর মত একটি বিদ্রোহী চরিত্র সমকালীন বাংলা উপন্যাসে হয়তো দুর্লভ। হয়তো পারিপার্শ্বিকতার চাপে দেবকী নুইয়ে পড়তে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিদ্রোহীসত্তা অপরাজেয়। দেবকী তো অত্যাচারী স্বামীর পদবী পর্যন্ত নিজের নামের সাথে লাগাতে নারাজ। মেঘীর ভেতরেও কি ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত প্রথাবিরোধী একজন নারীর শক্তিশালী অস্তিত্বকে আমরা অনুভব করি না? এমনকি ঈশানী দেবী এবং লতাও তো সমাজ পরিবর্তনে কম অগ্রণী নয়! স্বকালের বিদ্রোহী নারীসমাজের কর্মকাণ্ডে সাবিত্রী রায়ের ছিল অচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা। আর সেজন্যেই তো স্বরলিপি-র উৎসর্গে ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯ এর যে পাঁচজন শহীদের নাম উৎকীর্ণ তাঁদের মধ্যে চারজনই নারী। ৩৬
পাকা ধানের গান সন্দেহাতীতভাবেই একটি সফল রাজনৈতিক উপন্যাস। জীবন-ঘনিষ্টতায় সফল সামাজিক চিত্রণ এ উপন্যাসের মূল প্রতিবাদ্য। এবং সাবিত্রী রায়ের সাফল্য অথবা কৌশল এই যে তিনি উপন্যসটিকে সম্পূর্ণতই একটি রাজনীতির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না রেখে এবং ঘটনাক্রমের মূল ভিত হিসেবে রেখেছেন বাঙালির দৈনন্দিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবন। পাকা ধানের গান-এর আরও একটি বিশিষ্টতা এই যে, লৌকিক জীবনাচরণ সারা উপন্যাসটি জুড়ে বর্তমান যা উপন্যাসটির মূল গল্প-কাহিনীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে উপন্যাসটিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সেকালের বাঙালি জীবনের লৌকিক বিবিধ অনুষঙ্গ উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পুঁথির গল্প আর গান নিয়ে লাউল ৩৭ সাজানোর গল্প, হলুদ বাটার গান ৩৮, নীল সাজা ৩৯, আহলাদী পুতুল বানানো ৪০, গাজীর পট দেখানো ৪১, কালী নাচ ৪২, মনসার পাচালী পাঠ ৪৩, মাঘমঙ্গলের ব্রত ৪৪ তোষলা ব্রত ৪৫ এমনই কিছু উদাহরণ। লোককাহিনী লোকপুরাণের কতকত গল্পও এসে মিশে আছে পাকা ধানের গান-এর মূল গল্পের ভেতর। এবং নির্দ্বিধচিত্তে বলা চলে যে পাকা ধানের গান লৌকিক সংস্কৃতির যে কোন গবেষকের জন্য একটি মূল্যবান দলিল হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা চলে যে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গেও সাবিত্রীর উপন্যাসের এক অবিচেছদ্য অনুষঙ্গ। স্বরলিপি ও পাকা ধানের গান উভয় গ্রন্থেই বহু বহু রবীন্দ্র গান ও কবিতার উদ্ধৃতি লেখকের মনন ও পাঠগত চিত্রকে পরিস্ফুটিত করে।
সাবিত্রী রায়ের পরবর্তী দীর্ঘ উপন্যাস মেঘনা-পদ্মা ৪৬-এর দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে। সাত শতাধিক পৃষ্ঠায় এ উপন্যাসটির শেষাংশ সমুদ্রের টেউ আলাদাভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮-তে। সাবিত্রী রায়ের শেষ দুটি উপন্যাস হল ঘাসফুল (১৯৭১) ও বদ্বীপ (১৯৭২)। ঘাসফুল উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল সময়কে ঘিরে। উত্তাল রাজনীতির সেসব যুবকের বাংলাদেশের এক মফস্বল শহর যশোরেও কর্মব্যস্ত। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অধ্যাপক সুগত সাথে যোগাযোগ ঘটেছে ব্রিটিশ প্লেনচালক পিটারের। সাম্যবাদের বিশ্বনন্দিত মতবাদের পিটারও সুগতদের সাথে একই কাতারে উপস্থিত। পারিবারিক নৈকট্যে পিটার চলে আসে সুগতর পরিবারে নেমে তমস এক স্তদ্ধতা।
বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শুরু থেকে পঞ্চাশ দশকের প্রথম বছরগুলো পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল অতিক্রম করেছে কঠিন এক সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় হাঁসফাস বাঙালি জীবন যার সাথে যুক্ত রয়েছে ধুরন্ধর রাজনীতি। সর্বশেষে মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ এবং উদ্ধাস্ত সমস্যায় কন্টকিত এমন একটি কঠিন সময় হয়তো বাঙালি আর কোনদিনই অতিক্রম করে নি। এবং উল্লেখ্য যে এসবের ভেতরের দেশের প্রগতিশীল সিংহাভাগ মানুষ সেকালে যুক্ত হয়েছিল তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আন্দোলনে। এ আন্দোলন স্বদেশী পার হয়ে সাম্যবাদরে পথে তেভাগ্য ও হাজং বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই সমকালের এই উত্তুঙ্গতা সামগ্রিকরূপে বাংলা কথাসিহিত্যে প্রয়োজনানুযায়ী উপস্থাপিত হয় নি। সে সময়ের সাথে সমকালীন লেখকদের সম্পৃক্ততা কম থাকায় বা পরবর্তীকালে সে সময়কে ইতিহাস পাঠের ভেতর দিয়ে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের উপন্যাস বঞ্চিত হয়েছে। সামান্য যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছিল তার মধ্যে সাবিত্রী রায়ের অন্ততপক্ষে পাকা ধানের গান উপন্যাসটির নাম অন্যতম হিসেবে গণ্য হতে পারে। অথচ রাজনীতির নিমর্ম দৃষ্টির বাইরে। বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় লৌকিক সমাজকে রাজনীতির বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে সাবিত্রী রায় তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। নারী হয়েও ঘরে বন্দী থাকেন নি। তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল। সন্দেহ নেই সাবিত্রী রায়ের সাহিত্য নতুন মূল্যায়নের দাবী রাখে।
অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
১. শতবর্ষের কৃতী বঙ্গনারী, শামলী গুপ্ত (সম্পা), কলকাতা, ২০০১।
২. প্রগতির পথিকেরা, ১৯৩৬-১৯৫০, দেবাশীষ সেনগুপ্ত (সম্পা.), কলকাতা, (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)।
৩. বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, ১৯৪৫-১৯৯৮, বীরেন্দ্র দত্ত, কলকাতা, ১৯৯৮।
৪. পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস (১৯৪৬-১৯৭১), শাহীদা আখতার, ঢাকা, ১৯৯২।
৫. বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা, ২০০০।
টীকা:
সত্য ত্রেতা ছাপরেতে
ছিল না মা পাশ।
মা-মা-মাগো।
নন্দীরে কয় যাও কৈলাসে
নীল হবে না বিনা পাশে রেখো মা তোর চরণ তলে
তোমার অনন্ত নীলে।
উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া
ইয়লের পঞ্চাশটি শয়রে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য কোনখান দিয়া
উঠিবেন সূর্য গোয়ালবাড়ির ঘাট দিয়া।
কোদাল কাটা ধান পাব
গোয়াল আলো গরু পাব
দরকার আলো বেটা পাব
সঙা আলো জামাই পাব
সেজ আলো ঝি পাব
আড়িমাথা সিঁদূর পাব
ঘর করব নগরে
মরবো গিয়ে সাগরে
তোমার কাছে মাগি বর
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর
সুব্রত কুমার দাস, কামারখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ বর্তমানে থাকেন টরন্টো, কানাডা