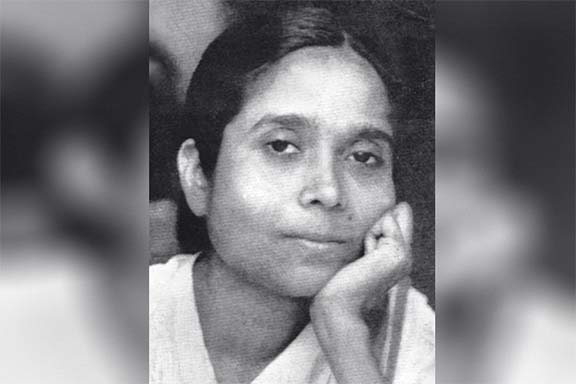
পাকা ধানের গান-এর জন্য সাবিত্রী রায় যে প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেন তার বিশালতা যেকোন উপন্যাস পাঠককেই বিস্মিত করবে। দিঘির পাড়, তালপুকুর, মনসাডাঙ্গা, শ্যামগঞ্জ নদীবিধৌত বাংলার এসকল গ্রামের পটে সাবিত্রী রায় হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শুদ্র, জেলে-কৃষক সকল ধর্ম শ্রেণী ও পেশার একটি সমাজকে উপস্থাপন করেছেন যার বাসিন্দা উপন্যাসের কলাকুশলীরাও। তাদের কেউই অনন্য নয়, তারাও যেন উপন্যাসে অনুল্লেখিত অন্য মানুষদের মত সাধারণ। উপন্যাসের কাহিনী আবার ঐ সকল গ্রামের কোন বিশেষ পরিবারে গণ্ডিবদ্ধ নয়, বিস্তৃত হয়েছে অনেকগুলো পরিবারে, সম্পৃক্ত হয়েছে অনেক মানুষ। আর তাই পার্থকে দিয়ে উপন্যাস শুরুর পর ক্রমে ক্রমে সেখানে সমবেত হয়েছে দীনবন্ধু মাস্টার, দেবকী, সুবালা, সুখদা, কেতকী, কুন্তী, সাথী, মফির মা, আমিনুদ্দিন, আমিন জগাই বাঁড়ুজ্যে, আলি, পার্থর বাবা সুদাম, লক্ষ্মণ, অমূল্য, কুণ্ড মাঝি, আল্লাবক্স, মঙ্গলা, অর্জুন, লক্ষ্মী, দাসুর মা, মেঘীসহ আরও অনেকে। নিকটবর্তী ঐ সকল গ্রামপুঞ্জ থেকে কাহিনী ছড়িয়েছে কাঞ্চনপুরে ; যেখানে দেবকী স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে পাওয়া যায় ঈশানী দেবী, সুন্দর ঠাকরুণ ও লতার মত চরিত্র। আবার দেবকীর শ্বশুরবাড়ি একই গ্রামে যখন হলো তখন আরও অনেকগুলো চরিত্র এসে যুক্ত হলো এদের সাথে। দেবকীর মামী শাশুড়ি, ননদত্রয় পুসি-টুসি-হাসি, বিধবা জা আন্না, স্বামী রাজেন। আর বিপ্লবী সুলক্ষণ সরকারও ঐ বাড়িরই ছেলে।
প্রথম পর্বের মাঝামাঝি জায়গায় ২৯ আমরা পেলাম নতুন আরও একটি স্থান পাহাড়পুর – দক্ষিণবঙ্গের আগের গ্রামগুলো থেকে অনেক দূরে। কারাবাসের দিনশেষে পার্থর অন্তরীণ হয়েছে ঐ এলাকায়। দক্ষিণের সে গ্রামগুলো পার্থকে দিয়েছিল চেতনা যা চূড়ান্ত বিপ্লব কার্যে উত্তরের ঐ পাহাড়পুর এলাকায় স্মরিত। পাহাড়পুরের নতুন মানুষদের মধ্যে সারথী, সরস্বতী, শঙ্খমান, বাসুমনি, আলাপী, কার্ত্তিক চৌকিদার। পনের ষোল পৃষ্ঠার এই অংশ শেষে আমরা দেখি পার্থর অন্তরীণ কাল শেষ। এই অংশটি পাকা ধানের গান উপন্যাসের মূল উপপাদ্য হাজং বিদ্রোহী প্রেক্ষাপট নির্মাণে প্রধান নিয়ামক। এই অংশে হাজংদেরকে যে সপ্রতিভ চরিত্রে দেখানো হয়েছে তা দ্বিতীয় বার যখন আমরা পাহাড়পুরে উপস্থিত হই ৩০ তখন বিদ্রোহী চেতনায় পরিবর্তিত। সেখানে বিপ্লবী গণেশ দাসের সশরীর উপস্থিতি। কিছুদিন পর সেখানে সুলক্ষণ ও তার স্ত্রী লতা উপস্থিত। আর এখানে পাহাড়পুরের হাজং বিদ্রোহের লেখ্যরূপ দেওয়ার জন্য সাবিত্রী রায় স্বাবলম্বী একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করে ফেলেন।
ইতোমধ্যে প্রথম পর্বে দুই-তৃতীয়াংশ শেষে ৩১ পার্থর অবস্থান হয় কলকাতায়। সেখানে ভদ্রার সাথে পার্থর পরিচয়; যে কিনা আর একটি প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে উপন্যাসে পরিস্ফুটিত। ভদ্রাসূত্রে আর যারা উপস্থিত হয় — তারা হলো আনন্দবাবু, নিউ লাইট পত্রিকার ফটোসাংবাদিক অবাঙালি কুনাল কুরূপ প্রমুখ। আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ভদ্রার সূত্রে আরও পাওয়া যায় সত্যদর্শন, টিয়া ও টিপুর মত ছোট ছোট চরিত্রগুলো। মৃত স্বামীর বাড়িতে (শহরটি যশোর বলে অনুমান ৩২) অবস্থানকালে তার সাথে যোগাযোগ ঘটে আইরিশ সৈনিক অ্যানড্রু ওদোনেল বা ও-নীলের। আর এভাবেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাই শুধু পার হয় নি, হয়েছে ভারতবর্ষের সীমানাও। পরিচয় পত্রিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন —
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়তে পড়তেই আশঙ্কাই জাগে, ভয় হয় এতগুলি বিচ্ছিন্ন বিভিন্নমুখী চরিত্রের সামঞ্জস্য কি সম্ভব হবে? সুলক্ষণ ও লতার কাহিনী, সারথি ও সরস্বতীর প্রেম, দেবীর সংক্ষুব্ধ জীবনেতিহাস, আলি ও মেঘীর কাহিনী, ফোটোগ্রাফার কুনালের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, চোরাকারবারী দুলাল দত্তের সংসার, আনন্দবাবু ও ভদ্রার জীবনবৃত্ত — এদের সকলকে একটি সমগ্রতার মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ ঐক্য পরিণতি কি দিতে পারবেন লেখিকা? কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশ থেকেই বোঝা যায় এতগুলি চরিত্র ও ঘটনার ভিন্নমুখী গতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি তাঁর আছে; তৃতীয় খণ্ডে এসে অতি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ধারাগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একটি ধারায় মিলে গেছে।
অন্যদিকে কলকাতায় দেবকীর অবস্থান নেয়ার সূত্রে গড়ে উঠেছে আরও একটি চরিত্র জগত। হেনামামী, দুলালমামা, সুখনলালের মত অর্থগৃধ্নু চরিত্রগুলোকে আমরা এখানেই পেয়েছি। সর্বরকম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবকী যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তখন তার উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ অন্নপিসি — দেবকীরই মত আর এক অসহায় কিন্তু সংগ্রামী নারী। দেবকী পরে যখন যক্ষা হাসপাতালে চাকরি নেয় তখন আরও যারা ভীড় করে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে রয়েশে আশাদি, মিহিরবাবু, রাখিদি, অসীম। আর এভাবেই কয়েকশত চরিত্র উপন্যাসের কালের ভেতরে দিয়ে গ্রন্থের ঘটনাসমুহকে কোন-না-কোন-ভাবে স্পর্শ করেছে। এ সকল চরিত্রের মধ্যে পার্থ, দেবকী, ভদ্রা প্রধান ঘটনাসমূহের নিয়ন্ত্রক হলেও সুলক্ষণ, আলি, মেঘী, সারথি, সরস্বতী, কুনার প্রভৃতি চরিত্রও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সেজন্যেই বোধহয় একজন সমালোচক পাকা ধানের গান উপন্যাসের আলোচনায় বলেছেন —
‘নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার কোন আকর্ষণই সাবিত্রী রায়ের নেই। কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ বীরত্বের শক্তি এবং সম্ভাবনার প্রকাশ এ গ্রামটি ও এর বিপ্লবী সরল অধিবাসীরা’। ৩৩
পাকা ধানের গান হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এক অনুপম চিত্র। উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন যেমন এ উপন্যাসে মিলেমিশে আছে তেমনি চেতানগতভাবেও তাদের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। লক্ষ্মণ যে আমিনুদ্দির বাড়িতে যায় গাজির গান শুনতে অথবা গরুগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় মঙ্গলার যে বিশ্বাস পীরের পূজো দিলে গরুর মঙ্গল হবে, তীব্র ঝড়ের দিনে আমিনুদ্দির বাড়িতে যখন হরি ও আল্লাহ উভয়ের নামই ধ্বনিত হয় তখন ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত ও চেতনাগত নৈকট্য উপলব্ধি করা যায়। আর সচেতনভাবে সাবিত্রী রায় যে কাজটি করেছেন তা হলো আলির সাথে ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ে মেঘীর প্রেম ও বিয়ে। আলি ও মেঘীর এই বৈপ্লবিক কাজটি কিন্তু উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সামাজিক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই। মেঘীর জন্মকালেই বাপ মারা যায়। বিয়ের পরপরই স্বামীকেও হারায়। এমন অভাগী মেয়ের জায়গা কোথায়! পৈতে বিক্রি করেই চলে মা-বেটির সংসার। সেখানে আলির উপস্থিতি মেঘীর ভেতরে জায়গায় স্বপ্ন দেখার সাহস। ‘ঐ মুসলমান ছেলেই একমাত্র ব্যথার ব্যথী তার।’ ৩৪ কিন্তু সে স্বপ্ন কি পূরণ হবার জন্য জেগেছে? জগাই বাড়ুজ্জ্যে, যে কিনা মেঘীর শরীর চেয়ে পায় নি, থাকে ওৎ পেতে। তারপর ওদের ভালবাসাবাসি ফাঁস হয়ে গেলে মাথা মুড়িয়ে মেঘীর গালে পোড়া ছ্যাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু পার্থর দৃঢ়তার কারণেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় সবকিছু। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ের জন্য ওদেরকে ট্রেনে তুলে দেয় পার্থরা। আর এভাবেই আলি-মেঘীর নতুন এক জীবন শুরু হয়; যা হিন্দু-মুসলমান সমাজের জন্য এক নতুন ইঙ্গিতের সূচনা বৈকি। আলি-মেঘী চলে গেলে পার্থর বাবা সুদাম এবং মা মঙ্গলার নিচের ভাবনা দিয়ে এ অধ্যায় আপাতত শেষ হয় —
সুদামও নিশ্চয় হ’য়ে বসে থাকে ঘরে। কাজটা একবার সায় দেয়, একবার দেয় না মনে, বামুনের মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে — ঘর সংসার চলবে কি ভাবে কে জানে? নামাজ পড়বে, কলমা পড়বে মেঘী? আবার ভাবে, নামাজকি আলিই পড়তো কোনোদিন? এরা সব আলাদা জাত। আলাদা যুগের আলাদা মানুষ। পার্থ, আলি, লক্ষ্মণ — এরা কলিকালের চেলে সব, এছাড়া এ বিয়ে না দিলেও মেয়েটার দুর্দশার অন্ত থাকবে না।
মঙ্গলা মেঘীদের রওয়ানা করে দিয়ে এসে বলে ‘গালের উপর টিকে আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে মেয়েটার। এরা কি মানুষ নয়?’ ৩৫
জমিদারী অত্যাচারের এক জীবন্ত দলিলের মতো পাকা ধানের গান। সে অত্যাচার কখনও একজন ব্যক্তির ওপর আবার কখনো একটি সামাজিক দলগোষ্ঠীর ওপর নেমেচে। সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের উঠে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা এতে রয়েছে। আর সেজন্যেই তো এতদ্অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সামাজিক আন্দোলন তেভাগা-হাজং বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। মফির মা’র জমি যেমন করে নাকি দু’হাজার টাকা কর্জ নিয়েছিল সে অজুহাতে জমিদারের আমিন জগাই বাড়ুজ্যে দখল করে, আমার পথকর না দিলে চলাচল নিষেধ তেমনি একটি শমন আসতেও খুব বেশি দেরী হয় না। জমিদারের ছত্রছায়ায় থাকা এসব অত্যাচারী মানুষগুলোই নীচুতার চূড়ান্ত প্রমাণ করে। এদের বিরুদ্ধে আলির অবস্থান বলে তার ওপর নির্যাতন বেশি। তাদের এমন অত্যাচার তো পাহাড়পুর এলাকায় তীব্রতর। পার্থরা যাদের সংগঠিত করছে তাদের বেশিরভাগই হদি। ক্ষত্রিয়জ মর্যাদার দাবিদার এই হদিরা হলো রাজা হৈহয়ের বংশধর। তাদের হাতের পদ্মফুল না হলে মায়ের পূজো হয় না, অথচ তাদেরকে পূজায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। এভাবে ধর্মীয় অত্যাচার যেমন আছে, আছে সামাজিক অত্যাচার। কিন্তু প্রকৃতিগত বিদ্রোহী চেতনার অধিকারী মানুষ মেনে নেয় নি এসব। আন্দোলন হয়েছে। হদিরা প্রতিমা কাঁধে নিতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনই হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাবুরা রাজি হয়েছে পূজাকে সর্বজনীন করতে। এই বিদ্রোহী চেতনারই অঙ্গ হিসেবে এক সময় আসে টংক আন্দোলন। জমির ধান কৃষকেরা জমিদারের গোলায় তুলতে রাজি হয় না; যার পরিণতিতে হাতি আর লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে হাজংদের ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয়া হয়েছে। শঙ্খমানকে ধরে নিয়ে জমিদারের পাইকরা দিনরাত শারীরিকভাবে অত্যাচার করেছে। কিন্তু মাথানত করে নি হাজংরা। ব্যাপকভাবে সংগঠিত হাজংদের ওপর শেষ পর্যন্ত ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে যার চূড়ান্ত ঘটেছে মেশিনগানের গুলিতে পার্থর মৃত্যুতে। [ক্রমশ]
সুব্রত কুমার দাস, কামারখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ বর্তমানে থাকেন টরন্টো, কানাডা