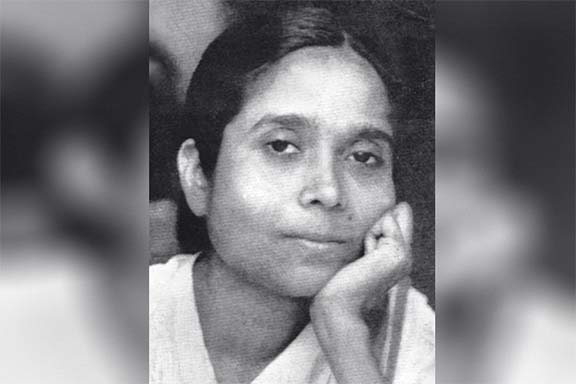
স্বরলিপি বা সাবিত্রী রায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মতই পাকা ধানের গানও বাংলার উভয় অংশকেই এর ক্ষেত্র করেছে। স্বরলিপিতে এসেছিল কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক পরিক্রমা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, উদ্ধান্ত সমস্যা ইত্যাদি। অন্যদিকে পাকা ধানের গান বাংলা অঞ্চলের সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের মর্মস্পর্শী চিত্র। কৃষকদের সে-আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর সম্পৃক্ততাসহ পুরো চিত্রটি সাবিত্রী রায় বিধৃত করেছেন যা শেষ হয়েছে ১৯৪৬-৪৭-এর হাজং বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। এ উপন্যাসে তিনি আবার স্বরলিপির মত সংক্ষিপ্ত একটি সময়ের রূপায়ণ না করে ধারণ করেছেন একটি দীর্ঘ কালকে যা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ যুগের শেষ কাল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তেভাগা আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত: যার প্রথম দিককার কিছু কিছু অনুষঙ্গ ত্রিসোতাতে পাওয়া যেতে পারে। যদিও অবশ্য উল্লেখ্য যে লেখিকা সেসবের নির্মিতিতে সুস্পষ্ট ভিন্নতা দিয়েছেন। পৌনঃপুনিকতা তাঁর রচনাগুলোকে দুষ্ট করতে পারে নি।
ত্রিশ-চল্লিশের দশকের বাংলাভাষী অঞ্চলে যে বিপুল প্রস্ফূরণ তা নিয়ে উপন্যাস রচনার কি শেষ থাকতে পারে! স্বদেশী যুগের অগ্নিগর্ভ সময় অতিক্রান্ত হয়ে বীর্যবান সেসকল তরুণরা তখন নতুন বিশ্ববীক্ষার দিকে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা – যার কাঁপনে বঙ্গবাসীও উদ্বেগাকুল। তারই মধ্যে এলো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন। বছর না পেরুতেই সাম্রাবাদী সরকারের সাথে মজুতদার ও জোতদারের যোগসাজশে ছারখার হয়ে গেল বাংলার সাধারণ বিত্তের জীবনযাপন। পঞ্চাশের (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) যে মন্বন্তরে সরকারি হিসেবেই মারা গিয়েছিল ১৫ লাখের বেশি মানুষ, বেসরকারি হিসেবে যে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ লাখ ২১ — তারই মধ্যে শুরু হলো তেভাগা আন্দোলন — কৃষকের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার আমৃত্যু প্রচষ্টা। বাংলা অঞ্চলের অধিকাংশ জেলার মানুষ সাড়া দিল সে আহবানে। একই কাতারে দাঁড়িয়ে সাহস যোগালো শিক্ষিত প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী। বাঙালি জীবনের ঘটনাবহুল সে-সময়ের সামগ্রিক চিত্র বাংলাভাষায় রচিত উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য না হলেও তার সংখ্যাকে কি প্রতুল বলা চলে? বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনকে একমাত্র উপাত্ত করে রচিত উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) জাগরী ছাড়া কোন ভাল উদাহরণ কি আমাদের আছে? পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়েও তো মাত্র গোটাকয়েক: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) অশনিসংকেত (১৯৪৪), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) মন্বন্তর (১৯৪৪) এবং গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) ত্রয়ী উপন্যাস পঞ্চাশের পথ (১৯৪৪), ঊনপঞ্চাশী (১৯৪৬) এবং তেরশ পঞ্চাশ ২২ (১৯৪৫)। এছাড়া সরোজকুমার রায় চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২) কালোঘোড়া (১৯৫৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) চিন্তামণি (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের (১৯০৮-১৯৮০) তিলাঞ্জলি (১৯৪৪), আবু ইসহাকের (জন্ম. ১৯২৬) সূর্য দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), অমলেন্দু চক্রবর্তীর (জন্ম. ১৯৩৪) আকালের সন্ধানে ২৩ (১৯৮২) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রাসঙ্গিক হিসেবে প্রবিষ্ট হয়েছিল এমন অন্য কয়েকটি উপন্যাস হলো সুমথনাথ ঘোষের (১৯১০-১৯৮৪) সর্বংসহা (১৯৪৪) ভবানী ভট্টাচার্যের ২৪ (১৯০৬-?) ইংরেজি উপন্যাস So Many Hungers (১৯৪৮) এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৯-১৯৯০) একমাত্র উপন্যাস মাটি ও মানুষ (১৩৬৮), আলাউদ্দিন আল আজাদের (জন্ম, ১৯৩২) ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪) প্রভৃতির নাম করা যায়। বাঙালির দুর্ভাগ্য এই যে মন্বন্তর নিয়ে কিছু উপন্যাস রচিত হলেও তেজোদীপ্ত বাঙালির দুর্মর সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলন নিয়ে বিশেষ কোন উপন্যাস রচিত হয় নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামায় তেভাগার প্রসঙ্গ অনেকখানি আসলেও দুর্ভিক্ষের দূরতম ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। যদিও দাঙ্গা প্রসঙ্গ খোয়াবনামায় এসেছে পরিপূর্ণ বিস্তৃতিতে। ব্যাপক দাঙ্গার পরিচয় যেসব উপন্যাসে রয়েছে তার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), নারায়ণ চৌধুরীর (১৯১৮-১৯৭০) লালমাটি (১৯৫১) অন্যতম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গটি অন্যান্য যেসকল উপন্যাসের ঘটনাস্রোতে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) উত্তরণ (১৯৭০), আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৯) পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) জননী (১৯৫৮), শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) সংশপ্তক (১৯৬৫), অসীম রায়ের (১৯২৭-১৯৮৬) একালের কথা (১৯৫৩) প্রভৃতি। হয়তো কৃষণ চন্দরের গাদ্দার, খুশবন্ত সিং-এর ট্রেন টু পাকিস্তান বা অতি সম্প্রতি রচিত শশি ঠারুরের রায়ট-এর মত সম্পূর্ণতই দাঙ্গা বিষয়ক কালজয়ী উপন্যাস বাংলাভাষার হয়ত দূর্লভ। দাঙ্গা নিয়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও যতটুকু ঘটেছিল তেমনটি তেভাগার উপন্যাস না থাকা নিয়ে প্রার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন: ‘দুঃখের বিষয় তেভাগা আন্দোলনকে নিয়ে এই ধরণের উপন্যাস প্রচেষ্টা আমাদের প্রধান ঔপন্যাসিকেরা কেউ করেন নি।’ ২৫ খোয়াবনামার চল্লিশ বছর আগে পাকা ধানের গান-এ তেভাগার বিপুল উপস্থিতি আমাদের স্মরণে আসে না যেহেতু এর লেখিকা হারিয়ে গেছেন বিস্তৃতির অতলে।
পাকা ধানের গান-এর পর্ব তিনটি আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। অখণ্ড সংস্করণটি প্রকাশ পায় ১৯৮৬ তে যার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে ১৯৯০-এ। অখণ্ড সংস্করণে কোন পর্ব-উল্লেখ নেই। অখণ্ড সংস্করণকে সংক্ষেপিত বলা হয়েছে। ২৬ পাকা ধানের গান হিন্দী, মালায়ালাম ও চেক ভাষার অনূদিত হয় এবং সমাদর লাভ করে। এস. উপাধ্যায় হিন্দী ভাষায়, দুর্বান জবাভিতেল চেক ভাষার এবং এম. এন. সত্যার্থী মালায়ালাম ভাষায় গ্র্রন্থটি অনুবাদ করেন। অখণ্ড সংস্করণে সাড়ে ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি বাঙলাভাষা অঞ্চলের সর্ব-অগ্রণী রাজনৈতিক উপন্যাস। নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আর শ্রেণী-সচেতন রাজনৈতিক কথাসাহিত্যিক হিসেবে সাবিত্রী রায় সর্বাগ্রে উল্লেখ্য এবং সফল এক কথাশিল্পী; যার উত্তরসূরী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীকে (জন্ম ১৯২৬) চিহ্নিত করা চলে। বাংলা কথাসাহিত্যে একই রূপ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন আর যে একজন নারী কথাকার তিনি হলে সুলেখা সান্যাল।
পাকা ধানের গান উপন্যাসে ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের বাংলাদেশের যে উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক সময়কে চিত্রায়িত করা তার প্রধান চরিত্রটি হল পার্থ। একুশ বছর বয়সী পার্থকে পাওয়া যায় উপন্যাসের প্রথম লাইন থেকেই। এরপর পার্থর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। এক পর্যায়ে হাজং এলাকা। চূড়ান্ত বিদ্রোহের এক সময় পত্রিকা অফিসে টেলিপ্রিন্টার শিটে নিউজ: ‘হাজং অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন তোরজোর চলছে। খুব লড়াই করছে চাষীরা। … মেশিনগান দিয়ে গুলি চালাচ্ছে হাজংদের ওপর। সতের জন আহত হয়েছে। … একজন কৃষক নেতা পার্থ দাস গুলিতে নিহত। ২৭ হাজংদের এই যে রণসাজ তার চূড়ান্ত বর্ণনা সাবিত্রী যেভাবে দেন —
ঘরের বাইরের সে কফিন স্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ বনের ভেতর থেকে শিঙা বেজে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে চলে সে সাংকেতিক শিঙার বেতার বার্তা।
সমস্ত রক্তকণিকা দিয়ে শোনে পার্থ অরণ্য-প্রান্তের সে শিঙার প্রতিধ্বনি। সিগ্ধ একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে অধর প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আরও খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে ক্ষত দিয়ে।
সন্ধ্যা হতে না হতেই হাজার হাজার হাজং সারি বেঁধে টিলার ঢালু বেয়ে নিচে নেমে আসে। নেমে আসে হাজার হাজার ডালু, কোচ, গারো বানাই – প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক, লাঠি-সড়কি, বর্শা। দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর মতো অন্ধকারে শালবনের ভেতরে দিয়ে ছুটে আসে মশালের পর মশাল। মাদলের গুরু গুরু আওয়াজ আর মশালের গণনাতীত সংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে যায় মিলিটারী সশস্ত্র বাহিনী। সৈন্যের ঘাঁটি তুলে নিয়ে যাবার হুকুম আসে ওপরওয়ালার। ২৮
সংগঠিত হাজংদের বিদ্রোহী কার্যক্রমের এই যে বর্ণনা তা থেকে ধারণা করা যায় সমকালীন রাজনীতির কর্মকাণ্ড নিয়ে সাবিত্রী রায়ের ধারণা কত প্রত্যক্ষ। বিপ্লবী দলের ছেলে হিসেবে পার্থর প্রথম উপস্থিতি থেকে সংগ্রামী নেতা হিসেবে পার্থর ক্রমঅগ্রসরণ। জেল খাটার পর পার্থরা ক্রমশ ঝুঁকছে সমাজতন্ত্রের দিকে। ব্রিটিশ-বিরোধিতার সাথে তখন যুক্ত হয়েছে অত্যাচারী ধনিক জমিদার-বিরোধিতাও। তবে ব্রিটিশ-বিরোধী বা জমিদার-বিরোধী যাই হোক না কেন এ দলভুক্ত মানুষদের ওপর সরকারি নির্যাতন কোনদিনই কমে নি। [ক্রমশ]
সুব্রত কুমার দাস, কামারখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ বর্তমানে থাকেন টরন্টো, কানাডা