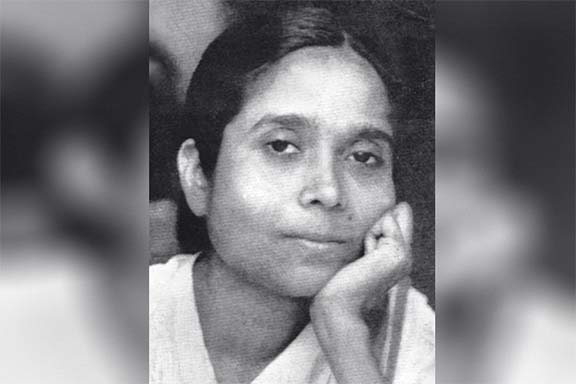
স্বরলিপির এসব চরিত্ররা কিন্তু শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা নয়। তাদের বিরাট অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরও নাগরিক। পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বাংলার এ অঞ্চলও উপন্যাসটিতে যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গতায় উপস্থাপিত। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও উভয় বাংলাই প্রাসঙ্গিক হয়েছে। হাজং বিদ্রোহের সংবাদ তো এ উপন্যাসে রীতিমত উদ্দীপক তথ্য। হাজং বিদ্রোহের অনেক দূরে অবস্থান করেও উপন্যাসের চরিত্রদের সাবিত্রী রায় এ ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেন সহজেই। শীতার বাসায় মিঠুর ছোটমাদের ফেলে যাওয়া কাগজেই তো আমরা প্রথম পড়ি —
গুলি চলেছে চাষী কন্যার বুকে। দুধের শিশু ঢলে পড়েছে হাজং বধূর কোলে। বুকের দুধটুকু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো, জন্মের মত শেষ হল তার স্তন্য খাওয়া। স্তন্যপায়ী শিশুর বুকে গুলি ছুড়তে দ্বিধা করে নি সাম্রাজ্যবাদের অনুচরেরা। ১২
মিঠুর ছোট মা-ই তো পার্বর্তী এবং মনিকাকা হল কমরেড নিখিলেশ। দুজনেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মী। এই পার্বতীই তো ইতিহাসখ্যাত কর্মী ইলা মিত্র; যার বিবরণ আমরা পাই —
সারাদিন ঘুরছে পৃথ্বী মামুদপুর মামলার আসামীদের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে। দশ হাজার টাকা তুলে দিতে হবে তিন দিনের মধ্যে। পাকিস্তান থেকে আত্মগোপন করে পালিয়ে এসেছে নিখিলেশ এ টাকা সংগ্রহ করতে। একটা ডিফেন্স কমিটিও গঠন করতে হবে।
পার্বতীসহ সতের জন কৃষকের বিরুদ্ধে মামুদপুর থানার দারোগা হত্যার মামলা চলছে। …
সমস্ত কাজের ভিতরে পৃথ্বীর মাথায় ঘুরছে পার্বতীর জবানবন্দী। আজই পত্রিকায় বেরিয়েছে তার উপর অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ। গলিত অগ্নিস্রোতের মত প্রতিহিংসার লাভাস্রোত ধাবিত হচ্ছে পৃথ্বীর অস্তিত্বের শিরা উপশিরায়।
শীতের রাতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে লোহার পেরেক ঢুকিয়েছে সর্বাঙ্গে।…
জীবনে ভুলতে পারবে না মানুষ সর্পদংশনের মত এ লাইনগুলি — Then they pushed hot eggs one after into my …’ ১৩
আর এভাবেই সাবিত্রী রায় রূপ দিয়ে চলেন স্বকালের বাংলার সামগ্রিক এক রূপকে। এরই প্রসঙ্গে গ্রন্থে এসে উপস্থিত হয় আরও দুটি প্রসঙ্গ — উদ্ধান্তু সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। সমকালের প্রেক্ষাপটেই নয় শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। সন্দেহ নেই উদ্ধান্ত বিষয়ে সাবিত্রী রায়ের উপস্থাপনা অপূর্ণ। স্বরলিপিতে বিবৃত হয়েছে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় উদ্ধান্ত হিন্দু গৃহহীনদের কথা, পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ববাংলায় আগত মুসলমান উদ্ধান্তদের কথা আসেনি। এ প্রসঙ্গে আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামার কথা স্মরণ করতে পারি। সে উপন্যাসের পশ্চিমবাংলা বা ভারত থেকে আগত মুসলমান উদ্ধাস্তুদের কথা এসেছে। সাবিত্রী রায় যেহেতু উভয় বাংলাকেই তাঁর প্রেক্ষাপট করেছেন, তাই উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ধাস্তু প্রসঙ্গটি তাঁর উপন্যাসে প্রত্যাশিত ছিল যেমনটি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ক্ষেত্রে তিনি করেছেন। পশ্চিমবাংলায় যাওয়া সেসকল উদ্ধাস্তুদের নিয়ে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহলের যে কূটচক্র তা-ও এ উপন্যাসে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত।
ঘটনার ক্রমঅগ্রসরণে এক পর্যায়ে উপস্থিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপন্যাসের সময়কাল ১৯৪৬ এর পর হওয়ার সে দাঙ্গার চিত্র স্বরলিপিতে লিখিত হয় নি, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ত্যাগের উত্তরকাল তো এ উপন্যাসের গল্প অতিক্রম করছে। আর তাই অতর্কিত এক সংবাদ ‘পাকিস্তানে আবার গোলমাল শুরু হয়েছে’। ১৪ ছেচল্লিশের যে দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হয়ে আস্তে আস্তে সারা বাংলায় ছড়ালো — এ দাঙ্গা শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সে গোলমাল প্রথমে দেখানো হয়েছে হয়েছে কলকাতা থেকে। হাজার হাজার মানুষ দাঙ্গায় আত্মীয় পরিজন, ধনসম্পদ হারিয়ে পশ্চিমবাংলায় যেতে তাদের যে অভিব্যক্তি, মানুষজন যে চিঠিপত্রাদি লিখছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে, পত্রিকায় যে সকল সংবাদ ছাপা হচ্ছে – এসবের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে দাঙ্গার পূর্ণ চিত্র। উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শীতা তখন পূর্ব পাকিস্তানে। এবং সাবিত্রী রায় দেখাতে ভোলেন নি যে শীতাকে যারা রক্ষা করেছে তারা মুসলমান; যেমনভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার কারণে যখন পশ্চিমবাংলায় ‘রক্তের বদলে রক্ত চাই, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই’ ১৫ শ্লোগান ও পোস্টারে যখন কলকাতার পথঘাট উচ্চকিত তখন মানবিক বোধসম্পন্ন কিছু মানুষই একত্রিত করে সুস্থ বোধসম্পন্ন সকলকে এবং অসৎ সকল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের বিরুদ্ধে। পৃথ্বীরা সবাই কলাকাতার দাঙ্গা রোধে সামনের কাতারে। কিন্তু তারপরও রক্ষা হয় না। মধু মুখার্জীর ইন্ধনে কালু গুণ্ডা ও তার লোকজন হাঁশিয়াকে তুলে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণের পর বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলে যায়।
ঔপন্যাসিক সাবিত্রী রায়ের জীবনে এটি একটি পরিহাস যে স্বরলিপির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লেখক ও রাজনৈতিক পৃথ্বী পার্টির সমালোচনামূলক বক্তব্যের জন্য যেমন বহিষ্কৃত হয় স্বরলিপি প্রকাশের পর সাবিত্রী রায়ের ভাগ্যেও বহিষ্কারপ্রাপ্তি ঘটে। বহিষ্কৃত হয়ে পৃথ্বীর যেমন মনে হয়েছিল ‘কি নিয়ে চলতে পারে সে জীবনে। সাহিত্য? কিন্তু কি লিখবে সে?’ ১৬ সেই মনে হওয়া দৃঢ়তর হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর। নিজেকে সম্বোধন করে পৃথ্বীর বক্তব্য ‘লেখক তোমার কলম তুলে ধর। কলমে, তুলিতে আর গানে — নতুন সুর বাঁধা স্বরলিপিতে রচনা করো কল্যানী মানুষের মুক্তির আহ্বান। জানাও দিকে দিকে অনন্ত শান্তির ডাক।’ ১৭ সাবিত্রী রায়ের লেখিকা সত্তাও পৃথ্বীর মত — সাহিত্য রচনার ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া। আর তারই ফলশ্রুতি পরবর্তী দুটি বিশাল উপন্যাস পাকা ধানের গান এবং মেঘনা পদ্মা।
কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ এসকল দ্বন্দ্বের প্রকাশই কি সাবিত্রী রায়কে বিস্মৃত হবার প্রধান কারণ? পূর্বসূরি এবং সমকালীন অধিকাংশ অন্য লেখিকারা যখন ঘরোয়া বিষয়-আশয় নিয়ে লিখতে ব্যস্ত তখন সাবিত্রী ঝুঁকেছেন রাজনীতিকে তার উপন্যাসের বিষয় করতে। স্বীয় লব্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁর পুজি। মনন এবং বিশ্লেষণ তার অনুষঙ্গ। যেখানে উত্তাল এই সময়ের বিপুল টানাপোড়েন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাচিত্র একজন পুরুষ ঔপন্যাসিকও রচনায় সাহস করেননি, সেখানে সাবিত্রী রায়ের রচনা রীতিমত প্রথাবিরোধী। সুজিৎ ঘোষ বলেছেন ‘প্রকৃতপক্ষে প্রথম উপন্যাসটি থেকেই লেখিকা এক প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের গুণাগুণ আলোচিত হয়নি, বরং আলোচনা ও প্রচারের অভাবজনিত এক নৈঃশব্দের বাতাবরণ ক্রমশই তাঁর রচনাগুলির ওপর পরিব্যপ্ত হয়েছে।’ ১৮ প্রতিষ্ঠানবিরোধী এ অবস্থানের সাথে যুক্ত হয়েছিল উপন্যাসে বিধৃত পার্টির কিছু কাজ সম্পর্কে কোনো কোনো কর্মীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, যা তাঁকে পার্টির পরিমণ্ডল থেকে দূরে ঠেলে দেয়। স্বরলিপি নিষিদ্ধ ঘোষণাকালীন এক প্রবীণ পাঠকের স্মৃতিসমৃদ্ধ আলোচনা রয়েছে যা রীতিমত উদ্দীপক। সাবিত্রী রায়ের স্বামী শান্তিময় রায়ের ছাত্র সৌরীন ভট্টাচার্য এ আলোচনায় জানিয়েছেন —
ইতিমধ্যে বাহান্ন সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। … তা ‘স্বরলিপি’ পড়া শেষ হতে না হতেই আর এক দুঃসংবাদ। ঠিক যে কোনো সংবাদ পাওয়া গেল তা নয়, কীরকম যেন এক ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। বাড়ির বড়রাও যে বেশি কিছু বলতেন তা নয়। সুন্দর দেখতে ঐ স্বরলিপি বইটা আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল … শোনা গেল বা জানা গেল বা বোঝা গেল, যাই হোক, বইটি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই রকমই ভাসা ভাসা জানা গেল বইটি পার্টি বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়েছে, তাই এ-বইয়ের প্রচার নিষিদ্ধ।
… ওই সময়ে পার্টির ভেতরের কথায় খানিকটা আলগোছে প্রচার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, লিখিত কোনো সার্কুলার কিংবা ফতোয়া পার্টি সদস্যদের জানা ছিল কিনা তা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। সম্ভবত ছিল। অন্তরালের চাপাচাপি কতটা ছিল, সে ব্যাপারে নিজের অবস্থান কী ছিল, তাঁর সম্ভাব্য আপত্তি কত তীব্র ছিল এসব কথা আজ হলফ করে বলা শক্ত। ১৯
আর এভাবেই সাবিত্রী রায় চলে গেলেন বিস্মৃতির গভীর তলে। অথচ পঞ্চাশ বছর আগে সাবিত্রী রায়ের ভাবনা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপারে সত্য বলে স্বীকৃত। পার্টির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কর্মীমহলে সকল প্রকার আলোচনাকে নিষিদ্ধ রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সেজন্যই তিনি যেমন স্বরলিপির স্বরকে সমুন্নত রাখতে পার্টির সদস্যপদ ছাড়তে পিছপা হন নি, তেমন পরবর্তীকালেও নিরত হন নি তাঁর জীবনদর্শনকে প্রকাশ করতে। সাহিত্যিক সত্যই ছিল তাঁর একমাত্র আদর্শ। সাহিত্যিক সে-চেতনায় যুক্ত ছিল সাম্যবাদ আকাঙ্ক্ষা। পার্টির আদর্শকে তিনি সে আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে স্থান দেন নি। আর সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের মানবিক বোধ পাঠকের কাছে সমাদৃত। দলীয় সংকীর্ণতার উপরে উঠে তাঁর চরিত্রগুলো মানবিক স্পর্শ পেয়েছিল বলেই সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস এখন নতুন করে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। স্বরলিপির এক আলোচনায় সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন —
সাবিত্রী রায়ের রচনায় একটি গভীর মানবিক আদর্শবাদের ফল্গুধারা প্রবাহিত। এ শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, সমাজ মানসে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনচারী মানুষের, স্বাধীনতাচারিনী মানবীর যে চলাফেরা তিনি চিত্রিত করেছেন অত্যন্ত সহজে, কোন ঢাক ঢোল না বাজিয়ে, কোন দীর্ঘ যুদ্ধং দেহি গোছের বক্তৃতার প্রবর্তন না করেই, সেটাতে সত্যিকার বিস্ময় জাগায়। এটা বিশেষ করে লক্ষণীয় তাঁর নারীচরিত্রে। এরা কেউ প্রেমে সফল, কেউ বা ব্যর্থ, কিন্তু প্রত্যেকেরই হৃদয়বত্তার দুটি সমাজ প্রকাশ, একটি তার আদর্শের ক্ষেত্রে, অন্যটি তার মানবিক সম্পর্কগুলির পরিবেশে। ২০
সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসের মানবিক বোধের অনুসন্ধানে সাফল্যের কারণেই তাঁর পরবর্তী মহাকাব্যিক উপন্যাস পাকা ধানের গান ১৯৮৬ সালে অখণ্ড সংস্করণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশ পেয়েছিল? [ক্রমশ]
সুব্রত কুমার দাস, কামারখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ বর্তমানে থাকেন টরন্টো, কানাডা