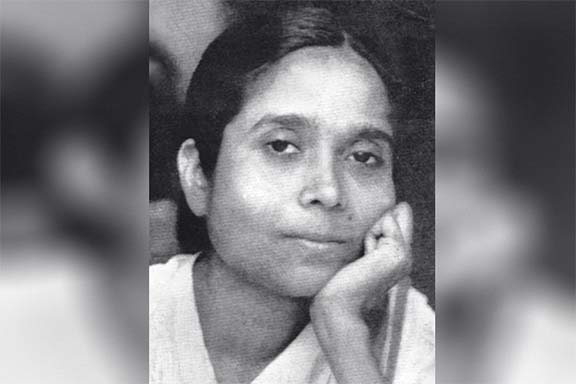
স্বরলিপির ‘লেখিকার কথা’য় সাবিত্রী রায় যে বলেছিলেন ‘এ উপন্যাসেরও আমার পূর্ববতী উপন্যাস দুইটির মতই, কোন চরিত্র মিথ্যা নয় – বাস্তবেরই ছায়া, আবার কোনও চরিত্রই সত্য নয় – কল্পনারই প্রতিছায়া মাত্র’ যাকে ঔপন্যাসিকের সাহিত্যাদর্শ হিসাবে ধরে নেয় চলে সহজেই। তাঁর উপন্যাস সকলের কাহিনী বুনন করেন তা তো অন্য যে কোন লেখকের মতই স্বতঃসিদ্ধ। স্বরলিপির কালসীমা ১৯৪৬-১৯৫১। অর্থাৎ বলা চলে ত্রিসোতার প্রায় শেষ দিকে এসে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরবতী তিন/চার বছর কাল পর্যন্ত এ উপন্যাস বিস্তৃত। প্রায় একই সময়কাল নিয়ে সাম্প্রতিককালেও আরও যে একটি কালজয়ী উপন্যাস আমরা পেয়েছি তা হলো খোয়াবনামা (১৯৯৬)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) রচিত সে উপন্যাসও বাংলা অঞ্চলের সে সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত – যেমন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদিকে যেমন আত্তীকরণ করেছে, সাবিত্রী রায়ও তা করেছেন তাঁর স্বরলিপিতে। ইলিয়াস পঞ্চাশ বছর পর, আর সাবিত্রী পঞ্চাশ বছর আগে। সাবিত্রী যে কাজটি করেছেন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকে, ইলিয়াসকে তা করতে হয়েছে ইতিহাসের পঠনের ভেতর দিয়ে। আর সে কারণেই হয়তো ইলিয়াসের অনেক বিবরণ ইঙ্গিতবাহী, স্বপ্নমিশ্রিত, যেটি সাবিত্রীর ক্ষেত্রে সাদামাটা বিবরণেই ব্যক্ত। তবে ইলিয়াস ও সাবিত্রীর রচনাদ্বয়ের একটি চূড়ান্ত পার্থক্য এভাবে হয়তো চিহ্নিত করা চলে যে সাবিত্রীর সামগ্রিক প্রকাশ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাস্নাত, যেমনটি ইলিয়াসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ঘটে নি।
স্বরলিপির প্রকাশক লিখেছিলেন —
রাজনীতিকে প্রধান উপজীব্য করেও অনাবিল জীবনালেখ্য রচনা যে সম্ভব তারই জ্বলন্ত প্রমাণ পূর্বগামী সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সৃজন ও ত্রিসোতা। বিপ্লবী বাস্তবতায় পরিপ্লুত ‘স্বরলিপি’ হল মুক্তিকামী, শান্তিপিপাসু ভারতীয় আত্মায় সংগ্রামী সাধনার অনুলেখ। জীবনকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম নয় — তাই বৃহত্তর সংগ্রামের সাথে দেখি মিলিয়ে গেছে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংঘাত, দোলাচল চিত্ততা, প্রেম ও প্রয়োজনের শত সহস্র খুঁটিনাটি। ‘ত্রিস্রোতা’ ছিল বাংলা সাহিত্যেও এক অকর্ষিত পথের প্রথম পদ্রক্ষপ। ‘স্বরলিপি’ হল সেই পথের বলিষ্ঠ অভিযান। ৬
স্বরলিপি শুরুই হয়েছে এক সমাবেশ দিয়ে। যেখানে মুহুর্মুহু স্লোগান ‘তেলেঙ্গনার পথ আমাদের পথ’। আর সামান্য পরেই সেখানে উপস্থিত দর্শকের মানসিক অভিব্যক্তি: ‘প্রতিহিংসাই। শুধু সাম্রারাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে নয়, এতদিনের ভুল পথ ধরা আপোসী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধেও’ ৭ এবং শেষ বক্তার কথা ‘এতকাল আমরা যা বলেছি, তা সবই ভুল। আজ থেকে যা বলছি, তাই একমাত্র ঠিক’ ৮ থেকে বোঝা যায় সম্পূর্ণতই রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সাবিত্রী রায়ের অন্বিষ্ট। সাধারণভাবে রাজনৈতিক না বলে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল অর্থাৎ তৎকালীন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজন এবং কর্মকাণ্ডকে ঘিরে স্বরলিপির আবর্তন। পার্টির কঠোর অনুশাসনের সেই চুড়ান্ত আদর্শকে লালন করে, সার্বক্ষণিক কম্যুনিস্ট পার্টিকর্মী সাবিত্রী রায়, সার্বক্ষণিক পার্টিকর্মী শান্তিময় রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী রায় তাঁর দেখা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। পার্টির ভেতরের লোকজনের ভাবনায় পার্টির কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও বিপুল। আর সেকারণে পার্টির পক্ষ থেকে সাবিত্রী রায়কে মুখোমুখি করা হয় এক অগ্নিপরীক্ষার। এ প্রসঙ্গে সুজিৎ ঘোষের ভাষ্য হল —
কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির বিচ্যুতিগুলোকে তাত্ত্বিকরূপে না রেখে জীবন্ত প্রতীকে চিত্রিত করায়, প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের মতো পার্টির কর্ণদারদেরও তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন। ‘স্বরলিপি’ প্রকাশের পরে, পার্টির তরফে থেকে এই বই প্রত্যাহার প্রত্যক্ষ নির্দেশ তার প্রতি আসে। তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হন নি। ফলে বইটি পার্টি থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তার অনমনীয়তায় পার্টির সদস্যপদ শেষ পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেন। ‘সৃজন’র ‘বিশ্বজিৎ’ এর মতোই আদর্শে আত্মনিবেদিত অথচ উদাসী লেখিকার স্বামীও পার্টি এবং লেখিকার মধ্যে এই সংঘাতে থেকেছেন উদাসীন, কিছুটা ইচ্ছাকৃত নিরপেক্ষ। হয়তো লেখিকার মনে সেকারণে ছিল অভিমান, কিন্তু পরবর্তীকালে তার যেন একলব্যের সাধনা – পাটির স্বীকৃতি বা সভ্য পদ প্রভৃতির প্রতি না তাকিয়েই তিনি একটা নিজের লক্ষ্যভেদের সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। লিখে গেছেন পরবর্তী উপন্যাসগুলি একের পর এক। সে উপন্যাসগুলিতেও তিনি শ্রমজীবি-শোষিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে, শোষণের বিপক্ষে এক শোষণ-নিপীড়নহীন মুনষত্ব্যের, সাম্যসমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। ৯
কিন্তু স্বরলিপির বিশেষত্ব এই যে এ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র রাজনৈতিক মানুষ হলেও সর্বোপরি তারা মানবিক বোধে সিঞ্চিত। উপন্যাসের পৃথ্বী, রথী, শীতা, সুমিত্রা, মেনকা, সাগরী, ফল্গু, কুরী, আক্রাম খাঁ এরা সবাই জীবন্ত। অর্থাৎ সাবিত্রী রায় তাদের সর্বোপরি মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। রাজনীতি বা আদর্শের পুতুল হিসেবে নয়। এমনকি প্রয়োজনহীন বিবেচনা করে লেখিকা উপন্যাসের অনেক স্থানেই একটি রেখাতেই একটি চরিত্রকে মূল ঘটনাক্রমে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। নমিতার স্কুলের বোর্ডিঙে সিপ্রা ও চন্দনার অনুপ্রবেশ ১০ এমনই এক উদাহরণ।
উপন্যাসের মূল বিষয় রাজনীতি হওয়ার কারণে এমন কুড়ি কুড়ি চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে খুব সহজেই। শিবশম্ভুবাবু, মহিমদা, স্বরাজ, সুন্দরপ্রকাশ, কুমারী, উর্মি, শুক্লা, মায়া, ছায়া, দেবজ্যোতি, মেনকা, বিনু, সুদর্শন, শীতাংশু, অরুণাংশু প্রমুখ চরিত্রের আবির্ভাব উপন্যাস শুরুর প্রথম থেকেই। উপন্যাসের শেষে গিয়ে বোঝা যায় চরিত্রের একটি দীর্ঘ তালিকা নিয়ে সাবিত্রী তাঁর গল্প বুনেছিলেন। এবং এদের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই, অথবা তাদের সকলেই প্রকৃতপক্ষে একটি সামগ্রিক ও বৃহত্তর পরিম-ল নির্মাণে অংশগ্রহণকারী – কোন একটি বা একাধিক বিশেষ চরিত্রকে বিশেষভাবে রূপায়নে সাবিত্রী রায় মোটেই আগ্রহী নন।
স্বরলিপির মূল পরিক্রমা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী তিন/চার বছরের সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক এবং বিশেষভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনীতি। স্পষ্ট কোন সময়কাল দিয়ে উপন্যাস শুরু না হলেও উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আচরণ ও বক্তব্য দিয়ে বোঝা যায় সাবিত্রী সেকালটাকেই ধরতে চান যখন বাংলার মুক্তিকামী দামাল ছেলেরা এমনকি পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী। পার্টি নেতৃত্বে তখন ধরে ঘুণ। উত্তাল সে সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লব অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতাই ছিল পার্টি নেতৃত্বের আমলা মানসিকতা ও দুর্নীতি পরায়ণতা। এবং ইতিহাস সচেতন সকলেই জানেন পার্টির অভ্যন্তরের ঐ কলুষের কারণেই পার্টির জন্য ভাল ফল বয়ে আনে নি। এবং বিশেষ মনোযোগের যে, সাবিত্রী রায় একজন নারীকর্মী হয়েও পার্টির ভেতরের এ ব্যর্থতাকে চিনতে এবং তার সাহিত্যিক রূপায়ণে ভুল করেননি।
উপন্যাসের প্রধান যারা পার্টিকর্মী তাদের মধ্যে পৃথ্বী অন্যতম। সাথে আছে রথী, সাগরী, শীতাংশু, অরুণাংশু, ফল্গু। এদের প্রত্যেকেই পার্টি-অন্ত-প্রাণ। আবার এরা সকলেই পার্টির নেতৃত্বের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড ও আচরণ সম্পর্কেও সচেতন। পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরও ১১ এরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ কাজে আরও যেন বেশি করে নিমগ্ন। সহ্য করছে অমানুষিক পুলিশি যন্ত্রনা। অথচ নেতৃত্বে যারা সেই নন্দলাল বা তার বিশ্বস্ত সাগরেদ ব্যোমকেশ বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত — শুধু তাই নয়, তাদের সে বিলাস পার্টির টাকায় — যে টাকা পার্টি ফান্ডে আসে কৃষক-মজুরদের এক টাকা/দু টাকা চান্দা থেকে। নন্দলালের মত একটি চরিত্রকে উপন্যাসে সমকালেই উপস্থাপন করা সাবিত্রী রায়ের জন্য ছিল এক দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ। পার্টিকর্মী রথীর স্ত্রী সাগরীকে নিজে বিয়ে করার জন্য নন্দলাল যেসব ফাঁদ পেতেছে, অথবা আরেক পার্টি কর্মী চিত্রকর অরুণাংশুকে দিয়ে পিয়নের কাজ করিয়ে নন্দলাল যে আচরণ করেছে তার চিত্রণ এ উপন্যাসে প্রীতিকর। এমনকি পার্টির ফান্ডের টাকা নিয়ে ব্যোমকেশের ক্রিয়াকলাপও যথেষ্ট মনোযোগ দাবী করে। অথচ যারাই এসব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে তারাই হয়েছে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। কুমার শংকরের মত একজন সৎ কর্মীকেও পার্টি অন্যায় দোষারোপ করতে দ্বিধা করে নি। যেমনটি ঘটেছে পৃথ্বীর ক্ষেত্রেও। শুধু কি বহিষ্কৃত! সাহিত্যিক পৃথ্বী হয়েছে একঘরে। অন্যসকল কর্মীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে পৃথ্বীর সাথে কোনরকম যোগাযোগ না রাখার জন্য। আর সে পরিক্রমাতেই বহিষ্কৃত হয়েছে রথী। আর নন্দলালের কূটচালে রথীর স্ত্রী পার্টিকর্মী সাগরীকে বলা হয়েছে রথীকে ত্যাগ করতে। ব্যক্তিগত সকল মানবিক বোধকে অস্বীকার করে পার্টি কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া অন্যায়গুলো নিরলস, সৎ, একনিষ্ঠ বহু পার্টিকর্মীকে একসময় হতাশ ও ব্যর্থ মনোবল করেছিল এমনটি বুঝতে বাকি থাকে না। আর তাই সাগরী, অরুণাংশু উভয়েই চলে যায় কৃষক এলাকায়। ফল্গুর উপরও এসেছে অন্যায় ফরমান। অথচ পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনকালে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় এর ব্যাপকতা রোধে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ে পার্টির এই বহিষ্কৃত কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি আন্তরিক। [ক্রমশ]
সুব্রত কুমার দাস, কামারখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ বর্তমানে থাকেন টরন্টো, কানাডা