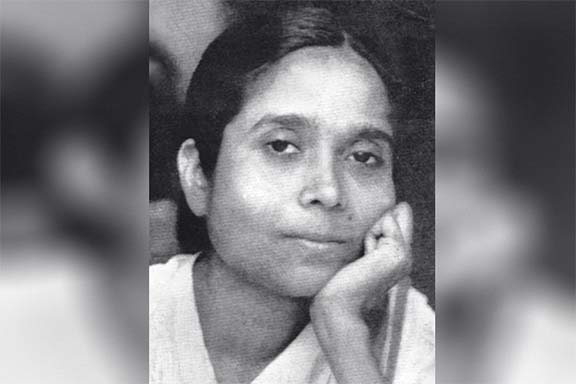
ঔপন্যাসিক সময়কালীন যে রাজনৈতিক বাস্তবতা তাঁকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে সৃজনসহ তাঁর অন্যান্য সকল উপন্যাসেই চিত্রিত করেছেন। অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ অশনি পত্রিকায় সৃজন নিয়ে যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন তার অংশবিশেষ এমন : —
গোড়াতে একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাস্তব জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লেখিকা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। … লেখিকার প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রবল। … সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে মনে হয় একটি সত্য কাহিনীকে যেন লেখিকা উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন। … কেউ কেউ করবেন যে প্রায় সব চরিত্রগুলি মধ্যবিত্তের চরিত্র মাত্র। এমনকি মজুরেরাও তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি নিয়ে চলাফেরা করছে। … মোটের উপর প্রথম রচিত হিসাবে আধুনিক ও আধুনিক লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে লেখিকাও আসন দাবী করতে পারেন।
সৃজন-এর দুর্বলতাকে ভোলানাথ ঘোষ যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি অসহিষ্ণু সমালোচকের সম্ভাব্য সমালোচনায় উত্তরও তিনি আগে থেকেই প্রস্তুত করেছেন। অভ্যুদয় পত্রিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও উৎসাহসূচক মন্তব্য করে বলেছিলেন ‘ভাষার এই স্বাভাবিকতায় লেখিকার বৈশিষ্ট্য, হয়তো মনে হবে বাংলা উপন্যাসে নৈর্ব্যক্তিকতার সার্থক সূচনা এই বইয়েতে পাওয়া যায়’। সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসকে ক্রম অনুযায়ী পাঠ করলে বোঝা যায় চেনা সমাজ ও চেনা মানুষের ছবি সৃজন ও দ্বিতীয় উপন্যাস ত্রিসোতাকে যে সহজতায় তিনি এঁকেছেন স্বরলিপি হয়ে পাকা ধানের গান পর্যন্ত তার রূপ অপরিবর্তিত থাকেনি। ক্রমান্বয়ে তিনি শিল্পসচেতন হয়ে উঠেছেন, এবং তাঁর লেখিকা সত্তায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী চেতনা দার্ঢ্য লাভ করেছে। ত্রিসোতা প্রকাশ পায় ১৯৫০ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণটি এসেছে ১৯৫৪-তে। দ্বিতীয় সংস্করণে ‘প্রকাশকের কথা’ অংশটি ১৯৬১-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ থেকে বাদ দেয়া হয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে সাবিত্রী রায়ের কৃতিত্ব ত্রিসোতা পর্যন্ত প্রশ্নাতীত না হলেও প্রগতি সাহিত্যের একজন কলাকার হিসাবে তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টা যে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা ‘প্রকাশকের কথা’ অংশে স্পষ্ট। এতে আছে —
নির্জিত শ্রেণীবিভক্তসমাজে প্রগতিসাহিত্যের ভূমিকা হল প্রতিবাদের। তাকে হতে হবে বিপ্লবের হাতিয়ার। তার দৃষ্টিভঙ্গী হবে জনগণের। এখানে লেখকবাহিনীর কাজ হবে ধনিক সমাজের ক্রূর, নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ছলনার কথা পরিষ্কার করে সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া — যেন জনসাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রেরণা পেতে পারে তা থেকে। জনগণের সংগ্রামের অকুণ্ঠ প্রশংসাই থাকবে এতে।…
রাজনীতির বিচারে যে সব সাহিত্যিক নিজেদের শ্রেণীচ্যূত, জাতিভ্রষ্ট মনে করে শ্রমিকশ্রেণীরই দর্শনকে জীবনাদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন — তাঁদের গভীর প্রয়াস লক্ষ করা যায় নতুন শ্রেণী-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। লেখিকার বর্তমান উপন্যাসটিকেও এই পর্যায়ে ফেলা চলে অকুণ্ঠ চিত্তে। এমনি একজন মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা সমগ্র জাতির জীবনচাঞ্চল্য! গ্রাম্য পরিবেশ থেকে শহরের জনারণ্যে সর্বত্রই আশ্রয়চ্যুত মধ্যবিত্ত মনের ছোঁয়াচ। এ মধ্যবিত্ত মন নিজের খোলস ছড়িয়ে বের হয়েছে অনন্ত যাত্রার পথে। উদ্বেগ, বিভ্রান্তি আর সমস্যা-সংশয় জড়িত সে পথ। আর তার পাশেই চলেছে দিগ¦লয় রেখায় কাতার দিয়ে বলিষ্ঠ মানুষের দল – শোষিত সর্বহারার মিছিল — উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র ব্যাকুল। দুঃখে আসে তাদের জীবনে — কিন্তু মুহ্যমান করে বিবশ করে দিতে পারে না সে দুঃখ। কর্ম প্রেরণায় এগিয়ে যায় তারা। তাঁদেরই দলে যে মিশতে হবে তাকেও।
সেই অবিনাশী প্রাণশক্তির শিকড়ের সন্ধান যে লেখিকা খুঁজে পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহ। আর কিছু না হোক, গণসাহিত্য সৃষ্টির সযত্ন প্রচেষ্টা এর প্রতিছত্রে সুপরিস্ফুট। ২
দীর্ঘ এ উদ্বৃতির অপ্রত্যক্ষ কারণ হল এটি সুষ্পষ্ট করা যে সাবিত্রী রায় ততদিনে গণসাহিত্যের লেখক হয়েছেন। অথচ মর্মান্তিক এই যে সেই জনগণের প্রাণ যে পার্টি তাই তাঁর স্বাধীনতা হরণ করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। ত্রিসোতাতে 3 সাবিত্রী রায়ের আত্মজৈবনিক উপাদানের উপস্থিতি খুব বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য। উপন্যাসের রূপসী গ্রামকে ব্যক্তি সাবিত্রীর বাল্যজীবনের উপসী গ্রাম হিসেবে সনাক্ত করতে সচেতন পাঠকের অসুবিধা হবার কথা নয়। এমনকি সেখানে রয়েছে রথীন্দ্র মাস্টার (প্রয়াত সাহিত্যসেবক রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী) এবং আরও অনেক চেনা মুখ যাঁদেরকে ব্যক্তি সাবিত্রী রায়ের জীবনের চারপাশে আমরা দেখি। উপন্যাসের অন্য চরিত্র কুসুমলতাকে সাবিত্রী রায়ের পিসিমা অম্বিকা দেবী হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।
ত্রিসোতা শুরু হয়েছে চরকা কাটার সময়। সাথে সাথে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুবকদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মত গ্রামীণ জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ ত্রিসোতা-রও বিশাল জায়গা দখল করে আছে। আর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পদ্মার সাথে লেখিকার সাজুয্যও দুর্লক্ষ নয়। নিজ পরিবার এবং সমাজকে প্রেক্ষাপট বানিয়ে লেখিকা তাঁর এ উপন্যাসের নির্মিতি দিয়েছেন। পদ্মা শুধু উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র নয়, বিদ্রোহী চরিত্রও বটে। ঘটনার ক্রমপ্রসারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এ উপন্যাসে তীব্রভাবে অনুভূত। দুর্ভিক্ষের তীব্র ছোবলে রক্তাক্ত বাঙালি সমাজের কমবেশি চিত্র এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। বাঙালি সাধারণ নারীর যৌন নিরাপত্তাহীন সে সময় বড় ক্রুর। নারীর সম্ভ্রমের মূল্যহীনতার এমন মর্মন্তুদ চিত্র বুঝি শুধুমাত্র সুলেখা স্যানালের (১৯১৮-১৯৬২) ‘সিদূরে মেঘ’ ৪ (১৩৫৯) গল্পেই পাওয়া যায়। ‘সিদূরে মেঘ’ গল্পের অনন্ত আর মালতী দুজনেই তো ঘরে পোড়া গরু। বাংলার সর্বকালের বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষে মালতী যেমন তার সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে পারেনি, তেমিন অনন্তও প্ররোচিত হয়েছিল তার মৃত স্ত্রী ললিতার শরীরকে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে। ত্রিসোতার মদনতো বিলাতী সাহেবের মন গলিয়ে দু’পয়সা বেশি কামাই করতে যে কারও গৃহস্থ বধূর যৌবনকে কালিমাময় করতে রাজী। আর ক্ষুধা! সে তো নিত্যসঙ্গী সে কালেও বাঙালি সাধারণ মানুষের। ধারণা করা যায় সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসসকলের মধ্যে ত্রিসোতাতেই দুর্ভিক্ষের চিত্র সবচেয়ে বেশি মাত্রায় উপস্থিত —
মুসলমান পাড়ার মেয়েরা আসিয়া শাক তুলিয়া লইয়া যায় আশ্রমের ভিটা হইতে। কানে আসে শিশুদের আর্তনাদ। চাউল আনছে তোর বাজানে?
— চাউল নাই আউজকা কয়দিন না? কচু সিদ্ধ চলছে দুই সন্ধ্যা। এক সন্ধ্যা গেছে মিষ্টি আলু-পোড়া দিয়া। আউজকা একমুঠা চাউল আনছে বাবুগো বাড়ির থন — জিভটা জুড়াইয়া আসে। আউস ধানের ফ্যানা ভাতের স্বপ্ন ক্ষুধায় স্তিমিত চোখগুলোতে।
ছোট ছোট একপাল ছেলেমেয়ে পিতলের বাটি রাখিয়া যায় রান্না ঘরের সামনে ফ্যানের প্রত্যাশায়। তারাসুন্দরী একজনের মত চাইল বেশি লয় রোজই। কিছু কিছু ভাত ও ফ্যান একসঙ্গে ঢালিয়া দেয় ঐ পিতলের ঘটিগুলিতে। কোন কোন দিন নিজের ভাতটুকুও দিয়া দেয়। বুকটা যেন স্তদ্ধ হইয়া গিয়াছে — কি ভীষণ দুর্দিন। ঘরে ঘরে অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হাড়গিলা শিশুগুলি টিকিয়া থাকিবে কি এই ফ্যানটুকুর জোরে। ঘটিতে ফ্যান ঢালিতে ঢালিতে ভাবে তারাসুন্দরী। ৫
দুর্ভিক্ষের এ চিত্রের মতই তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় ত্রিসোতার অগ্রসরণ। সেখানে দৃপ্ত পদক্ষেপে কর্মব্যস্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীবাহিনী, কিন্তু সাথে আছে ফরোয়ার্ড ব্লক ও সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমনবার্তা। এসবের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, ভারতের স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু সে স্বাধীনতা যে সাধারণ মানুষের স্বাধীন হওয়ার ইঙ্গিত নয় তা-ও স্পষ্ট। কিন্তু তারপরও মানবজীবনতো আশারই প্রত্যাশায় স্থাপিত। আর সেজন্যেই হয়তো পদ্মা সকলকে হারিয়েও যখন মেয়েকে কোলে তুলে নেয় তখন ‘একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে রোয়াকে’। উপন্যাসটির আলোচনাশেষে একথা স্বীকার করতেই হয় ত্রিসোতা পর্যন্ত সাবিত্রী রায় বড় বেশি ঘটনার বিবরণকারী। সামগ্রিক সময়কাল ও সমাজজীবনকে ধারণ করতে তিনি মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিত ও দৃষ্টিকটুভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেন যা উপন্যাসের সামগ্রিক সৌকর্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তবে পরবর্তী উপন্যাস স্বরলিপিতেই তিনি সে-দার্ঢ্য অনেকখানি অর্জন করেছিলেন কোন সন্দেহ নেই। [ক্রমশ]
সুব্রত কুমার দাস, কামারখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ বর্তমানে থাকেন টরন্টো, কানাডা