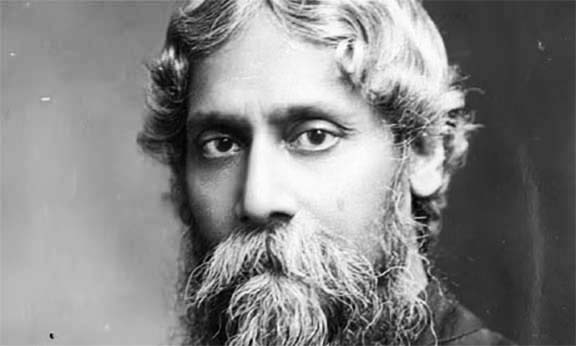
ভারতীয় সংগীতের মূল রসটি হোলো নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-রস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি ছিলো নির্বিশেষের লীলাভূমি। বিশেষের স্থান ছিলো না ভারতীয় সংগীতের রাজ্যে। কোনো একটি বিশেষ সকালের রূপ বর্ণনা করে না ভৈঁরো কিম্বা ভৈরবী। তারা প্রকাশ করছে এমন একটি সকালকে যা সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে আপনার মুখ থেকে। আমাদের রাগরাগিণীর রস তাই এই ব্যক্তি-বিশেষত্বহীন নৈর্ব্যক্তিক রস। বৈচিত্রের অবকাশ নেই এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র-বর্জিত রাগরাগিণীর মধ্যে। অথচ বিশেষকে নিয়েই সৃষ্টির লীলা। বিশেষ মনোভাব, বিশেষ হৃদয়াবেগ, বিশেষ অনুভূতিকে প্রকাশ করাই হোলো আর্টের উদ্দেশ্য। নির্বিশেষের নিস্তরঙ্গ ধারায় যেই বিশেষ দেখা দিলো অমনি ভাব এলো, রস এলো, সৃষ্টি শুরু হোলো। চিরকালের সব সকাল ছেঁকে একটি নির্বিশেষ সকালের রসাস্বাদন করে মানুষের মন তৃপ্ত নয়। সে চায়—বসন্তের পেয়ালায় ঢালা একটি রঙীন সকাল, শরতের মন-কেমন-করা উদাসী সকাল, কালো মেঘের ঘোমটা-দেওয়া বর্ষার সকাল, শীতের কুহেলি-মাখা সকাল, ভালোবাসার আলো-জ্বালা সকাল, বিরহের স্নিগ্ধ প্রশান্ত পাণ্ডুর সকাল, অশ্রুসিক্ত সকাল, আনন্দ-উজ্জ্বল সকাল—এই সকালগুলির প্রতিটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র বিশেষ রস আস্বাদন করতে। ভারতীয় সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষের রাজ্যে বিশেষের প্রকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভূতির প্রকাশ নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের গান। গান আর নৈর্ব্যক্তিক রইলো না। বিশেষ তার অসীম বৈচিত্র নিয়ে দেখা দিলো সুরের রাজ্যে। গান আর নিছক সুরের ব্যঞ্জনা রইলো না, গান তখন বিশেষ মনোভাবের ব্যঞ্জনা হয়ে উঠলো। ভৈঁরো আর ভৈরবী হার মানলো প্রতিটি সকালের বিশেষ অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করতে। তাই সুরের মিশ্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আর এই সুরের মিশ্রণের প্রয়োজন হোলো শুধু সুরের জন্যে নয়, ভাব প্রকাশের জন্যে।
রবীন্দ্রনাথের গান আর একটি নূতনত্ব নিয়ে এলো আমাদের গানের এলাকায়। ভারতীয় দরবারী সংগীতে গানের সুরের ও কথার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো মিল ছিলো না। চমৎকার সুরের সঙ্গে অতি নীরস কথার মিলন ঘটানোই ছিলো রেওয়াজ। শুধু সুরটিকে দাঁড় করাবার জন্যেই গানের কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিলো এতো দিন ।
গানের কথার রস ও সুরের রস, এই দুই রসের মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। কবিতার রস আর সুরের রস, এই দুটি আলাদা হলেও এদের মিলন সম্ভব। তবে সব মিলনের মতো এ মিলনও তিনিই ঘটাতে পারেন যিনি প্রজাপতি অর্থাৎ স্রষ্টা। রবীন্দ্রসংগীতে গানের কথা আর গানের সুর, এ দুটির কোনোটাই আত্ম-বিজ্ঞপ্তির অহংকারে কুরুচির পরিচয় দেয় নি। কথা সুরকে অবজ্ঞা করে নি, সুরও কথাকে অবহেলা করে আপনার পার্থক্যের অসঙ্গতি প্রকাশ করে নি।
কোনো ক্ষেত্রেই সংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সংগীতের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। রাগরাগিণীর এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে তো সুরসৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—“যতো দৌরাত্মই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারি নে। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তার বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমই চলবে। কেন না আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা-পথটায় তাকে বাঁধে না।”
***
রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানে যদিও বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র ছিলো অফুরন্ত, কিন্তু সে গানগুলি সুরের দিক থেকে দরবারী সংগীতের সুরের ঠাটের মধ্যেই বদ্ধ ছিলো। বাগেশ্রী-বাহার তেওরা তালে ‘আমার মিলন লাগি তুমি’, বেহাগ চৌতালে ‘ভয় হতে তব অভয় মাঝে’, আশাবরী ঝাঁপতালে ‘মনমোহন গহন যামিনী শেষে, কানাড়া চৌতালে ‘হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে’, শ্রীরাগ তেওরায় ‘কার মিলন চাও বিরহী’, বড়হংস সারং চৌতালে ‘তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন’, আড়ানা চৌতালে ‘বাণী তব ধায়’, — এইগুলি হচ্ছে এই পর্যায়ের কতকগুলি গান ।
প্রচলিত রাগরাগিণী দিয়ে সব অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এইটে অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন অনেক অনুভূতির সন্ধান পেলেন কবি যাদের ঐশ্বর্য, গভীরতা ও চমৎকারিত্ব ধরা পড়ছিলোনা চলতি রাগরাগিণী দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ অনুভূতিগুলির পূর্ণ প্রকাশের তাগিদে নতুন সুর সৃষ্টির তাগিদে নতুন সুর সৃষ্টির দিকে মন দিলেন। বলাই বাহুল্য যে রাগরাগিণীর মিশ্রণ থেকেই নতুন সুরের সৃষ্টি। তাই ঠাট ও মিশ্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাগুলি আমাদের জানা দরকার। তিনি বলছেন, “গানের জীবকোষ হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ সুরের মিলন। এই সব দানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান বাঁধেন। এমনি করেই সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরী হয়ে ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে নিয়েই গান তৈরী হয়।” রবীন্দ্রনাথ বলছেন—“এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরেই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। সুরের ঠাটগুলি ইঁটের মতো হলেই তাদের দিয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়। দেয়াল কিম্বা আস্ত মহলের মতো হলেই তাদের দিয়ে জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়।” প্রতিটি অনুভূতির ‘জাতিগত সাধারণতা নয়, তার ‘ব্যক্তিগত বিশেষত্ব’ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে রাগরাগিণীগুলোকে ভেঙ্গে চুরে সুরের টুকরোগুলোকে নব নব সুর-রূপে বিকশিত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় “আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড়ো বড়ো ফালি, তাকেই বলে রাগিণী। আজ সেই ফালিগুলোকে ভেঙ্গে-চুরে সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছেমত কোঠা গড়বার চেষ্টা চলছে।”
কিন্তু এই ভাঙ্গা-গড়ার স্বাধীনতা, নব নব সুর-সৃষ্টির জন্যে সুরের উপাদানগুলিকে ভেঙ্গেচুরে নানাভাবে সাজিয়ে দেবার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। রাগরাগিণীর ঠাটগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে তাদের টুকরোগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে সুরের নতুন জীবকোষ তৈরী করবার যে চেষ্টাই আমরা করি না কেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সেই টুকরাগুলি যতই টুকরা হোক তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে।” এই ‘আস্ত জিনিসটার ব্যঞ্জনা’-র অনুভূতিই হোলো সুর-মিশ্রণ-তত্ত্বের সার কথা। যিনি টুকরোর মধ্যে আস্ত জিনিসটা দেখতে পান না, তিনি মিশ্রণের অর্থাৎ নতুন সুর-সৃষ্টির অধিকারী নন। রূপের অখণ্ড ও সমগ্র অনুভূতি, শ্রুতির অনুভূতি ও মূর্ছনার জ্ঞান—এই হচ্ছে নতুন সুর-সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য।
কি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গেই না রবীন্দ্রনাথ সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গান, ‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু’ গানটি দেখুন। গানটি আশাবরী, ললিত, রামকেলি ও বিভাসের মিলনের ফল। এমনি সৃষ্টির নিপুণতা যে গানটিতে কোনো একটি রাগকে আলাদা করে ধরবার যো নেই। মনে হচ্ছে, বুঝি একটিকে ধরেছি, দেখি, অমনি সে সরে গেছে। শুদ্ধ ‘ধা’ ও শুদ্ধ ‘নি’র আশেপাশে আনাগোনা নেই, বিভাস রূপহীন অথচ কতকগুলি সুর আছে বিভাসের প্রতিনিধি হয়ে। রামকেলি লুকিয়ে ফুটেছে স্বরবিন্যাসে। ‘কুসুম ফোটে’ কথাগুলির সুর ললিতকে প্রকাশ করছে। আর সব ছাপিয়ে আছে আশাবরী। ভীমপলশ্রীর সঙ্গে মূলতানের মিশ্রণে অনেক গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন, ‘বুঝি বেলা বহে যায়’, ‘আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে’, ‘নাই রস নাই’, ‘আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া’ প্রভৃতি গানগুলি। সারঙ, মল্লার ও কানাড়ার মিশ্রণ তিনি ঘটিয়েছেন ‘চক্ষে আমার তৃষ্ণা’ গানটিতে। মীড় ও মূর্ছনার ঠাসবুনুনি নেই গানটিতে, আকস্মিক পরিবর্তনের খেলা ধরা দিয়েছে এর হৃদয়হরণ সুরে। তিলক কামোদ ও দেশ, এই দুটি রাগের সঙ্গে মল্লারের মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ‘ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো’ গানটি এই তিন রাগের ত্রিবেণীসঙ্গম। ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ’ গানটির সুরে পঞ্চমের সঙ্গে বাহার এসে মিলেছে। ললিতের আমেজও লেগেছে সুরটিতে। সোহিনীর সঙ্গে পঞ্চমের মিলন হয়েছে ‘আজি বরিষণ মুখরিত’ গানটিতে। এ রকম মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ কখনো করেন নি। কি অনুপম এই মিশ্রণ! এ রকম অফুরন্ত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টির।
ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা সুরের গান রবীন্দ্রনাথ ভেঙেছেন। শুধু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের সুরে কেন, পাশ্চাত্য সংগীতের সুরেও গান বেঁধেছেন তিনি। বাল্মীকিপ্রতিভার ‘কালী কালী বলো রে আজ’ গানটি, আর ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’ ও ‘পুরাণো সেই দিনের কথা’ প্রভৃতি গান পাশ্চাত্য গানের সুরের ছাঁচে ঢালাই-করা।
ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলি থেকে যেসব সুর আহরণ করে গান বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মহীশূরী ভজনের সুরে ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’, মাদ্রাজী গানের সুরে ‘নীলাঞ্জন ছায়া” ও শিখ ভজনের সুরে ‘বাজে বাজে রম্য বীণা’ গানগুলি।
হিন্দী গানও অনেক ভেঙ্গেছেন, যেমন মিঞাকি মল্লারের সুরে গাঁথা ‘কোথা যে উধাও হোলো’ অপূর্ব গানটি। মিঞাকি মল্লারের রাগ-শুদ্ধতা ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই গানটির কয়েক জায়গায় কোমল নি, কোমল দা, নি, পা, এই স্বরগুলি ব্যবহার করেছেন। তাতে শুদ্ধতা-বিশারদ ওস্তাদদের মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছেন হয়তো, কিন্তু সুরটি অপূর্ব হয়েছে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের ঠুংরি চালের গানের সুরে বেঁধেছেন ‘তুমি কিছু দিয়ে যাও’। কাফি সুরের হিন্দী গান ভেঙে এসেছে ‘অশ্রুভরা বেদনা’ আর ভৈরবী সুরে গাঁথা মীরাবাঈয়ের একটি গানের সুরে পিলু আর বারোয়াঁ মিশিয়ে বেঁধেছেন ‘কখন দিলে পরায়ে’। টপ্পাও মহাকবির প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুর টপ্পার চেয়ে পরিমিতি তানের, চিকণ ও স্বল্প কাজের শোরীর টপ্পার ধরণ বেশী পছন্দ করতেন। টপ্পার সুরে বেঁধেছেন—‘বন্ধু রহ রহ সাথে’, ‘হৃদয়বাসনা পূর্ণ হোলো’, ‘কে বসিলে আজি হৃদয় আসনে’, ‘এ পরবাসে রবে কে’ প্রভৃতি গানগুলি।
***
দেশবিদেশের বহু গানের সুর চয়ন করে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই তিনি নকলনবিশ ছিলেন না, অর্থাৎ যা পেলেন তাই হুবহু ধরে দিলেন এই গোলামি তিনি কখনো করেন নি। যা নিয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর প্রাণের সুরের দু একটি সুর মিলিয়ে তাঁর নিজের অন্তর—ঐশ্বর্যের রঙ মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সত্য করে গ্রহণ করেছেন। নিজের রঙ ও সুর না মেশালে কোনো কিছুকেই নিজের করে নেওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন বাহার রাগের ‘আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ’ গানটিতে শুদ্ধ বাহারের রূপ ফোটাবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েন তো তাঁকে বোঝাতে না পারলেও সাধারণ মানুষকে এটা সহজেই বোঝানো যাবে যে গানের সুরকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন কথার ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। রাগ-রাগিণীর রূপ ফোটাবার জন্যে সুরকে তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—“যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকে বাহাল রাখিব না কেন?”
তাই রবীন্দ্রনাথের হিন্দী-ভাঙ্গা গানগুলিতে শুদ্ধ রাগ রূপ ফুটিয়ে তোলবার অমার্জনীয় প্রয়াস থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরগুলির বিশেষত্ব লোপ করে তাদের সাধারণ করে জাতে তোলবার চেষ্টা করলে সুরগুলির অনন্যসাধারণতা নষ্ট করা হবে।
রবীন্দ্রনাথের গানে তান যোজনা সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথ তানের দীর্ঘ টানাটানি পছন্দ করতেন না। চিকণ কাজের স্বল্প তান, এই ছিলো তাঁর পছন্দ। গানের একটা অংশ হচ্ছে রসাত্মক বাক্য। সেই বাক্যগুলিকে ভেঙ্গে চুরে তাদের অংশ নিয়ে বেপরোয়া ব্যবহার করা যায় না। তাতে রসের ব্যাঘাত ঘটে। তান হচ্ছে সুরের অলংকার। অলংকার পরতে জানা চাই, পরাতে জানা চাই। মাত্রাবোধ না থাকলে অলংকার সৌন্দর্যের হানি করে। বহু ললনা তাঁদের ললিত দেহে সেই বিপদের প্রমাণ নিয়তই বহন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিতে যে স্বল্প তান ব্যবহার করেছেন, সেই তানগুলিকে বিস্তারিত করবার অধিকার কারো নেই। কেননা স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হাত চালাবার অধিকার আটপৌরে মানুষের নেই। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি করেন, তার থেকেই রস, তার থেকে সৃষ্টি। যিনি গান গান তিনি সাধারণত স্রষ্টা নন, তাই স্রষ্টার রসোপলব্ধি তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—“যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়। এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড় মেলে…….। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশলের অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসেবেই চলে, সোনা হিসেবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়তেই থাকে। কেননা ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।
এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানে, তাঁর গানের সুর-দেহে তানের স্ফীতি না যোগ করবার অধিকার গায়ককে দেওয়ার অর্থ হবে রবীন্দ্রনাথের গানকে সুরস্রষ্টা নয়, সুর-কৌশলী গায়কের কৌশল দেখানোর যন্ত্র করে তোলা।
***
যেমন বাংলা কবিতার ছন্দের আড়ষ্টতা দূর করেছেন রবীন্দ্রনাথ পয়ারের রাজত্বে যুগ্ম বর্ণকে দু মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করে শব্দের মধ্যে ফাঁকটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত করে, তেমনি নানা ছন্দের প্রবর্তন করে গানের সুর-দেহকেও সাজিয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ ভাবের উপর লক্ষ্য রেখে গানের ছন্দ-বৈচিত্ৰ সাধন করেছেন, যেমন ‘কালমৃগয়া’র ‘আর নহে আর নহে’ আর ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যের ‘ধীরে ধীরে বও’ গানদুটিতে ছন্দের মন্থরতা সৃষ্টি করেছেন ভাবের লক্ষ্য রেখে। আবার ছন্দে ও তালে উল্লাস, পৌরুষ ও উচ্ছ্বাস ফুটিয়েছেন ‘আমরা নূতন যৌবনেরি দূত’, ‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে’ প্রভৃতি গানে।
আবার যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে ছন্দ-বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। ‘সর্বখর্বতারে দহে’, ‘গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে’, ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’ প্রভৃতি গান যুক্তাক্ষরের ধ্বনির মিশ্রণে অভিনব রূপলাভ করেছে।
কথার ধ্বনি-বৈচিত্রে ছন্দের বৈচিত্র এনেছেন, যেমন, ‘বাজোরে বাঁশরী বাজো’ গানটিতে ‘মধুকরপদভর-কম্পিত-চম্পক-অঙ্গনে’ এই কথাগুলির ধ্বনিবৈচিত্রের দ্বারা ছন্দের বৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে।
কোথাও আবার সুরের ছন্দের বিভিন্ন মাত্রায় কথার বিরামে ছন্দ-বৈচিত্র এনেছেন যেমন ‘ফু—লে ফু—লে ঢ—লে ঢ—লে’ এই তিন মাত্রার ছন্দের গানে মাঝের মাত্রায় বিরাম দিয়েছেন।
কথার দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক দেওয়া তালও সৃষ্টি করেছেন, যেমন ‘তুমি তো সেই যাবেই চলে’ গানটিতে।
একই গানের নানা অংশের বিচিত্র ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে একই গানে বিভিন্ন তাল ব্যবহার করেছেন, যেমন ‘ঐ আসে ঐ অতি’ ও ‘হে নিরুপমা’ গান দুটিতে।
কোথাও আবার তালের বিভিন্নতায় গানে ছন্দ-বৈচিত্র এনেছেন। যেমন ‘শ্যামল ছায়া নাই বা এলে’ গানটি ২।৪ মাত্রার তালে, ‘কাঁপিছে দেহলতা থর থর’ এটি ৩।৪।৪ এই এগারো মাত্রা গুচ্ছের একাদশী তালে, ‘জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে’ ৩।২।৩ মাত্রার রূপকড়া তালে, ‘ও দেখা দিয়ে যে চলে গেলে’ গানটি ৩।৬ মাত্রার নবতালে ও ‘যেতে যেতে একলা পথে’ গানটিতে ৩।২ মাত্রার ঝম্পক তালে।
***
ভারতীয় সংগীতের ধারার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টি স্রোতহীন বদ্ধ জলে নতুন সুরসৃষ্টির স্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে কোন দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ সম্ভব তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন-কিছু-করার নেশা বড়ো সর্বনেশে নেশা। নতুন কিছু করবার মত্ততার মতো সৃষ্টির শত্রু খুব কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“সৃষ্টিশক্তিতে যখনই দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তাই তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করে থাকে।”
রবীন্দ্রনাথ বলছেন—“আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনায় আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগের অরুণবর্ণে সহজেই নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের ঊষাকে নিউমার্কেটে ‘খুন’ ফরমাশ করতে হয় না ।”
তাক-লাগানোর এই নেশার হাত থেকে আধুনিক সুরকারেরা যেন আপনাদের বাঁচিয়ে রাখেন। তবেই রবীন্দ্র-সংগীত-ধারার সঙ্গে যোগ রেখে তাঁদের স্বজন-প্রয়াসে তাঁরা নবীনের স্পর্শ পাবেন।