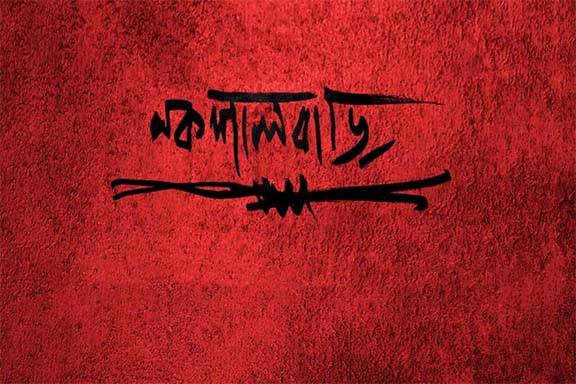
তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তর পরিসরে সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা দেশ। নকশালবাড়ি আন্দোলনও সূচনায় ছিল কৃষক আন্দোলন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকার সশস্ত্র কৃষকগণ ধনী জোতদার ও চা-বাগানের মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি দখল করার জন্য লড়াই শুরু করে। পরবর্তীতে এতে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণের ফলে এই আন্দোলন সামগ্রিক বৈপ্লবিক চেহারা নেয় এবং তা ব্যাপ্ত হয় ভারতের বিভিন্ন অংশে। দেশের হাজার হাজার তরুণ চলে আসে এই বিপ্লবের কাজে। এই আন্দোলন ছাত্র-যুব সমাজের বিপুল অংশগ্রহণে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা উত্তর পরিসরে সত্তর দশক এসেছিল একটা পৃথক আত্মবিচার আর আত্ম-আবিষ্কারের দশক হিসেবে। ‘সত্তর দশক মুক্তির দশক’ রাজনীতির এই শ্লোগানে যেমন উন্মাদনা এনেছিল তেমনি একদিকে এনেছিল চরম বিপর্যয় আর অনিশ্চয়তা । মধ্যবিত্ত জীবনে এ এক চরম অস্থিরতার কাল। নকশালদের ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি, সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা ঘোষণা আর রাজনৈতিক পালাবদলের ভেতর দিয়ে এ এক স্বতন্ত্র দশক। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সেই সময়ের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। নকশাল আন্দোলন যেমন দেশের রাজনৈতিক জীবনে আলোড়ন ফেলেছিল তেমনই সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি। তবে কবিতাতে এই আন্দোলনের প্রভাব সর্বাধিক এবং সুদূরপ্রসারী।
১৯৬৭ সালের ২৫ মে অর্থাৎ সংঘর্ষের দিনই কবিতায় নকশাল বাড়ির পদধ্বনি শোনা যায়। সেদিনই রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষায় দিলীপ বাগচি তুলে ধরেন তাঁর অনুভবের কথা।
“ও নকশাল নকশাল নকশালবাড়ির মা
ও মা তোর বুকত্ অকেতা ঝরে
তোর খুনত্ আঙ্গা নিশানা লঘ্যা
বাংলার চাষী জয়ধ্বনি করে।।
… ওমা তোর বুকত্ অকেতা ঝরে”
আন্দোলনের সূচনালগ্নেই যেভাবে কবির লেখনী সচল হয়েছে তা বিস্ময়কর। এত দ্রুততার সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের কথা কবিতাতেই উঠে এসেছে। অনেকেই আন্দোলনের শরিক হয়ে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। যেমন দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ, মুরারী মুখোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তেমনই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, তরুণ সান্যাল, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ সচেতন ভাবে কবিতা লিখেছেন। নকশাল আন্দোলনের কবিতায় উঠে এসেছে রাজনৈতিক মতবাদ থেকে শুরু করে সশস্ত্র সংগ্রাম, মতবাদ, লড়াইয়ের ময়দানে অংশগ্রহণকারীদের কথা। বেশ কিছু কবিদের কবিতায় সশস্ত্র সংগ্রামের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। দুর্গা মজুমদার ১৯৬৭ সালের প্রকাশিত ‘সশস্ত্র বিপ্লব’ কবিতায় সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী তুলে ধরেছেন।
নকশাল আন্দোলনে কয়েকজন কবি পুলিশের গুলিতে বা জেলখানায় বন্দি হয়ে খুন হয়। এঁদের মধ্যে তিমির বরণ সিংহের কথা প্রথমেই বলতে হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র তিমিরবরণ সিংহ। নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করতে পার্টির নির্দেশে গ্রামে যান। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ বহরমপুর জেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাঁর কবিতায় বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কবি চিনেছেন শত্রুদের মুখ। দিনবদলের স্বপ্নে মশগুল কবিকে মধ্যবিত্ত চেতনায় পাগল বলে মনে হলেও তাদেরকেই কবি প্রশ্নের সম্মুখে এনেছেন :
“ও পাগল, ও পথ তুই মাড়াসনে মাড়াসনে
ও পাগল, পাগলামি তুই ছাড়
ঘরে তোর মুমূর্ষু বোন
পাগলামি তুই ছাড়
বল তো
শহিদ হওয়া কি আমাদের পোষায় ?”
অমিয় চট্টোপাধ্যায় ২৬ নভেম্বর ১৯৭১-এ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে শহিদ হন। তাঁর ‘যুদ্ধের জন্য’ কবিতায় প্রতিবাদী সত্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্রোণাচার্য ঘোষ ১৯৭২-এ হুগলি জেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ‘বস্তুত এখন প্রয়োজন’ কবিতায় কবি শোষণহীন হৃদ্যতার মধ্যে আরামের হাতছানি দেখতে পান। আর তার জন্য কবি মনে করেন :
“এখন সময় নেই চপল ছায়ায় বসে গল্পের আসর
এখন সময় নেই পান করি অসহায় চরিত্রের মদ;
তীক্ষ্ণ বুলেটের মুখে বস্তুত এখন প্রয়োজন
শ্রেণিশত্রুনিধনের কঠিন কঠোর এক দৃঢ় সংগঠন।”
আবার কবি মুরারি মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ সালে ২৫ জুলাই হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে শহিদ হন। কৃষক আন্দোলনে তিনি গোপীবল্লভপুর, ডেবরা, সুরমুহী, বহড়াগোড়া অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর ‘ভালোবেসে’ কবিতায় কবি ভালবাসাকে সূর্যের তাপে, বাঁধ ভাঙা বন্যার তোড়ে, বজ্রের শব্দে, আগুনের জ্বলন্ত শিখার উপরে করাঘাত করে নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তুলেছেন। ভালবাসা আপাতত স্থগিত। তাই কবি বলেন :
“চাঁদ নদী ফুল তারা পাখি
দেখা যাবে কিছুকাল পরে
কেননা এ অন্ধকারে শেষ যুদ্ধ বাকি
এখন আগুন চাই আমাদের এই কুঁড়েঘরে।”
নকশাল আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সরোজ দত্ত (১৯৭১–এর ৫ আগস্ট, পুলিশ কলকাতা ময়দানে তাঁকে গুলি করে মেরে রটিয়ে দেয় তিনি নিখোঁজ) ‘কোনো বিপ্লবী কবির মর্মকথা’য় কবি নিজের মর্মবেদনাই তুলেধরেছেন। ‘দুঃসাহসী বিন্দু’ হয়ে তিনি ‘বুকে সিন্ধুর চেতনা’ বয়ে বেড়ানোর পরিচয় তুলে ধরেছেন।
নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও যাঁরা কবিতাকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করে তুলেছেন তাদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। নকশাল আন্দোলনের প্রতিটি ঘটনায় তিনি আলোড়িত হয়েছেন। তাঁর ‘নরক’ কবিতায় হত্যার চিত্র তুলে ধরে সময়কেই নির্মাণ করেছেন কবিতায় :
“কেননা হত্যাই সত্য, হত্যা ধর্ম, কে মারে এবং কাকে মারে, এই নষ্ট
চরিত্রের ভিড়ে কেউ নেই হিসেব নেবার। শুধু হত্যা চাই।”
নকশাল আন্দোলন দমনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিষয়টি বহুচর্চিত। সে-সময় আন্দোলনকারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা বা কারাগারে গুলিকরে খুন করা বা গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে খুন করা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্নরূপ উঠে এসেছে কবি কৃষ্ণ ধরের ‘একদিন সত্তর দশকে’ কবিতায়। আবার সমীর রায়ের কবিতায় উঠে এসেছে সেই সব রক্তাক্ত দিনের স্মৃতি :
“আমি ভুলিনি, আমি ভুলিনি, আমি ভুলিনি
আমার গলার উপর পা রেখে, আমার মুখের রক্ত দিয়ে
নরমুণ্ড শিকারীরা কলকাতা শহরে পোস্টার সেঁটেছে-
‘বাঁচুন, বাঁচতে দিন, হিংস্রতা বর্জন করুন’।”
আবার মণিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর ‘গান্ধি নগরে এক রাত্রি’ কবিতায় নকশাল আন্দোলন দমনে পুলিশি সন্ত্রাসের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। কবিতায় তুলে এনেছেন ‘বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজি রক্তধারা’র প্রসঙ্গকে। তারই অন্য একটি কবিতা ‘সুচরিতা’। যেখানে প্রেম-ভালোবাসা সঙ্গে সংগ্রাম এর পরিচয় যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনই অনন্তজয়ের প্রতিশ্রুতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।
নকশাল আন্দোলনের শহিদ হওয়া কবিরা যেমন কবিতা লিখেছেন। তেমনই তাদের নিয়েও কবিতা লেখা হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের শহিদ তিমিরবরণ সিংহকে নিয়ে শঙ্খ ঘোষের মতো স্বনামধন্য কবিও কবিতা লিখেছেন :
“ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুট মার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।”
তেমনই কবি সনৎ দাশগুপ্ত দ্রোণাচার্য ঘোষকে মনে রেখে লিখেছেন ‘দ্রোণফুল’ নামক কবিতাটি। কবি লিখেছেন- ‘রক্তমাখা দ্রোণফুল পড়ে আছে ঘাতকের থাবার তলায়’। মৃদুল দাশগুপ্তের ‘আগামী’ কবিতায় দ্রোণাচার্য ঘোষের কথা উঠে এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। আবার তিমিরবরণ সিংহ ও স্মরণ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিতা রচনায় সামিল হয়েছেন সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ‘তিমির স্মরণ তিমির হরণ’ কবিতায় দুই বিপ্লবীর কথা উঠে এসেছে। আবার আজিজুল হক হাওড়া জেলে বন্দি অবস্থায় প্রবীর রায়চৌধুরীর মৃত্যুতে লেখেন ‘প্রবীর রায়চৌধুরী শহিদ হওয়ার সংবাদে’ কবিতাটি। আবার নকশাল আন্দোলনের প্রাণপুরুষ চারু মজুমদারের মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রেখেছেন মনোরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর ‘শহিদের মৃত্যুকে মনে রেখে’ কবিতায়। এছাড়াও নকশাল আন্দোলনের বিস্তৃত পরিসর কবিতায় নানাভাবে উঠে এসেছে নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না’, সৃজন সেনের ‘থানাগারদ থেকে মাকে’, অনিন্দ্য চাকীর ‘সত্তর দশকের কবিতা’, অমিত চক্রবর্তীর ‘নকশালবাড়ি’, কবি কৃষ্ণ ধরের ‘রক্তপাত’, গণেশ বসুর ‘রক্তের ভেতরে স্বপ্ন’ তরুণ সান্যালের ‘বিষন্ন শহিদ’ প্রভৃতি কবিতায়। এই নকশাল আন্দোলনের কবিতা আলোচনায় সুজিত কুমার পাল বলেছেন : “নকশাল আন্দোলনের কবিতায় কবিতার আঙ্গিক নিয়ে ভাবনার কথা বিশেষ কেউ বলেন না। এখানে আন্দোলনের গুরুত্বটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের কার্যকারিতা থেকেও গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিবাদীসত্তা।” তাই কবিরা তাদের নকশাল প্রভাবিত কবিতায় নকশাল আন্দোলনের রক্তাক্ত সময়ের ছবি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই শহিদ স্মরণেও কবিতাকেই মাধ্যম করেছেন। তাই নকশালবাড়ি আন্দোলনকেন্দ্রিক কবিতা গুলি সময়কে তুলে ধরার পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের কথাও আমাদের স্মরণ করায়, ভাবায়।
লেখক : কার্তিক কুমার মণ্ডল, সহকারী শিক্ষক, মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জয়পুর, পুরুলিয়া।