
জয়নগর
প্রায় পাঁচশো বছর আগে আদি গঙ্গা এই শহর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেব নীলাচলে গমনকালে জয়নগরে থেমেছিলেন। পলি জমে জমে গঙ্গা ক্রমে মজে জয়নগরের সঙ্গে মজিলপুর শব্দটি উপসর্গ হিসেবে জুড়ে গিয়েছে। প্রাচীন জনপদ গড়িয়া হরিনাভি দক্ষিণ বারাসাত হয়ে যদি জয়নগরে যান তাহলে রাস্তার ডান পাশে যে সব নয়নজুলি বা ছোট ছোট খাত দেখবেন, আদতে এই রাস্তায় একসময় চলন ছিল গঙ্গার। রাঢ় বাংলার বিশাল বিশাল সওদাগরী জাহাজ এই রাস্তায় যেত সমুদ্রপানে। জয়নগরে এই মজে যাওয়া গঙ্গা বেঁচে আছেন এই শহরে ঘোষের গঙ্গা, মিত্র গঙ্গা হয়ে। অর্থাৎ ঘোষেদের বা মিত্রদের এলাকা দিয়ে প্রবাহিত ছিলেন যে গঙ্গা সে গঙ্গা আজ মজা দহে পরিণত হয়েছে। সেই দহ দেখার সময়েই সেখানকার মন্দির আর সংগ্রহশালাটি দেখে নেওয়া যেতে পারে।
এই শহরে আদি বাংলার প্রাচীন শিক্ষাব্রতীদের বাস ছিল — যারা ব্রিটিশ পূর্ব সময়ে বাংলার এই অঞ্চলে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন জ্ঞানের প্রদীপ শিখা। প্রখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই শহরে বাসিন্দা। তাঁর পরিবারকে এখনও এলাকায় সিদ্ধান্ত পরিবার হিসেবে ডাকা হয়।

জয়নগর বললেই বাঙালির আর কিছু না মনে পড়ুক, এই শীতে অবশ্যই মনে পড়বে মোয়ার কথা। বাংলার প্রায় সব মিষ্টিই এলাকা ভিত্তিক – প্রত্যেকটিই স্বনামেই খ্যাত। আমরা যখন মিষ্টির কথা বলি সেই এলাকার কথা জুড়ে নিই মাত্র যেমন মালদার কানসাট, বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানা ইত্যাদি। তেমনি মোয়া মানেই জয়নগরের মোয়া। শীতকালে সারা বাংলা তথা ভারতজুড়ে মোয়া ব্যবসার যে স্বতষ্ফুর্ত জনগণ-ব্রান্ডিং হয় সেটা যে কোনও কর্পোরেট মার্কেটিং পেশাদারের স্বপ্ন। ছোট ব্যবসায়ীরা জানেন কোন সময়ে কী ব্যবসা হয়। তাঁদের মত বাজার বোঝা মানুষ আজও খুবই কম আছেন। রাস্তার পাশে যে যেখানে পারেন একটা দোকান খুলে বসে যান। সারা বছর হয়ত এটা ওটা সেটা বিক্কিরি করছেন, কিন্তু শীতকাল এলেই লাল শালুতে দোকান মুড়ে, দোকানে বিশাল বিশাল অক্ষরে জয়নগরের আসল মোয়া শব্দবন্ধটি লিখে তিন টাকা পিস থেকে পনেরো টাকা পিস পর্যন্ত মোয়া বিক্রি করতে থাকেন। মোয়া থাকে চিত্রিত মাটির হাঁড়িতে। একসময় বাংলাদেশে যা শখের হাঁড়ি নামে পরিচিত ছিল। রকমারি মোয়ার সঙ্গে খাজা, আর নানা সব মিষ্টি। সঙ্গে মাটির নাগরীতে নলেন গুড় আর সরায় মোড়া পাটালি। সে এক অপরূপ আয়োজন।
স্থানীয় মানুষেরা বলেন নৃত্যগোপাল সরকার আর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রথম জয়নগরের মোয়ার স্রষ্টা। কেউ বলেন পাশের গ্রাম বহড়ুই আদত মোয়ার উৎপত্তি। আমরা এই লড়াইতে ঢুকছি না। যাই হোক জয়নগরের মোয়া বানাতে আবশ্যিক প্রয়োজন কণকচূড় ধানের খই অনুপান হিসেবে উতকৃষ্ট ঘি, নলেনগুড় আর নানান মশলা সঙ্গে চূড়ায় একটা কাজুবাদামের অর্ধেক কোয়া আর অর্ধেক কিসমিস। মুখে মেলানো জয়নগরের মোয়া তৈরি।
জয়নগরের পুতুল শিল্প
গণেশজননী, নারায়ণী, কৃষ্ণ-বলরাম, দক্ষিণরায়, বনবিবি— পর পর সাজানো অসংখ্য পোড়া মাটির পুতুল। দেখতে প্রচলিত মাটির পুতুলের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। টানা টানা চোখ, গোলগাল গড়নের সাবেক বাংলার এই পুতুলের কদর গোটা পৃথিবী জুড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-মজিলপুরে তৈরি এই শিল্পসামগ্রী স্থান পেয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, ভারতীয় সংগ্রহালয় থেকে দিল্লির জাতীয় সংগ্রহালয়ে। শুধু সংগ্রহালয় নয়, লোকশিল্পের ইতিহাস, এমনকী, লোকশিল্পের বইয়েও স্থান পেয়েছে বাংলার প্রাচীন এই পুতুল শিল্প।
বর্তমানে শম্ভু দাস এই কাজ করেন। তিনি বাবা বিখ্যাত পাঁচুগোপাল দাসের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। পাঁচুগোপালও ছিলেন নাম করা শিল্পী। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শম্ভু আঁকড়ে ধরে রেখেছেন এই শিল্পকে। কিন্তু কত দিন আর পারা যাবে তা নিয়ে সংশয়ে জয়নগর-মজিলপুর আর শিল্পী নিজেও।

জয়নগর মজিলপুরের পুতুল দু’প্রকার। হাতে তৈরি এবং ছাঁচের। প্রচলিত দেবদেবীর পাশাপাশি তৈরি হয় নানা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি। হাতে তৈরি পুতুলের মধ্যে নারায়ণী, শীতলা, বনবিবি, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন, মানিকপীর, আটেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর উল্লেখযোগ্য।আর ছাঁচের পুতুলের মধ্যে রয়েছে গণেশজননী, জগদ্ধাত্রী, রাধাকৃষ্ণ, কালিয়দমন, ষড়ভূজচৈতন্য, কলকাতার বাবু, গয়লা-বৌ, কৃষক ইত্যাদি। এ ছাড়াও রথের সময় জগন্নাথ, ঝুলন-জন্মাষ্টমীর সময় রাধা-কৃষ্ণ, গোপাল, নববর্ষে লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তির ভাল চাহিদা থাকে। এমনও হয় সময়ে সময়ে শম্ভু চাহিদামত সরবরাহ করতে পারেন না।
জয়নগরের শোলা
শোলা শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে – অন্তত ২৪ পরগণার জয়নগর প্রান্তে। এই ব্যবসা ক্রমশই গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অল্পপুঁজির দক্ষতা নির্ভর শিল্পের ইতিবাচক বিশেষ দিকটি হল অন্যান্য কারিগর উৎপাদনের মত এই শিল্পে দূষণ নেই। এটি একটি কৃষি ভিত্তিক শিল্প। শুধু শিল্প নয়, শোলার চাষও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। শোলা গাছ জলা জায়গায় বেশি হয়।
বাংলাদেশ বা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে বনগাঁ, হাবড়া, বসিরহাট, কল্যানীর দিকে জলা জায়গায় যে শোলা হয় সেগুলি মোটা, বড়ো, নরম ও তাজা। ওইগুলিই সেরা জাতের শোলা। চাষ হত ওই সব অঞ্চলে, তবে বাজার বসত হাওড়ায়। শিল্পীরা আগেই হাওড়া থেকে শোলা গাছ কিনে আনতেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার মহেশপুর গ্রামেই প্রথম শোলার কাজ আরম্ভ হয় – আনুমানিক দু’শ বছর আগে।
প্রায় ১০০ বছর আগে মোকিমপুরে ও ৪০-৫০ বছর আগে পুকুরিয়ায় শুরু হয়। মহেশপুরের ১০০ শতাংশ ও পুকুরিয়ার ৯৯ শতাংশ পরিবার এই শোলার কাজ করেন। এছাড়াও হাটতলা, গোকুলনগর, সুঁদির হাট, কালিতলা, গোপালনগর প্রভৃতি গ্রামে কাজ হচ্ছে। শোলার শিল্পদ্রব্য মাদ্রাজের তুতিকোরিন বন্দর দিয়ে জাহাজে কন্টেনারে ভরে বিদেশে রপ্তানি হয়। আগে শোলা শিল্পীরা টোপর, কল্কা, ঠাকুরের গহনা, কদমফুল, চাঁদমালা ইত্যাদি তৈরি করতেন।

ফুলের কাজ প্রথম শুরু করেন মোকিমপুরের মন্টু গায়েন ও মহেশপুরের ভীষ্ম কয়াল। তারপর অন্যরাও করতে থাকেন। শোলার ফুলের মধ্যে দর্শনীয় গোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকা এই কাজ মন্দিরবাজার থানার কিছু গ্রাম ছাড়া কোথাও হয়না। যদিও দক্ষিণ ২৪ পরগণারই শিরাকোল, আমতলা, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও শোলার কাজ হচ্ছে। এখন এই পুকুরিয়া হাটে প্রতি শনিবার সকাল পাঁচটা থেকে ৮/৯ টা অবধি শোলার শিল্প সামগ্রি কেনা বেচা হয়। জয়নগর ও মগরাহাট থানার বাঁকার দাঁড়, ঈশ্বরীপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে হিন্দু ও মুসলিম চাষিরা শোলা গাছ আনেন এখানে বিক্রি করতে।
শোলা গাছের বান্ডিলকে আঞ্চলিক ভাষায় ‘তারি’ বলে। এক তারি-তে আট-দশ বা পনেরো পিস শোলা গাছ থাকতে পারে। এক তারি সরু শোলা গাছের দাম ৪ টাকা হতে পারে, আবার ভালো শোলা হলে তার দাম ২০ টাকাও হতে পারে। শোলা শিল্প সামগ্রী তৈরিতে লাগে সাদা সূতো, ফেভিকল, আঠা, হলুদ, লাল, সবুজ, ব্রাউন ইত্যাদি আট দশ রকমের রাসায়নিক রঙ। সরঞ্জাম বা হাতিয়ার হিসেবে লাগে ১) কাতি — দুরকমের শোলা পাতা কাটার জন্য। ২) ডিজাইন ছুরি ছয় সাত রকমের। ৩) বাটালি (ছোটো) তিন রকমের। এছাড়াও লাগে কাগজ কাটার জন্য কাঁচি।

এই অঞ্চলের শোলার কাজ প্রথম শুরু হয় মহেশপুর গ্রামের মালি পাড়ায়। প্রকৃতপক্ষে এটি হালদারপাড়া, সবার পদবী হালদার। কিন্তু যেহেতু প্রতিমার শোলার চাঁদমালা ইত্যাদি তৈরি করেন সেই অর্থে তারা মালাকার বা মালি। তাঁরা শোলার মুকুট, টোপর, ঠাকুরের গয়না করেন। তাঁদের মালা যায় কুমোরটুলি, বড়োবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে। আর যায় কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবারেও। কুমোরটুলি থেকে বোম্বে দিল্লীও যায় তাদের তৈরি শোলার দ্রব্য। আনেকের হাতের কাজ আমেরিকা পর্যন্ত যায়। এই শিল্পের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। আগের থেকে অনেক বেশি লোক যুক্ত হয়েছেন এই শিল্পে। বাঁশবেড়িয়া, মৌখালি, হাটতলা, রাঙাবেড়িয়া, চৈতন্যপুর, মূলদিয়া ইত্যাদি গ্রামেও হচ্ছে এই কাজ। আমেরিকা, হংকং, সিঙ্গাপুরে শোলা মাদ্রাজ বন্দর দিয়ে রপ্তানি হয়। প্রায় ২০-২৫ টি গ্রামের আনুমানিক হাজার কুড়ি মানুষ এই শোলা শিল্পে নিযুক্ত আছেন। এবং মাসে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার কেনাবেচা হয় এই গ্রামগুলিতে (এটা ২০১৫র হিসেব)।

সিনেমায় ডেকরেশন, গৃহ বা আঙিনা সজ্জার কাজে শোলার সামগ্রীর দারুন চাহিদা। এমনকি বিদেশেও চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ১৫-১৬ বছর ধরে শোলার সামগ্রীর রমরমা চলছে। তবে বর্তমানে নকল প্লাস্টিকের তৈরি ফুল কিছুটা বাজার দখল করেছে। কিছুটা খেজুরপাতা, তালপাতা থেকে প্রস্তুত ঘর সাজাবার জিনিসও বাজারে জায়গা নিয়েছে। মহেশপুর গ্রাম তথা মন্দিরবাজার থানায় ৫ শতাংশ বাজার এসবের দখলে। দক্ষিণ বারাসাত অঞ্চলের গোঁড়ের হাট এলাকায় খেজুর পাতা ইত্যাদির প্রাকৃতিক জিনিস ভালো তৈরি হচ্ছে, জানালেন সুব্রত হালদার।
জয়নগর মজিলপুরে মাহাত্ম্য বোঝা যায় রাসযাত্রার দু-তিনদিন আগে থেকে। সে সময় মজিলপুর দত্তবাজারে শোলার কদমফুল পাখি নিয়ে শোলাশিল্পীরা বিক্রি করতে আসেন। আর বাজারের ভর্তি তলির সাথে ফুল, পাখি হাতে লোকেদের বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। রাসের সঙ্গে শোলার কদমফুল, কাকাতুয়া, টিয়ার সম্পর্ক কতদিনের সে কথা বলে গিয়েছেন সুধাংশু কুমার রায় ১৯৫১ সালে দ্য আর্টিজান কাস্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গল এন্ড দেয়ার ক্রাফট গবেষণায়।(বেশ কিছু তথ্য মন্থন সাময়িকী থেকে নেওয়া)
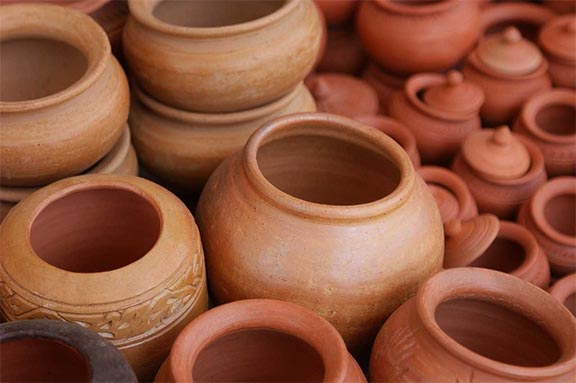
শাসনের পোড়ামাটির কাজ
শাসনে নতুন ধরণের নতুন ধরণের ঘর সাজানোর পোড়ামাটির কাজ হচ্ছে। মাটির চেয়ার থেকে বইএর তাক, টেব্ল, ড্রেসিং টেবল, নাম নেম প্লেটসুহ আরো কত কি। গ্রামের প্রায় ৬০ জন কুমোর এই কাজ করছেন। কোনও জিনিসই পড়ে থাকে না। নতুন ধরণের বাজার পাবার কাজে তাঁরা ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠেছেন।
দত্তপুকুরের মাটির কাজ
কলকাতা-বনগাঁ রাস্তায় দত্তপুকুর। পরম্পরার মাটির কাজ বলতে এখন টিকে রয়েছে শুধুই সরার কাজ। কিন্তু পরম্পরার কাজ ছাড়া অন্যান্য নানান মাটির কাজ অন্যান্য প্রদেশ আর বিদেশেও যাচ্ছে। এ ছাড়া বাড়ির মেঝেতে লাগানোর জন্য পোড়ামাটির টালি থেকে পাইকারিহারে তৈরি ঘরে ঝোলানো মুখোশ সবই তৈরি হয় দত্তপুকুর অঞ্চলে। এলাকার মানুষজন এই শিল্পকে পাইকারি ব্যবসায় রূপান্তরিত করে ফেলেছেন। গবেষকের মুখে বাঁকা হাসি। যাঁরা এই কাজ করেন তাদের মুখেও হাসি, কিন্তু সে হাসি তৃপ্তির। দত্তপুকুর-বিড়া-হাবড়া অঞ্চল জুড়ে এখন মাটির কাজের রমরমা। কলকাতার বিভিন্ন রেস্তোঁরায় যে বাহারি মাটির থালা বা জলের পাত্র দেখা যার তাঁর নিরানব্বই শতাংশ আসে এই পোড়ামাটির অক্ষ থেকে।

দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল কিছু মানুষ সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। পারম্পরিকভাবে এই অঞ্চলে ছিল বেশ কিছু কুমোর পরিবার। সব বিপর্যয়ে যা হয়, স্থানীয় মানুষ হাত বাড়িয়ে দেন সেই আতান্তরে পড়া মানুষদের দিকে। ক্রমশ তাঁরা গুছিয়ে ওঠেন। আজ তাঁরা এমন ভারত জোড়া ব্যবসা ফেঁদেছেন যে ছোট শিল্পের পাশে না দাঁড়ানো ব্যাঙ্কও তাদের ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছে।
কলকাতা-বনগাঁ রাস্তায় বিড়া। বিড়ার চৌমাথার অদূরে শ্বেতপুর গ্রাম – ট্রেকার যায়। স্থানীয় অঞ্চলের চাহিদা আনুযায়ী তাঁরা হাঁড়ি, ঠেঁকি, ইত্যাদি তৈরি করতেন সম্বৎসর। তাদের নতুন প্রজন্ম সেই মানুষদের দেখাদেখি নতুন করে নিজেদের আবিষ্কার করতে শুরু করে দিলেন। তাঁদের আনেকে এখনও পুরোনো কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু নতুন ধরণের কাজ করছেন।

টোকা
কলকাতা-টাকি রাস্তায় পড়ে মেটিয়াহাট, ধান্যকুড়িয়ার পরের স্টপ। এই অঞ্চলের বিভিন্ন হাটে ওঠে টোকা। চাষীরা মাথায় দিয়ে মাঠে চাষ করেন। চাচা হোচিমিনের মাথায় য়েন ২৪ পরগণার টোকাকেই দেখি। সেটি শহুরে কেউ কেউ পরেন যেমন প্রাক্তন আমলা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কিছু মানুষ। তারা নতুন করে পরিধান করে আবার নিজস্ব নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন।

হোগলা পাটির মাদুর
উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত, বসিরহাট, দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া, বনগ্রামে রামনগরের ধাঁচে একহারা বুনন পদ্ধতি অনুসরণ করে মাদুর তৈরি হয়। তবে এ অঞ্চলে পাতি বা হোগলা বেশি তৈরি হয়।
অসম্ভব নরম, অসম্ভব কম দামি এই মাদুর ওঠে মেটিয়াহাটে। কাঠিটা যদিও হোগলা নয়, কিন্তু অনেকটা হোগলার মত দেখতে। স্থানীয় মানুষ বলেন পাটি। আপনার পকেট খুশি, মাদুরের আরামে দেহ মহাশয়ও আরও খুশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আলিদায় রূপোর ফিলিগ্রি
এখানে যাওয়া যায় ঠাকুরপুকুর হয়ে নেপালগঞ্জ হয়ে বা বারুইপুর থেকে। এখানে রূপোর নানান দ্রব্য তৈরি হয় যেমন বালা, বাউটি, নেকলেস, গলার মালা, পালকি, রথ, আগরবাতি স্ট্যান্ড, মুকুট, সিংহাসন ইত্যাদি। মোটামুটি দেড় হাজার শিল্পী রয়েছেন।
Interesting article
Thanks Souvik Roy
অনেক অনেক কিছু শিখলাম।
এই শিল্পীদের নাম ঠিকানা দিতে পারবেন?