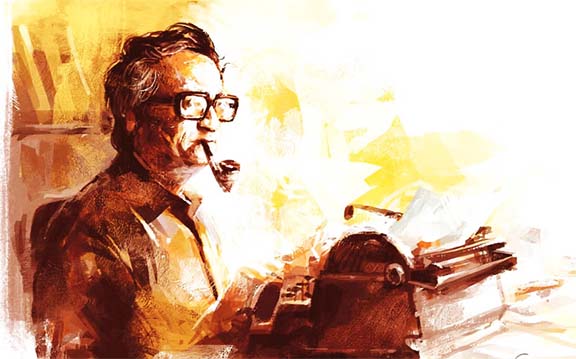
বাংলায় উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছে ১৮৫৮ সালে ‘আলালের ঘরে দুলাল’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তারও ৫০ বছর পর ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম উপন্যাস ‘আনোয়ারা’ প্রকাশিত হয়। গত ১০০ বছর সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশে অনেক মানসম্মত ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হয়েছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ এ-ভূণ্ডের সাহিত্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি করে। এর মানে এই নয় যে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা-পরবর্তী উপন্যাসকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে বরং ১৯৭১ এজন্যে একটি বিভেদক রেখা যে স্বাধীন জাতিসত্তা পূর্ববঙ্গের লেখকদের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করেছে; দিয়েছে আত্মবিশ্বাস এবং প্রাদেশিকতার পরিবর্তে স্থলাভিষিক্তি হয়েছে বৈশ্বিকতা। এর সঙ্গে আরো জড়িত ছিল শিক্ষার বিস্তার, প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ এবং হুমাযূন আহমেদের মতো যুগস্রষ্টা কথাশিল্পীর আবির্ভাব।
উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে প্রথমে বাঙালি জাতি এবং পরে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল বলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আকাক্সক্ষা এই ভূণ্ডের মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ দিয়েছে এই জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ অর্জন করেছে স্বাধীনতা। জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য — অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র গঠনের সূত্রপাত ঘটা থেকে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথেই তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। অন্যদিকে উপন্যাসে বিবৃত হয় ঔপন্যাসিকের জীবনভাবনা। ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তা কাহিনীর আধারে নানা আঙ্গিকে, ভাষাবৈচিত্র্যে, উপমা-রূপকের অনুসূত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় উপন্যাসে। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে, উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ ও বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যেতে পারে আর এদের সঙ্গে উপন্যাসের আন্তসম্পর্ক উন্মোচন করে বুঝে নেওয়া এবং বাংলাদেশের উপন্যাসে উপজীব্য এসব প্রসঙ্গের স্বরূপ এবং সৃজনশীল তাৎপর্য উন্মোচন করা অনিবার্য।
এক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) একটি বাক্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, ‘একটি জনগোষ্ঠী থেকে পরিপূর্ণ একটি জাতিতে পরিচিত হওয়ার সংকল্প’ ছিল বাঙালির। এজন্য বাংলাদেশের উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজ স্পষ্টভাবে উপজীব্য হয়েছে তাঁর উপন্যাস ‘চিলেকোঠার সেপাই’তে। পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিজীবন তখন এতটাই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে ঊনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনের মধ্যেও এর নায়ক ওসমান চিলেকোঠার মধ্যেই আত্মরতি আর বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে, কেঁপে কেঁপে উঠেছে মিছিল আর স্লোগানের অভিঘাতে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘খোয়াবনামা’য় (১৯৯৬) তিনি ফিরে গেছেন পাকিস্তান সৃষ্টির মুহূর্তে। শহুরে জীবন নয়, গ্রামীণ মানুষের জীবনই যে পাকিস্তান আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছিল, পাওয়া যায় সেই রাজনৈতিক-ব্যক্তিক বিবৃতি; আর কাহিনীর নেপথ্যে সক্রিয় থেকেছে অনতিদূর কালের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি আর তেভাগা আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিল যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদের কথাও চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে, সেসঙ্গে শ্রেণিবিভক্তির সূক্ষ দিকও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। মূলত আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের শিল্পসংগ্রামের মহাকাব্যিক শব্দরূপ ‘খোয়াবনামা’। বর্তমানের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস থেকে ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আত্মসমিধ সংগ্রহ করেছেন বাঙালির অতীত ইতিহাসের প্রাণময় মানব সংগ্রামের বহুবিধ প্রান্ত থেকে। তেভাগা আন্দোলন এবং ভারত বিভাগের ঐতিহাসিক গ্রন্থিজটিল সময়স্রোতের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে অতীতের পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলনের অনুসূত্র।
কাৎলাহার বিল ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম গিরিরডাঙ্গা ও নিজগিরিরডাঙ্গা, গোলাবাড়ি হাট প্রভৃতি স্থানের লোকায়ত চেতন, অবচেতন-অচেতন জগতের সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনা ধারার ক্রমরূপান্তরশীল অধ্যায়ের দ্বন্দ্ব জটিল সংঘাতই বাংলাদেশের চিত্রণ হিসেবে গণ্য। ঔপনিবেশিক শাসন ও শ্রেণি শাসনের আধিপত্য বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে কাৎলাহার বিলের তীরবর্তী মানুষের সামাজিক স্তরের বহুভঙ্গিলতা, সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিস্তার, মানবীয় প্রান্তের বিচিত্র গতি প্রকৃতি, শ্রেণিবোধের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রূপ সর্বোপরি সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঔপন্যাসিক। তাঁর কথায় — ‘আমি নির্দিষ্ট কোনো philosophy মাথায় রেখে reality দেখি না। reality কে আমি ভেতর থেকে দেখতে চাই। কিন্তু আমি তো journalists না। reality মানে যা দেখতে পাচ্ছি কেবল তাই না। এর ভেতরকার স্বপ্ন, সাধ, সঙ্কল্প, কুসংস্কার সবই reality-র ভেতরকার reality.’ ভেতরকার reality-এর অন্বেষণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রয়োজনীয় বাস্তব উপাদানের সঙ্গে বাহ্যঅভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের দ্বান্দ্বিক উপাদ্যের সদ্ব্যবহার করেন। ব্যক্তি অস্তিত্বের সঙ্কটকে তিনি মিলিয়ে নেন প্রবহমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে এবং বস্তুজগত থেকে আহৃত উপাদানকে তিনি প্রসারিত করেন মনস্তত্ত্বের গহীন, অতল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। reality-এর মাত্রাকে বহুবর্ণিল ঘটনাধারায় অঙ্কন করায় ঔপন্যাসিকের সচেতন অভীপ্সা জ্ঞাত হয়েছে সামাজিক ও কালিক মাত্রার দ্বৈতস্রোতে।
কাৎলাহার বিলের ভৌগোলিক বিবরণ ও তৎসঙ্গে ফকির বিদ্রোহের প্রাককথন দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। কাৎলাহার বিলের আদি ইতিবৃত্তের সঙ্গে মুনসি বয়তুল্লা শাহ-এর পাকুড় গাছের মাথায় অবস্থান গ্রহণের ইতিহাস বিবৃত করে ঔপন্যাসিক ‘খোয়াবনামা’র প্রাথমিক প্রতিপাদ্য করেছেন সুস্থিত। কারণ মুনসি বয়তুল্লাহ শাহ, যিনি এক বিকেল বেলা মজনু শাহের অগুনতি ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান গড়ের দিকে যাবার সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেপাই সর্দার টেলরের গুলিতে মারা পড়েন, তার অলক্ষিত উপস্থিতি উপন্যাসে একটি জনপদের লোকায়ত মানুষের গল্প গাঁথা সাহস সঞ্চয়ে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছে। এই অলক্ষিত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বিলপাড়ের মানুষের চেতন অচেতন, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ প্রসারী থেকেছে উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত পর্যায় পর্যন্ত।
বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন উপস্থাপনে দেখা যায় উপন্যাসের প্রাথমিক প্রতিপাদ্যে বিলের তীরবর্তী জনপদের চাষী-মাঝি ও জোতদারের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে যা পরবর্তী সময় আখ্যানে প্রধান হয়ে উঠেছে চাষী-মাঝির দ্বন্দ্বময় জীবন স্রোতের বিবরণ অনুষঙ্গে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দূরাগত প্রতিক্রিয়ায় যে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব তারই পরের বছর কাৎলাহার বিল শরাফত মন্ডল ইজারা নিয়ে দখল করেছে। শরাফত মন্ডলের দখলে যাবার পূর্বে কাৎলাহার বিলের মাছ ভোগ করেছে মাঝিপাড়ার মানুষই। বাঘাড় মাঝির নাতি তমিজের বাপ এই বিলে মাঝিদের প্রাক্তন আধিপত্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বলে স্বপ্নের ভেতর সে বিল জুড়ে হাঁটে। পাকুড় গাছে ঘাঁটি গাড়া গুলিবিদ্ধ মুনসির কাছ থেকে শক্তি পাবার জন্যে, বাস্তবের নির্মমতা থেকে পরিত্রাণের আশায় গভীর রাতে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় তমিজের বাপ। তার হাতে একমাত্র নাতনি কুলসুমকে তুলে দিয়ে চেরাগ আলী নিরুদ্দেশ হন। অন্যদিকে তমিজের মধ্যে জাগ্রত হয় পেশাগত সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা। মাঝির ছেলে তমিজ জমির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু দেখতে পায় শরাফত মন্ডলের সঙ্গে মাঝিদের দ্বন্দ্বের সঙ্কট মোচনে নিজেকে চাষা বলে পরিচয় দিতে ও আধিপত্য বিস্তারে শরাফত মন্ডল বদ্ধপরিকর।
অতীতের মুনসির সংগ্রাম এক্ষেত্রে লোকায়ত মানুষের অনুপ্রাণনার উৎস। কিন্তু কোম্পানীর ও ব্রিটিশের ডান্ডা উঠে আসে দেশি সায়েবদের হাতে। ভারত ভাগ হয়ে গঠিত হয় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান, দেশি সায়েবরা নতুন আইন বানায়, কেউ হয় টাউনবাসী। কেউ হয় কন্ট্রাকটর। আবার নিজদেশে পরবাসী হয় কোটি কোটি মানুষ। হিন্দু জমিদার নায়েব চলে যাওয়ার পরও আজাদ পাকিস্তানে জমি আর বিলের মানুষ নিজেদের মাটি আর পানির পত্তন ফিরে পায় না। রাজনৈতিক ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গাছের সঙ্গে পাকুড় গাছও কাটা পড়ে, উন্নয়নের ধাক্কায় ইটের ভাটা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতি বদলে যায়। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গ্রাম। পাকুড় গাছের বিনষ্টি তমিজের বাপকে তাড়িত করতে থাকে। তার কাছে এর থেকে বড়ো সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না। সেই পাকুড় গাছ খুঁজতে গিয়েই তমিজের বাপ চোরাবালিতে পড়ে মারা যায়। আর ভবানী পাঠকের সঙ্গে পূর্ব পুরুষের জের টেনে যে বৈকুণ্ঠনাথ প্রতীক্ষা করেছিল ভবানীর শুভ আবির্ভাবে সে নিহত হয় নির্মমভাবে।
কাৎলাহার বিলের মালিকানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ‘খোয়াবনামা’ও হস্তান্তর হয়ে যায়। চেরাগ আলী ফকিরের পুরনো জীর্ণ প্রায় খোয়াবনামা কুলসুমের বা তমিজের বাপের জিম্মাদার থেকে কেরামতের অধীনে চলে যায়। আর কেরামতের মাধ্যমে তা শরাফত মন্ডলের শহরে চাকুরে পুত্র আজিজের হস্তগত হয়। ‘খোয়াবনামা’র এই বেহাত হওয়ার ঘটনা উপন্যাসে প্রতীকী হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখা ব্রাত্য মানুষের এই পটভূমি পাল্টে গেলে তার সামূহিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিনাশের করাল গ্রাসে। এ কারণে কেরামত আলী তেভাগার কবি থেকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের কবিতে পরিণত হয়। যশপ্রার্থী, গৃহগত সুখ আকাঙ্ক্ষী কেরামত আলী শেষ পর্যন্ত শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে হয় বিচ্যুত। উপন্যাসের প্রাথমিক প্রতিপাদ্যে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) মাঝির মেয়ে আবিতনের সঙ্গে ‘কলুর বেটা গফুরের’ প্রণয় সম্পর্ক ও তার প্রতিক্রিয়া বিবৃতির মধ্যদিয়ে লোকায়ত জীবনে বিরোধের মৌলসূত্রগুলো উন্মোচিত হয়েছে। এ জনপদের লোকায়ত সম্প্রদায় পরস্পরের বাড়িতে খাওয়া, বিবাহ, যাতায়াত এমন কি জেয়াফতে মুসলমান জোতদার, মাঝি, চাষা সবার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা হয়। কাৎলাহার বিল কেন্দ্রিক মাঝি-চাষী বিরোধ পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা মুসলমানদের হানাফী-রফাদানী মাযহাব সংক্রান্ত জটিলতায় পরি¯্রুত হয়ে রাজনৈতিক বাতাবরণের তমসায় পর্যবসিত হয়। একটি উদ্ধৃতি- ‘পরিবেশনের দায়িত্বে থাকলেও প্রথম দল বিদায় হবার পর হুরমতুল্লা খিদেয় অস্থির হয়ে আর অপেক্ষা করতে পারে না। গলির একটি সারিতে পাতা পেতে বসে পড়ে একটু চাপাচাপি করেই। কিন্তু পাশেই তমিজের বাপ। কেন বাপু, গোয়ালঘরের পেছনেই তো তোমাদের মাঝির জাতের মানুষের পাত পড়েছে। ওখানে সাকিদারি করার কাজও করছে মাঝি পাড়ার লোক। ওখানে বসলে তোমার পাতে ভাতের ভাগ কি কম পড়বে?…’ (পৃ. ১১০)
হুরমতুল্লাহ শরাফত মন্ডলের জমি বর্গাচাষ করে। মাঝি সম্প্রদায় তার কাছে সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। এ কারণে তার চাষের জমির পাশে শরাফত মন্ডল তমিজকে বর্গাচাষের জমি দিলে সে উন্নাসিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু তমিজ মাঝির সন্তান হলেও একই সঙ্গে সে চাষের জমিতে নিজেকে একজন সৃজনশীল চাষা হিসেবে আবিষ্কার করে। কিন্তু জমির গন্ধ, স্বভাব আয়ত্ত করেও সে নিজেকে জমির সঙ্গে যুক্ত রাখতে অক্ষম হয়। মালিকানার দাপটের সামনে সে কুলাতে পারে না। কালাম মাঝির নৌকা ও তার ছোটো শালা বুধাকে নিয়ে তমিজের বাপ বাঙালির কোলে মরা মানুষের বা ডোবা দয়ের ধার ঘেঁষে জাল খাটিয়ে এক মণ সোয়া মণ ওজনের যে বাঘাড় ধরে এসে ভোর রাতের দিকে কাৎলাহার বিলে প্রবেশ করেছিল; তার পরিণতিতে ঘটে মাঝি-চাষার বহুদিনের বিরোধের চূড়ান্ত রূপ। কাৎলাহার বিলে প্রবেশের পরে শরাফত মন্ডলের হাতে মাছ চোর হিসেবে ধৃত হয়ে প্রহৃত হয় তমিজের বাপ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালাম মাঝির নেতৃত্বে বিলের মালিক শরাফত মন্ডলের বিরুদ্ধে ঘটে বিস্ফোরণ — ‘কালাম মাঝির সঙ্গে সবাই একমত, কিন্তু কাৎলাহার বিলের পত্তন কাকে দেওয়া উচিত এ নিয়ে কারো তেমন মাথা ব্যথা নেই। বিল মাঝিরাই মাছ ধরবে। তাদের কথা হলো পত্তন-টত্তন আবার কী?’ (পৃ. ২১১) কাৎলাহার বিলের পশ্চিম পাড়ে গিরিরডাঙ্গার মাঝির এলোমেলো সারিতে দাঁড়িয়ে বিলে ঝপঝপ করে জাল ফেলে। কিন্তু বিলের চোরাবালি দলদলার মধ্যে আমিতনের বাপের নাতি, বুলুর বেটা পড়ে মৃত্যুবরণ করলে ঘটনার গতিধারা শরাফতের দুই পুত্র আজিজ ও কাদেরের সহায়তায় মাছ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ততায় প্রলম্বিত হয়। অথচ মাঝিদের মাছ ধরার সময় কবি কেরামতের শ্লোক আবৃত্তি উদ্দীপনার সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত কেরামত পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পায়। তমিজ জেলবন্দি হয়। গ্রামীণ স্রোতধারায় এই আলোড়নের পাশে পাকিস্তানে আন্দোলন সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইসমাইল নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার প্রত্যাশায় মাঝি-চাষী বিরোধের মীমাংসায় এগিয়ে আসে। এতে গ্রামীণ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয় রাজনীতির মশাল। ‘ইসমাইল তখন কাদেরের কানের কাছে মুখ নেয়, ‘কাদের তোমরা এটা করেছোটা কী? মাঝিদের নামে মামলা করার আর সময় পেলে না?’ কাদের কিছু বলবে করলেও ইসমাইল হোসেন তাকে সুযোগ দেয় না; ‘আরে ঐ যে কী নাম? — হ্যাঁ হ্যাঁ, তমিজ। তমিজ কি তমিজের বাপের ভোট না থাকলেও ছয় আনা ট্যাকস দেওয়ার লোক মাঝি পাড়ায় কম নেই। এটা বড় কথা নয়। মাঝি পাড়ার ভোট মালেক সাহেবের বাকসে পড়লে তার এফেক্ট পড়বে এই এন্টায়ার এরিয়ায়।’ (পৃ. ২২৮) এ কারণে ইসমাইল মাঝি পাড়ার বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কালাম মাঝির গৃহের উঠানে বসে — ‘মুসলমানদের মধ্যে সে সকল ভেদাভেদ দূর করার আহŸান জানায়। নায়েব বাবুর চক্রান্তেই তমিজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সে নিশ্চিত কাৎলাহার বিল মাঝিদের হাতছাড়া হয়েছে হিন্দু জমিদারের লোভে এবং চক্রান্তে। ইসমাইল ভোটে জিতলে এই বিলের ইজারা পাবে মাঝিরা। এটা হবে তার এক নম্বর কাজ। পাকিস্তানে তো আর জঘন্য ও বর্বর বর্ণপ্রথা থাকবে না, যার যা হক তাকে তাই দেওয়া হবে।’ (পৃ. ২৩১)
অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অস্ত্রে পরিণত হয় বিল পাড়ের জনগোষ্ঠী। কেরামত পারানিপাড়ার স্কুলের ফিল্ডের সভায় আবির্ভূত হয় তেভাগার শিল্পী থেকে পাকিস্তানের শিল্পী হিসেবে। কারণ ‘ইসমাইল সাহেবের তদবিরেই তুমি পুলিশের হাত থ্যাকা বাঁচিছো। হয় তার ফরমায়েশ মতো গান বান্দো, না হলে জয়পুর পাঁচ বিবির ঘাটা ধরো।’ (পৃ. ২৩২) ইতোমধ্যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের নায়েব মশাই শরাফত মন্ডলের সহায়তায় সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে চায়। বাঙালি নদীর কোলে ভবানী পাঠক গোরা কোম্পানীর সেপাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেহ রেখেছিল — এই লোকবিশ্বাসকে ধারণ করে প্রতিবছর পোড়াদাহ মেলার দিন তার পূজা হয়। কিন্তু নায়েব মশায় বৈকুণ্ঠ কর্মকার, দশরথ, যুধিষ্ঠির ও পালপাড়ার জনগণকে বোঝাতে চায় — ‘বাঙালি নদীর কোলে মা ভবানীর দয়া’ এবং এ প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয় — ‘ঐ মাছ চুরি করে বেটা মাঝি, ম্লেচ্ছমাঝি, এ্যাঁ’? মায়ের সন্তান হয়ে আমরা তা সহ্যও করি! আবার তার সঙ্গে তোদের মহাখাতির! ছি!’ (পৃ. ২৩৬) অর্থাৎ কি মহামেডান কনষ্টিটুয়েন্সি কি কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট সুরেন সেনগুপ্ত সকলেই তাদের ক্রীড়নক করতে চেয়েছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি ক্রমেই শিকড়ায়িত হতে থাকে গ্রামীণ সমাজে। আর দেশবিভাগের প্রাকমুহূর্তে কলকাতার নির্মম নৃশংস দাঙ্গার লোনা জল এসে প্রবেশ করে কাৎলাহার বিলপাড়ের জনমন্ডলে, গোলাহাটের বাজারে। তখন তার প্রতিক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকে না নায়েব মশায়ের কাছারি গৃহ। আর কামার পাড়ায় প্রজ্বলিত আগুনে মৃত্যুবরণ করে দশরথ কর্মকার। ছুটে আসে ইসমাইল, কমিউনিষ্ট পার্টির ডেডিকেটেড লোক অজয় দত্ত, মিনতি দত্ত প্রমুখ। ঔপন্যাসিক এ সূত্রেই উন্মোচিত করেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের স্ববিরোধী চারিত্র্য। কামার পাড়া পরিদর্শন শেষে রাতে কাদেরদের বাড়িতে ফিরে ইসমাইল অজয় ও মিনতি ‘এই গরমে খাওয়ার এতো এতো আয়োজন দেখে কাদেরকে মিষ্টি করে বকে, কিন্তু পেটপুরে পোলাও কোর্মা খায়।’ (পৃ. ২৬৬) কামার পাড়ায় আগুন লাগিয়ে আসার পর আফসার মাঝির বালামুসিবত আরম্ভ হলে বৈকুণ্ঠসহ সে কামার পাড়ায় যুধিষ্ঠিরের মার কাছে মাফ চাইতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ‘মন্ডল বাড়ির পর কয়েক বিঘা জমি পেরিয়ে কলুপাড়া, কলুপাড়ার পর বিলের দক্ষিণ উধার ধরে মন্ডলের বিঘার পর বিঘা জমি পার হলে খাল। খালের ওপারে পুব দিকেই কামার পাড়া।’ এই খালের এপার থাকতেই তারা দেখে কামার পাড়ার দক্ষিণ সীমানা থেকে খালের দিকে এগিয়ে আসছে কয়েক জনের ছায়া। এরপর আফসারকে নিহত হতে হয় এবং বৈকুণ্ঠ আহত হয়ে ফিরে আসে।
কুলসুম ঘটনার পরম্পরায় বদলে যায়। দাদার বই ‘খোয়াবনামা’ হস্তান্তর করে কেরামতের কাছে, কেরামতের জিম্মাদার থেকে আজিজের হস্তগত হয় এটি (পরি : ৩৮)। গ্রামীণ জীবনের নানা ঘাত-সংঘাতের সময় তমিজ খালাশ পায়। কাৎলাহার বিলের পত্তন ইসমাইল হোসেনের সাক্ষাতে নায়েব বাবুর সঙ্গে কালাম মাঝি বন্দোবস্ত করে নেয়। মাঝিপাড়ায় এ সংবাদ আনন্দ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। স্বপ্ন দেখে তারা। ইতোমধ্যে দেশভাগ হয়। তারপরে মাঝি পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বি তমিজের বাপের মৃত্যু ঘটে দলদলায় আটকে। স্বপ্নভঙ্গ ঘটে মাঝিদের। তারা উপলব্ধি করে কাৎলাহার বিলের পত্তনি কেবলমাত্র হস্তান্তর হয়েছে, কালাম মাঝি তার বর্তমান মালিক। তমিজ হুরমুতুল্লাহর ‘ঘেগি বেটি’ ফুলজানকে বিবাহ করে। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কুলসুমের ইঙ্গিতময় সংলাপ- ‘তোমার বাপ কয়, বেটা যেটি খুশি লিকা কর, কিন্তু বৌয়ের সাথে থাকবার পারবি না।’(পৃ. ৩০৮) উপন্যাসে পরিণতিতে সত্য হয়ে ওঠে। ৪৮ পরিচ্ছেদে দেখা যায় কাৎলাহার বিল একদিনের জন্যে জমা নিয়ে মাছ ধরতে আসা যমুনার বনেদি মাঝিদের সঙ্গে সংঘর্ষে তমিজের বর্শায় খুন হয় জনৈক যমুনার মাঝি। ফলে তমিজকে পালিয়ে বেড়াতে হয় মামলা কাঁধে নিয়ে। ইতোমধ্যে দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে মানুষের নির্লজ্জ লোভের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় ৫০ ও ৫১ পরিচ্ছেদে। আর স্বাধীন পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে সম্পত্তি দখলের উন্মক্ত আক্রমণে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হতে হয় বৈকুণ্ঠকে। অন্যদিকে তমিজ উপলব্ধি করে কাদের-আজিজ-ইসমাইল আপাত দৃষ্টিতে তাকে প্রশ্রয় দিলেও তারা কেউই তাদের মতো মেহনতি মানুষের মিত্র নয়। এ রাষ্ট্রে জমির উপরে বর্গাদারের হক কায়েম করার আইন জারি অসম্ভব। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন তমিজকে উদ্দীপ্ত করে। তার স্মৃতিতে ভাস্বর ‘জয়পুরে যখন ধান কাটিচ্ছিলাম, তখনি তো জোতদারেরা সব দৌড়াচ্ছিল পাছার কাপড় তুইল্যা।’(পৃ. ৩৩৬) এ কারণে সে কাদেরের চিরস্থায়ী চাকর হবার ভাগ্যকে অস্বীকার করার জন্যে ঢাকাগামী ট্রেন থেকে নেমে পড়ে নাচোলের উদ্দেশ্যে। যে তেভাগা, সরকারের দমন পীড়নে বিপর্যস্ত সেই তেভাগা আন্দোলনের সাফল্যের খোয়াব সন্ধানে তার যাত্রা সংগ্রামী মানুষের চিরায়ত আখ্যানে পরিণত হয়।
কাৎলাহার বিল পাড়ের চেরাগ আলির নাতনি যাকে তার দাদা ভবঘুরে জীবন থেকে স্থায়ী করেছিল তমিজের বাপের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে, সেই কুলসুম নিঃসঙ্গ গৃহে কালাম মাঝি ও কেরামতের জটিল সঙ্কটে আকস্মিক ঘটনায় হত্যাকাÐের শিকার হয় (৫৬ পরিচ্ছেদ)। আর ফুলজান তমিজ ও তার কন্যা সকিনার মধ্যে দেখতে পায় স্বপ্নের নবসৃষ্টি। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা থেকে সকিনা যেন (৫৯ পরি) স্বপ্নকে জাগরিত করে তুলতে চায়। সকিনা হয়ে যায় সামনের ইতিহাসের অবিনাশী কথক। বস্তুত সময়ের গ্রন্থিল স্রোতে কাৎলাহার বিল পাড়ের মানুষের স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্নরূপে ‘খোয়াবনামা’র ইতিবৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। এই ইতিবৃত্তে ইতিহাসের চিরায়ত মানবীয় সংগ্রামশীলতার কথা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি তা ভাস্বর হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবনের আশা-প্রত্যাশা, ব্যর্থতার ইতিহাসে। স্বপ্নভঙ্গের এই লোককথায় বিশিষ্ট মানবের ইতিকথা বাংলা উপন্যাসের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।
আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখলাম উপন্যাসই জাতিগঠন করে আর জাতিগঠনে পালন করে প্রধান ভূমিকা। মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যায় আমাদের সৃজনশীল লেখায় বিশেষ করে উপন্যাসে জাতিরাষ্ট্র, উপনিবেশবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে যাকে আমরা ‘বাংলা উপন্যাসে বাংলাদেশ’ শিরোনামে চিহ্নিত করতে পারি। তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত ‘খোয়াবনামা’।
লেখক : ড. মিল্টন বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু গবেষক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, email-drmiltonbiswas1971@gmail.com